আমরা এমন এক দৃশ্যমান বস্তুজগতের বাসিন্দা, যার পাশাপাশি রয়েছে অদৃশ্য অণুজীবের এক সমান্তরাল জগৎ (চধৎধষষবষ ড়িৎষফ)। জীবজগতের মোট ২৩টি বিভাগের ভেতর মাত্র তিনটিকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই – প্রাণী, বৃক্ষ ও ছত্রাক। বাকি সবাই আমাদের চোখের অন্তরালে, যা মোট জীবজগতের প্রায় ৮০ শতাংশ। এই অণুজগৎ আমাদের এমনভাবে বেষ্টন করে আছে যে তা আমাদের দেহের ভেতরে ও বাইরে সমানভাবে বিরাজমান। আমাদের ত্বকের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে রয়েছে অন্ততপক্ষে এক লাখ জীবাণুর উপস্থিতি, যারা আমাদের ত্বকের মৃত কোষকলা এবং লোমকূপ থেকে নিঃসৃত রস খেয়ে বেঁচে থাকে। এভাবেই বিলিয়ন বিলিয়ন জীবাণু আমাদের নাক, মুখ, চোখ, কান ও অন্যান্য রন্ধ্রপথে, যা বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের দেহাভ্যন্তরকে যুক্ত করে রেখেছে – সেগুলোতে নিঃসংকোচে বাস করছে। সত্যিকার অর্থে, এদের উপস্থিতি ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারব না, কারণ এরা আমাদের খাদ্য পরিপাক থেকে অনেক ধরনের কাজেই নিত্যসঙ্গী। আমাদের পরিপাকতন্ত্রে রয়েছে অন্তত ৪০০ ধরনের শত ট্রিলিয়ন অণুজীবের উপস্থিতি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ১০ কোয়াড্রিলিয়ন জীবকোষ (পবষষ) থাকে, কিন্তু তার শরীরে মোট অণুজীবের সংখ্যা এরও প্রায় দশগুণ। আমরা নানা উপায়ে তাদের ধ্বংস করার ফন্দি করলেও এ-পৃথিবীতে তারা কোটি কোটি বছর ধরে বেঁচে আছে এবং থাকবে, বলতে গেলে এটা তাদেরই পৃথিবী এবং তারা অনুমতি দিচ্ছে বলেই তাদের অনুগ্রহে আমরা এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারছি।
প্রখ্যাত মার্কিন জীববিজ্ঞানী লিন মারগুইলিস যেমনটা বলেছেন, পৃথিবীতে আমাদের উপস্থিতি ছাড়াও জৈবজগৎ ভালোভাবে বেঁচে থাকবে; কিন্তু অণুজীব না থাকলে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই পৃথিবীপৃষ্ঠ চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো উষর, প্রাণহীন হয়ে পড়বে।
বেশিরভাগ অণুজীবই হয় আমাদের জন্য উপকারী, নয় নিরপেক্ষ – মাত্র হাজারে একটি অণুজীব আমাদের জন্য ক্ষতিকর। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজে অণুজীব আমাদের সহায়তা করছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে – মাটিকে উর্বর ও ফলদায়িনী করা, জলকে বিশুদ্ধ রাখা, আমাদের অন্ত্রে ভিটামিন প্রস্তুত করা ও খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করা, নাইট্রোজেন চক্রকে সহায়তা করে আমিষ জাতীয় জিনিস (Amino acids nucleotides) উৎপন্ন করা ইত্যাদি। তারা যদি নাইট্রোজেন উৎপাদনে সহায়তা না করত, তাহলে শুধু আমরা কেন, কোনো বৃহৎ প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারত না। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন তৈরিতেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। তাদের বেঁচে থাকার প্রাণশক্তিও অফুরান। নোবেলজয়ী বেলজিয়ান জৈব রসায়নবিদ ক্রিস্টিয়ান ডি জ্যুব বলেছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হলে একটিমাত্র জীবাণু মাত্র একদিনে তার দুই লাখ আশি হাজার বিলিয়ন কপি তৈরি করতে সক্ষম। আর এই বংশ বিস্তারকালে প্রতি মিলিয়ন কপিতে একবার একটি নতুন ধরনের মিউট্যান্ট জিন তৈরি হয়, যা নতুন একটি জিন কোড লাভ করে। খাদ্য হিসেবে তারা খেতে সক্ষম কাগজ, ওয়ালপেপার, কাঠ, পাথর, এমনকি ধাতু পর্যন্ত।
অস্ট্রেলিয়ান জীববিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এমন একটি জীবাণু, যা ধাতু গলাতে সক্ষম শক্তিশালী সালফিউরিক অ্যাসিডেও বেঁচে থাকতে পারে। আবার এমন ধরনের জীবাণু পাওয়া গেছে, যারা পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের বর্জ্য-সংগ্রাহকের মধ্যেও বেঁচে থাকতে সমর্থ। তাদের জীবিত পাওয়া গেছে কস্টিক সোডার হ্রদে, উষ্ণ প্রস্রবণের ফুটন্ত পানিতে, অ্যান্টার্কটিকার হিমশীতল পানিতে, প্রশান্ত মহাসাগরের এগারো কিলোমিটার নিচে, যেখানে পানির চাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুচাপের চেয়ে হাজারগুণ বেশি। একটি সিল করা ক্যামেরা, চন্দ্রপৃষ্ঠে যা দু-বছর কাজ করেছে, তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পর তা থেকেও জীবিত স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু আবিষ্কার করা গেছে। প্রতিকূল পরিবেশে জীবাণুরা নিজেদের গুটিয়ে নেয় এবং সুদিনের অপেক্ষায় থাকে নবজন্ম লাভের জন্য, যা তাদের দীর্ঘজীবন লাভের রহস্য।
নরওয়ের একদল বিজ্ঞানী ১৯৯৭ সালে আশি বছর ধরে সুপ্ত থাকা অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর স্পোরকে আবার পুনর্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছেন। একইভাবে পাওয়া গেছে ১১৮ বছরের পুরনো মাংসের টিন থেকে এবং ১৬৬ বছরের পুরনো বিয়ার থেকে উদ্ধার করা নবজীবনপ্রাপ্ত জীবাণু। তবে এ-বিষয়ে রেকর্ড হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসেল ভিরল্যান্ড ও তাঁর সহযোগীদের, যাঁরা ২০০০ সালে ২৫০ মিলিয়ন বছর বয়সী সুপ্ত জীবাণুকে নতুন জীবন দিতে সমর্থ হয়েছেন, যা নিউ মেক্সিকোর লবণখনিতে মাটির ৬০০ মিটার গভীরে আটকে ছিল। সম্ভবত সে-জীবাণু মহাদেশটির চেয়েও পুরনো।
১৯৫২ সালে জীবাণু-প্রতিরোধক পেনিসিলিন যখন কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, তখন মার্কিন সার্জন জেনারেল উইলিয়াম স্টুয়ার্ট খুব নিশ্চিত ভাব নিয়ে ঘোষণা করেন, ‘সংক্রমক রোগের খাতাটি বন্ধ করার সময় পৃথিবীতে এসে গেছে। অন্তত আমেরিকা থেকে সংক্রমণকে আমরা দূর করতে পেরেছি।’ কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি – পেনিসিলিন ও তৎপরবর্তী আরো কিছু দামি জীবাণু-প্রতিরোধক জীবাণুঘটিত রোগের সংক্রমণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হলেও অণুজগতের অন্য একটি জীব (?) ভাইরাস আমাদের এখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলেছে। এই ভাইরাস হচ্ছে অণুজীব জগতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক, যা পরগাছার মতো কোনো জীবকোষ থেকে শক্তি সংগ্রহ না করে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। এই ভাইরাস এমনকি জীবাণুকেও আক্রমণ করতে পারে। ভাইরাস হচ্ছে, জীবিত ও নিষ্প্রাণ বস্তুর মাঝামাঝি একটি জিনিস। নোবেলজয়ী জীববিজ্ঞানী পিটার মেভাওয়ারের ভাষায় যা হচ্ছে, ‘নিউক্লিক অ্যাসিডের একটি সুতা, যা চারদিকে দুঃসংবাদ দিয়ে আবৃত।’
ভাইরাস কতটা ছোট ও বিধ্বংসী, তার একটি হিসাব আমরা পেয়েছি সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ ভাইরাসের (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ শুরু হওয়ার মাসতিনেক পর। তখন পর্যন্ত মাত্র ২০ লাখ লোক পৃথিবীব্যাপী করোনাক্রান্ত ছিলেন। কেউ একজন দেখিয়েছেন যে, করোনার একটি ভাইরাসের ওজন হচ্ছে ০.৮৫ এট্রোগ্রাম (০.৮৫ দ্ধ ১০-১৮ গ্রাম) অর্থাৎ এক গ্রামের এক ট্রিলিয়ন ভাগেরও ১০ লাখ ভাগের এক ভাগ। একজন মানুষকে অসুস্থ করতে অন্তত ৭০ বিলিয়ন ভাইরাস প্রয়োজন হয়, যার মোট ওজন হচ্ছে ০.০০০,০০০৫ গ্রাম। তখনকার আক্রান্ত ২০ লাখ লোকের জন্য মোট ভাইরাস হলো ০.০০০.০০০৫ দ্ধ ২০ লাখ, অর্থাৎ এক গ্রাম। এটি একটি বড় পানির ফোঁটার সমান আয়তনের, অর্থাৎ আমাদের এই উন্নত সভ্যতা, যা আমরা হাজার হাজার বছরের সাধনায় অর্জন করেছি – তা শুধু এক ফোঁটা ভাইরাসের কারণে হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে। এতেই প্রমাণ হয়, অণুজীবের কাছে আমরা কতটা ভঙ্গুর ও অসহায়।
আমাদের জানামতে, ভাইরাসের মোট সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার, যা আমাদের ফ্লু, বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক, এইডস ইত্যাদি শত শত ধরনের রোগ এনে দিয়েছে। এসব পুরনো রোগ ছাড়াও সাম্প্রতিক করোনা, সার্স, মার্স, জিকা, ইবোলা, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ বা ম্যাড কাউ ডিজিজ – সবই নানা ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। আমাদের শরীরের জীবন্ত কোষের জেনেটিক বস্তুকে এই ভাইরাসগুলোর ডিএনএ অণু হাইজ্যাক করে, যা তার বংশ বিস্তারের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ভাইরাসগুলোকে আমরা দেখতে পারি না। ১৯৪৩ সালে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পরই শুধু আমরা তাদের দেখতে পেরেছি। ভাইরাসদের রোগ সংক্রমণ ক্ষমতা এতো ব্যাপক যে, শুধু বিশ শতকেই বসন্ত রোগের ভাইরাস অন্তত ৩০ কোটি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ চার বছরে ২১ মিলিয়ন লোকের প্রাণহানির কারণ হয়েছে, আর স্প্যানিশ ফ্লু নামে পরিচিত ভাইরাস একই পরিমাণ প্রাণহানির কারণ হয়েছে যুদ্ধ-পরবর্তী মাত্র চার মাস সময়ে।
গত শতকের নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তৎকালীন সিআইএ পরিচালক জেমস উলসি মন্তব্য করেছিলেন, ‘আমরা ড্রাগনটিকে হত্যা করেছি ঠিকই, কিন্তু এখন এমন এক জঙ্গলে বাস করছি, যা ভয়ংকর বিষধর সাপে পূর্ণ।’ এর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন পৃথিবীর পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব প্রযুক্তির মারণাস্ত্রের বিপদকে বুঝিয়েছিলেন, যা সোভিয়েত আমলের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে নানা হাতে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জরুরি ভিত্তিতে সোভিয়েত শিবিরে কর্মরত সাবেক পারমাণবিক ও জৈব রাসায়নিক বিজ্ঞানীদের নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসার একটি কর্মসূচি নিয়েছিল, যাতে অন্য কোনো উগ্রবাদী রাষ্ট্র বা সংগঠন তাদের জৈব-রাসায়নিক ও পারমাণবিক কর্মসূচিতে এই বিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ত করতে না পারে। এর আগে সত্তর-আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিহাসের সব থেকে বড় জৈব-রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচিতে বিজ্ঞানীদের একটি বিশাল দলকে নিযুক্ত করেছিল। কানাডিয়ান আলিবেকভ ছিলেন সেই সোভিয়েত ‘বায়োপ্রেপারাত’ নামক কর্মসূচির দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি ১৯৯২ সালে কেন আলিবেক নাম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর বই বায়োহ্যাজার্ড থেকে জানা যায়, তিনি প্রায় ৩০ হাজার বিজ্ঞানী ও কর্মীদলের প্রধান ছিলেন। তিনি তাঁর বইয়ে স্মরণ করেছেন কীভাবে তাঁরা ‘আরো ভয়ংকর সংক্রামক’ রোগজীবাণু তৈরি করতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।
দীর্ঘদিন ধরেই প্রচুর খরচসাপেক্ষ পারমাণবিক অস্ত্রের পরিবর্তে তুলনামূলক সস্তা জৈব ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরিতে অনেক দেশের আগ্রহ লক্ষ করা গেছে – বিশেষ করে সেই সব দেশ, যারা এখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতায় পিছিয়ে রয়েছে; কিন্তু এ-ধরনের অস্ত্র শুধু রাষ্ট্র নয়, বেসরকারি সংস্থা কিংবা ব্যক্তিপর্যায়েও তৈরি করা অসম্ভব নয়। সুইস-মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ফ্রেড ইকেল যেমন বলেছেন, ‘ভয়ানক ধরনের জৈব মারণাস্ত্র তৈরির জ্ঞান ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে যেতে পারে হাসপাতাল ল্যাবরেটরি, কৃষি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য বেসামরিক রাসায়নিক কারখানার সর্বত্র। শুধু কোনো চরম একনায়ক সরকারই এ-ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টাকে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।’ অতীতে ঘটা এ-ধরনের কিছু ঘটনার আমরা চাক্ষুষ সাক্ষী – ১৯৮৪ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত গুরু রাজনিশের (যিনি তাঁর গৈরিক বসন ও পঞ্চাশটি রোলস রয়েস গাড়ির জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন) শিষ্যরা টাইফয়েড রোগের জীবাণু দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগনের ওয়াসকো কাউন্টিতে ৭৫০ জনকে মারাত্মক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত করেছিলেন। জাপানে ওম শিনরিকিও নামের কাল্ট সদস্যরা টোকিওর সাবওয়েতে সারিন গ্যাস নিয়ে হামলা করেছিলেন, যার ফলে ১২ জন নিরীহ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁরা এমনকি বটুলিনাম টক্সিন, অ্যানথ্রাক্স ও কিউ ফিভার সংক্রমণের জীবাণুও জোগাড় করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ২০০১ সালের ৯/১১ সন্ত্রাসী ঘটনার পরই দুজন সিনেটরসহ আরো কিছু গণমাধ্যম অফিসে সংক্রামক ও অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু ডাকযোগে পাঠানো হয়েছিল, যাতে মোট পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছিল। এ-ধরনের সন্ত্রাসী জৈব আক্রমণ যে-কোনো দেশে আরো বড় আকারে ঘটতে পারে – সে-আশঙ্কা এখনো ফিকে হয়ে যায়নি।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৭০ সালে তথ্য প্রকাশ করেছিল যে, কোনো শহরের ওপর উড়োজাহাজ থেকে বায়ুমণ্ডলে যদি পঞ্চাশ কেজি অ্যানথ্রাক্স জীবণু ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে তা অন্ততপক্ষে এক লাখ লোকের মৃত্যুর কারণ হবে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জেসন গ্রুপ এই জৈব হুমকির বিষয়টি আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, যদি সন্ত্রাসীরা নিউইয়র্ক সাবওয়েতে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ছড়িয়ে দেয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে? তেমনি মারাত্মক বিষাক্ত রাইসিন নামক রাসায়নিক পদার্থ মাত্র দশ মাইক্রোগ্রাম (এক গ্রামের একশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ একটা বড় সরিষার দানার সমান) হাজার হাজার সাবওয়েযাত্রীর জীবন হুমকিতে ফেলতে সমর্থ। এসব হুমকি ছাড়াও আমাদের সজাগ থাকতে হবে যেন ল্যাবরেটরি থেকে কোনো সুপ্ত বা সংরক্ষিত মারাত্মক সংক্রামক ভাইরাস বেরিয়ে আসতে না পারে। এমনই একটি ভাইরাস হলো বসন্ত বা ঝসধষষ চড়ী-এর ভাইরাস, যা বর্তমানে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা ও রাশিয়ার মস্কোতে
বিশেষ ব্যবস্থায় গবেষণাগারে সংরক্ষিত আছে। প্রায় চার দশক আগে বিশ্ব থেকে চূড়ান্তভাবে বসন্ত রোগ নির্মূলের পরও এর কিছু জীবাণু রেখে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে গবেষণায় প্রয়োজন হতে পারে – এই ভেবে। এই বসন্ত রোগ এতোটাই মারাত্মক ছিল যে, এতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের এক-তৃতীয়াংশই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন।
বর্তমান শতাব্দী শুরু হওয়ার আগে ঘটা প্রতিটি মহামারিই প্রাকৃতিক অণুজীব দিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই ছড়িয়েছে; কিন্তু বর্তমান শতকে এই মহামারির হুমকিতে যোগ হয়েছে গবেষণাগারে সৃষ্ট কৃত্রিম (Gene-modified) অণুজীবের সংক্রমণভীতি। এটি সম্ভব হয়েছে জৈবপ্রযুক্তি বা Biotechnology-র অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে। এখন পর্যন্ত আমরা কেউই সঠিকভাবে জানি না ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান প্রদেশ থেকে ছড়িয়ে পড়া ‘কোভিড-১৯’ নামক করোনা ভাইরাস কি একটি প্রাকৃতিক ভাইরাস, নাকি তা কোনো বায়োরিসার্চ ল্যাব থেকে ছড়িয়ে পড়া একটি কৃত্রিম ভাইরাস। মার্কিন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স ২০০২ সালের জুন রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল – ‘একটি উন্নতমানের গবেষণাগারে প্রবেশাধিকার রয়েছে, এমন কয়েকজন মাত্র জীববিজ্ঞানী খুব সহজেই বিধ্বংসী জৈব মারণাস্ত্র তৈরি করতে পারেন, যা মার্কিন জনগণের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেসব জৈব মারণাস্ত্র খুব সহজেই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা যায়, এমন যন্ত্রপাতি – যেমন ভেষজ, খাদ্য, পানীয় ও রাসায়নিকের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এভাবেই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্য নিয়ে নতুন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMD) তৈরি করা সম্ভব।’
নিউইয়র্কের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একার্ড উইমার ২০২০ সালে ঘোষণা করেছেন, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ইন্টারনেট থেকে ডিএনএ অণুর জেনেটিক নীলনকশা ডাউনলোড করে একটি কৃত্রিম পোলিও ভাইরাস তৈরি করেছেন। যেহেতু অধিকাংশ লোক আগেই পোলিরও প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করেছেন, তাই এই ভাইরাস তেমন কোনো মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু একই পদ্ধতিতে অন্যান্য ভাইরাস বা মিউট্যান্ট কপি তৈরি করা সম্ভব, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এইচআইভি, ইবোলা ইত্যাদি মারাত্মক ভাইরাস এভাবেই গবেষণাগারে তৈরি করা সম্ভব, যেমনটা উইমার করেছেন। উইমার বলেছেন, তিনি কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নয়, শুধু এর বিপদটি সবাইকে বোঝানোর লক্ষ্যেই এই পোলিও ভাইরাসটি তৈরি করেছেন। শিগগির ইন্টারনেটের মাধ্যমে এরকম আরো অনেক মারাত্মক ভাইরাসের জিন-নীলনকশা পাওয়া সহজ হয়ে যাবে, তখন এ-বিপদ আরো বাড়বে। জাপানের ওম শিনরিকিও গোষ্ঠী ১৯৯০ সালে চেষ্টা করেছিল আফ্রিকা থেকে প্রাকৃতিক ইবোলা ভাইরাসের নমুনা জোগাড় করতে; কিন্তু তারা তাতে বিফল হয়। এখন তারা নিজেরাই তা গবেষণাগারে বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারে। এ-কাজে তাদের সহায়তা করতে পারে শৌখিন জৈবপ্রযুক্তিবিদেরাও। একইভাবে এমনসব নতুন অণুজীব তৈরি করা সম্ভব, যেগুলো সব ধরনের জীবাণুধ্বংসী ওষুধ প্রতিরোধী (antibiotic resistant)। এ-ধরনের রোগজীবাণু অবশ্য multi resistant নামে প্রতিটি হাসপাতালেই রয়েছে, যা খুব দামি ওষুধ দিয়েও দমন করা কঠিন।
জিন প্রযুক্তিকে অবশ্য ভালো কাজেও লাগানো সম্ভব। যাঁরা হিউম্যান জেনোম সিকোয়েন্স তৈরি করেছেন, সেই সেলেরার সাবেক সিইও ক্রেগ ভেন্টর ঘোষণা করেছেন, তাঁরা পৃথিবীর দুটো বড় সমস্যা – জ্বালানিশক্তি সমস্যা ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন – এ-দুটোকে এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দূর করতে চান। তাঁরা এমন ধরনের নতুন অণুজীব তৈরির চেষ্টা করছেন, যা পানিকে তার গঠনকারী উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট করবে। এর মাধ্যমে যেমন পাওয়া যাবে হাইড্রোজেন জ্বালানি, তেমনি বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাই অক্সাইড কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে আনা সম্ভব। তাদের এ-পদ্ধতি যদি সত্যি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে তা হবে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। একইভাবে তৈরি করা সম্ভব প্লাস্টিক থেকে অণুজীব বা ছত্রাক, যা বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।
ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও ভুলবশত গবেষণাগারে দুর্ঘটনা ঘটে এসব অণুজীব আমাদের সংক্রমিত করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে Animal Conrol Cooperative Research Center-এ ২০০১ সালে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। রন জ্যাকসন ও ইয়ান র্যামশো ইঁদুরের প্রজনন হ্রাস করা নিয়ে কাজ করছিলেন। ইঁদুরের জন্মনিয়ন্ত্রণকল্পে তাঁরা mouse pox নামে একটি ভাইরাসকে বন্ধ্যাকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিলেন; কিন্তু দেখা গেল যে, সব ইঁদুরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই ধরনের ভাইরাস যদি মানুষের ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হয় তাহলে আমরা কী করব? একইভাবে গবেষণাগারে ন্যানোটেকনোলজির ব্যবহারও বিপদ ডেকে আনতে পারে। নিজেরাই নিজেদের প্রতিরূপ তৈরি করতে সমর্থ – এ-ধরনের ন্যানোটেকনোলজি মেশিন শুধু সূর্যালোকের শক্তি ব্যবহার করে ‘ম্যালথুসিয়ান লিমিট’ অতিক্রম করে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়ে চলতে পারে, যা মানুষসহ সমস্ত জীবজগতের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদিও এ-ধরনের সম্ভাবনাকে অনেকেই শুধু ‘রোমহর্ষক সায়েন্স ফিকশন’ অথবা কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিতে চান, তবে অন্যরা একে একটি অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা হিসেবেই দেখছেন।
প্রকৃতিতে যা কখনো ঘটা সম্ভব নয়, সেই কাজটি এখন বিজ্ঞানীরা নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তারা দুটো প্রজাতির জেনেটিক ম্যাটেরিয়েল একত্র করতে সক্ষম, যেমন – জেলিফিশের জিন স্থানান্তর করে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকা বানর বা ভুট্টা তৈরি করা সম্ভব। প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) কখনোই এভাবে দুটো প্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজনন করতে সক্ষম নয়। শিগগির এরকমভাবে জীবাণু ও ভাইরাসে জিন ট্রান্সফার খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। যেমনটা হয়ে দাঁড়াবে nanobot বা nanoreplicator। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে পরমাণু বিজ্ঞানীরা পরমাণু অস্ত্রের বিপদ দেখে যেভাবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন, এখন সেই একই আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন জৈবপ্রযুক্তি বিশারদরা। পৃথিবীর বুকে উল্কাপাত বা গ্রহাণুর আঘাত, ঝড়ঝঞ্ঝা, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো মানবসৃষ্ট মহামারির ভয়ও এখন একটি রূঢ় বাস্তবতা। যদি আমরা একে সফলভাবে মোকাবিলা করতে না পারি, তাহলে Doomsday Clock বা দুর্যোগ-ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাতের দিকে আরো এগিয়ে আসবে।

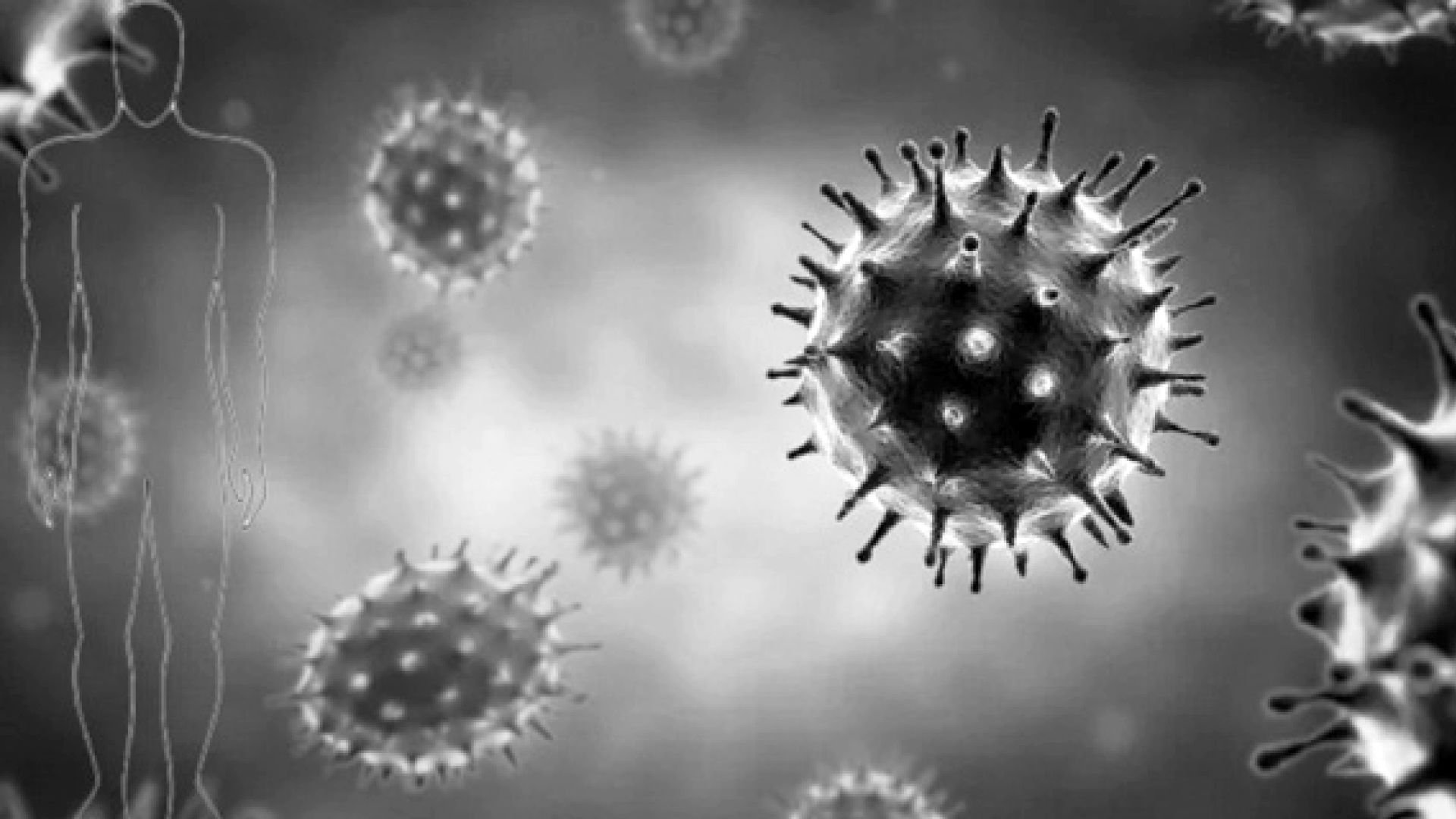
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.