কিছুদিন আগে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান স্মরণে অনলাইনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো – অনলাইনে, যেহেতু করোনা মহামারি আমাদের বাস্তব পৃথিবীকে ভেঙেচুরে এক উদ্ভট পরাবাস্তবে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যেখানে কায়ার হয়ে ছায়া কথা বলে, সেখানে সামাজিক দূরত্ব মানার জন্য জীবন্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তার ছবি। আয়োজকরা আমাকে অনুরোধ করলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের – আমাদের প্রতিদিনের সম্বোধনে, স্যারের – যে-কোনো একটি দিক নিয়ে যেন আমি আলোচনা করি। অনেক ভেবে আমি বললাম, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ পঠনে এবং গবেষণায় তাঁর অবদান নিয়ে বলতে পারলে আমি আনন্দিত হবো, যেহেতু এই একটি বিষয়ে তেমন বিস্তারে কেউ কিছু লেখেননি। কিছু সময় নিয়ে আমার ভাবার কারণ, স্যার ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ, যিনি এক সমৃদ্ধ গাছের মতো বহু ডালপালা মেলে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক সক্রিয়তা এবং সৃজনশীলতার অঞ্চলগুলিতে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য করে তুলেছিলেন। এরকম বহুজ্ঞ মানুষের কোন গুণটিকে আমি আলাদা করে বেছে নেব, তা নির্ধারণ করাটা একটা সমস্যাই ছিল আমার কাছে।
গাছের উৎপ্রেক্ষাতেই ফেরা যাক। আইরিশ কবি ডবিøউ বি ইয়েটস তাঁর ‘এমাং স্কুল চিলড্রেন’ কবিতাটিতে এক চেস্টনাট গাছের উদ্দেশে বলেছেন, তুমি কি পাতা, না পুষ্প, না কাণ্ড? অর্থাৎ একটা সজীব গাছকে কি তার কোনো বিশেষ অঙ্গ দিয়ে বিচার করা যায়, নাকি সবকিছু মিলিয়েই একটি গাছ তার উপস্থিতি মেলে ধরে? কবিতার শেষে তিনি একজন নৃত্যশিল্পী থেকে নৃত্যকে যে আলাদা করা যায় না, সে-কথাটি পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। আনিসুজ্জামান স্যারের ক্ষেত্রেও তো বলা যায়, তাঁর সব কাজকে সামুদায়িক বিচারেই দেখতে হবে, যেমন দেখতে হবে তাঁর কাজের সঙ্গে তাঁর জীবনকে মিলিয়ে। তিনি তো মূলত একজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোনো ঘরোয়া আড্ডায় বসতেন এবং আমরা তাঁর চমৎকার রসবোধে সিক্ত কোনো কৌতুক থেকেও কোনো শিক্ষা নিতাম, তখন তিনি তো শিক্ষকের কাজটিই করতেন। শিক্ষকের কাজ কী, এ নিয়ে স্যারের কোনো বক্তব্য চোখে পড়েনি। কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে, শিক্ষকও একটি গাছের মতো : তাঁর করণীয় সব কাজকে পাতায় পুষ্পে শাখায় সাজিয়ে সক্রিয়তার একাধিক অঞ্চলে তাঁকে থাকতে হয়। আদর্শ একটি সংজ্ঞায় শিক্ষক শুধু শেখান না, শুধু জ্ঞান বিতরণ করেন না, বরং জ্ঞানটা যাতে সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়, আলোর উৎস হয়ে দাঁড়ায়, তাও তাঁকে নিশ্চিত করতে হয়। শিক্ষক শুধু পাঠ দেন না, তিনি শিক্ষার্থীর রুচি গড়ে দেন, তাকে স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখান, তার পরিপার্শ্বকে নিজের অণুবিশ্বের অন্তর্গত করার উদ্দীপনা দেন। প্রাচীন পৃথিবীতে গুরুরা সেই কাজটি করতেন। আধুনিক দুনিয়ায় তাঁদের জায়গা নিয়ে নিয়েছেন বিষয়-বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা নিজেদের বিষয়ের বাইরে পা ফেলতে চান না। ফলে একজন অণুজীব বিজ্ঞানের ছাত্র সাহিত্য পড়ে না, সাহিত্যের ছাত্র গণিতের জগৎকে কারাগারের মতো ভয় পায়। স্যারের সান্নিধ্যে যারা যেতে পেরেছেন, যারা অনুষ্ঠানে, সভায় এবং সেমিনারে তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন আবার অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তাঁর কথা শুনেছেন, তারা বলবেন, কতভাবে তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন, তাদের মনের জানালাগুলি খুলে দিতে পারতেন।
আমি তো অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের ছাত্র ছিলাম না। তাঁর সাথে আমার পরিচয়ও গত শতকের মধ্য-আশির আগে নয়, কিন্তু তিনি কী করে আমার শিক্ষক হয়ে গেলেন – শুধু স্যার নন, শিক্ষক – তার উত্তরে এটুকু বলা যায়, আমার অনেক চিন্তাকে তিনি সক্রিয় হতে সাহায্য করেছেন, আমার জানাশোনার পরিধিটাকে প্রসারিত করেছেন এবং একই সঙ্গে আধুনিকতা যে পশ্চিম থেকে আমদানি করা কোনো পরিচিতি-মোড়ক নয়, বরং নিজ ভূমিতে শক্ত একটি পা রেখে চলমান সময়কে ছোঁয়া এবং তাতে উৎপাদিত চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বদর্শন থেকে নিয়ে প্রযুক্তি, তত্ত্ব ও জীবনকলাতেও একটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বৌদ্ধিক শক্তি, তা নির্ণয়ে সাহায্য করেছেন। এই আধুনিকতা তাঁর জীবনে ছিল, তাঁর কাজে ছিল, তাঁর আচরণে তো বটেই; কিন্তু তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণার জোগান দিত বাঙালির ঐতিহ্য।
মুসলমান বাঙালির মনকে তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, মধ্যযুগের অনেক মুসলমান কবির আধুনিকতা আমাদের সময়ের শিক্ষিত অনেক মানুষের মধ্যে নেই। কেন নেই? কারণ এরা মনকে সংকীর্ণ করেছেন ধর্ম, জাত্যাভিমান, গোত্র এসবের মাপে ফেলে, সংস্কৃতির উদার উত্তরাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে। স্যার দেখিয়েছেন, সংস্কৃতির একটা বহুমাত্রিকতা আছে, বহু সংস্কৃতির মিলনে সংস্কৃতির পরিচয়টি স্থান-জাত-গোত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে বহুজনের অধিকারে যায় এবং তখন আধুনিকতার সূত্রগুলি সে ধারণ করতে থাকে। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদে স্যারের আস্থা তাঁকে মধ্যযুগের, আঠারো-উনিশ শতকের এবং আমাদের সময়ের বাঙালি মুসলমানদের শক্তি ও দুর্বলতাকে চিহ্নিত করার বিষয়টি সহজ করে দিয়েছিল।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটা সহজাত প্রতিভা ছিল আলাদা আলাদা অনেক বিষয়কেও সামূহিকতার দৃষ্টিতে দেখার। তিনি কখনো রাজনীতির মাঠে নামেননি, কিন্তু বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনে যখন সক্রিয় অংশ নিলেন, অথবা তার আগে যুবলীগে যোগ দিয়ে এর দফতর সম্পাদকও হলেন – যদিও ওই যুবলীগ ছিল কমিউনিস্ট ভাবধারার একটি সংস্কৃতিপ্রধান সংগঠন – তিনি তো রাজনীতিই করেছেন। কিন্তু রাজনীতিকে স্যার কোনো ছাপমারা বাক্সে ফেলে বিচার করেননি, বরং এক সামূহিক দায় হিসেবে দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন এর বিকাশ হবে সংস্কৃতি ও শিক্ষার দর্শনের মধ্য দিয়ে, লোকহিত এবং মানবকল্যাণ হবে এর উদ্দেশ্য এবং যাতে যুক্ত হবেন অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, আইন এবং এরকম অনেক বিশেষজ্ঞতার অঞ্চল থেকে আসা চিন্তক ও চর্চাকারীরা। বলা বাহুল্য, এই রাজনীতির প্রয়োগ আমাদের দেশে, অথবা ভূভারতে দেখা যায় না। কিন্তু এই রাজনীতিকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একটি আদর্শ হিসেবেই দেখেছেন। একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আদর্শ বিষয়টা বিমূর্ত হতে হতে অপ্রয়োগযোগ্য কোনো কিছু হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বলেছিলেন, আদর্শবাদের ক্ষেত্রে সেটি হতে পারে, কিন্তু আদর্শের একটা শক্তি হলো এর প্রয়োগযোগ্যতা। কোনো আদর্শই বিমূর্ত হতে পারে না। যারা এটিকে ভয় পায়, বুলির অঞ্চলেই শুধু রাখে, কাজে ফলাতে সাহস পায় না, অথবা চায় না, তাদের হাতে আদর্শ অস্বচ্ছ একটি বিমূর্তে পরিণত হয়।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যে রাজনীতিকে আদর্শ মানতেন তাতে ঐতিহ্য থেকে সংস্কৃতিসাধনাও যুক্ত হয়েছিল। সেজন্যে কেউ কেউ তাঁর রাজনীতি নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিত। যেমন বিপুলা পৃথিবীতে তিনি তাঁর এক শিক্ষকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, ১৯৭৫-এর শেষ দিকে তিনি তাঁকে সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন, যেন দেশকে কিছু দিতে পারেন। যেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে শিক্ষা সচিব হিসেবে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতাটা তাঁর কাছে সরকারি কাজ থেকেও মূল্যবান ছিল বলে তিনি সেই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেননি, তাঁর শিক্ষকের প্রস্তাবও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওই শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে বলেছিলেন, ‘আনিস খুব রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছে।’ (২১৩) স্যারের শিক্ষক যে-রাজনীতির চিন্তা করেছেন তা দলীয়, সংকীর্ণ এবং কৃপণ; এটি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে সাক্ষী মানে, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ঠাট্টা করে যাকে ‘পলিটিক্স’ বলতেন। ‘রাজনীতিতে এখন পলিটিক্স ঢুকে গেছে’ – তাঁর এই মন্তব্যটি একটি আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। ওই রাজনীতিতে কোনোদিন তাঁর সায় ছিল না, চর্চা করা তো বহু দূরের কথা।
স্যারকে নিয়ে আলোচনায় রাজনীতির উল্লেখটা এজন্যে জরুরি যে স্যারের ওই শিক্ষকের মতো অন্য অনেকে রাজনীতি সম্বন্ধে একটা চলতি বা বাজারি ধারণা থেকে স্যারের অনেক কাজে রাজনীতি খুঁজতেন। তিনি যখন কবি সুফিয়া কামাল ও বিবেকের প্রশ্নে অটল অন্য অনেকের সঙ্গে গণআন্দোলনে যোগ দিলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে পথে নামলেন, আদালতেও সাক্ষ্য দিলেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেন, একসময় ‘বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও’ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন, কওমি স্বার্থের রক্ষকরা, সাম্প্রদায়িক এবং রক্ষণশীল কট্টরপন্থীরা ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়-অবিচার-অধর্মের বিরুদ্ধে স্যারের বিবেকবান অবস্থানকে দলীয় রাজনীতির অথবা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঘষা কাচ দিয়ে দেখল। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ চিন্তার মানুষের কোনো কমতি নেই। এদের দেখা যায় নানা পেশায়; শিক্ষক ও গবেষকদের সভায়ও।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নিজের জবানিতে, রাজনীতি, সমাজ, মানুষ ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর চিন্তাগুলি গড়ে দিয়েছিল তাঁর জীবন শুরুর কিছু ঘটনা ও সিদ্ধান্ত। তাঁর বয়স যখন নয় তিনি কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছেন, মানুষকে মানুষের হাতে শুধু ধর্ম ভিন্ন হওয়ার কারণে খুন হতে দেখেছেন। এক বছর পর দেশ বিভাগ হলে পরিবারের সঙ্গে খুলনা হয়ে ঢাকা এসে তিনি নতুন জীবন শুরু করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ এবং দেশান্তর তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। সেই থেকে তিনি ধর্ম-বর্ণের মাপে মানুষকে বিচার করাকে মানবসমাজের একটা ভয়ানক রোগ হিসেবে দেখেছেন। আর দেশভাগের পেছনে যে একটা উপনিবেশী কারসাজি ছিল, ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ রেখা টেনে দুটি স্বাধীন দেশের ওপর উপনিবেশী কর্তৃত্ব বজায় রাখার একটা পরিকল্পনা ছিল তাও তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন। স্যারকে আমি যেটুকু দেখেছি, তিনি যে-কোনো বিষয়ের গভীরে পৌঁছে এমন কিছু অঞ্চলে আলো ফেলতে পারতেন, যা অনেকেরই দৃষ্টি বা উপলব্ধি এড়িয়ে যেত। দেশ বিভাগ এবং নব্য-ঔপনিবেশিকতাকেও তিনি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই যখন পাকিস্তানি উপনিবেশী দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকট হতে শুরু করে, এবং ইংরেজদের মতো ভাষাদখল দিয়ে এর প্রতিফলন ঘটতে থাকলো (ইংরেজরা অবশ্য এ-কাজটি করতে কয়েক দশক সময় নিয়েছিল), তিনি এই অপচেষ্টাটি সংস্কৃতি দিয়েই প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সের এক স্কুলছাত্র যে ভাষা-আন্দোলনে যোগ দিলেন, তার পেছনে আবেগ থেকেও বেশি ছিল যুক্তি। যুবলীগে নাম লেখানোর পেছনেও ছিল একই যুক্তি।
যে-রাজনীতির চলৎশক্তি জোগায় সংস্কৃতি; অথবা ভিন্নভাবে বললে, যে-সংস্কৃতি রাজনীতিকে যেকোনো অচলায়তনের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়, তাতে স্যারের যে-আস্থা ওই অল্পবয়সে জন্মেছিল, জীবনের শেষে এসেও তাতে কোনো চিড় ধরেনি। তাঁর চারটি স্মৃতিকথামূলক বই আমার একাত্তর (১৯৯৭), কাল নিরবধি (২০০৩), চেনা মানুষের মুখ (২০১৩) ও বিপুলা পৃথিবী (২০১৫) সাক্ষ্য দেয়, তিনি রাজনীতিতে সংস্কৃতির প্রতিফলন অনুপস্থিত হতে থাকলে সংস্কৃতির ওপরই আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এবং সংস্কৃতি বলতে, আবারো বলি, সেই চর্চা যা বহুজনের, যাতে বিত্ত বা শ্রেণির বিষয়টি মোটেও বিবেচ্য নয় এবং এর প্রভাব শুধু নান্দনিক চর্চা বা কাজে নয়, বরং যা কিছু সৃষ্টিশীল, মানবমুখী, কল্যাণকর এবং ন্যায় ও বিচারের পক্ষে প্রতিবাদী, তাতে ব্যাপকভাবে অনুভূত। পটুয়া কামরুল হাসানের একটা গল্প স্যার আমাদের একবার শুনিয়েছিলেন। কোনো একটা স্বাস্থ্য-সমস্যা হলে কামরুল হাসান এক ডাক্তারের কাছে গেলেন। এবং ভালোও হলেন। পরে জানা গেল তিনি গিয়েছিলেন পুরানা পল্টনের এক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের কাছে। স্যার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর শুভানুধ্যায়ী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বাদ দিয়ে কেন তিনি ওই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। কামরুল হাসান হেসে বলেছিলেন, ভদ্রলোকের চিকিৎসায় সংস্কৃতি আছে। তিনি গান শোনেন, বই পড়েন, ছবি কেনেন এবং পুরানা পল্টনের বিপন্ন শিশুদের দেখাশোনা করেন। তাঁর হাতে চিকিৎসা পেলে ভালো তো হতেই হয়। স্যারের বাবাও তো একজন হোমিও চিকিৎসক ছিলেন, সংস্কৃতিকেও তিনি মূল্য দিতেন। হয়তো কামরুল হাসানের এই গল্পটি বলতে তিনি আনন্দ পেতেন, কারণ তাতে তাঁর বাবাকেও তিনি সম্মান দেখাতে পারতেন।
স্যার যে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রতি অল্প বয়সেই ঝুঁকে পড়েছিলেন, তার কারণ তাঁর এই বোধ যে, কোনো সংস্কৃতিই একক বিশিষ্ট নয়, সংস্কৃতি মানেই মিলন, বহুপথ একটা জায়গায় এসে মেশা, বহু মন একে অপরের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে তাঁর সম্পৃক্ততার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে সংস্কৃতির বাহন করা, যে-সংস্কৃতি একজন শিক্ষার্থীর ভেতর থেকে তৈরি হবে, একটা বীজ যেমন একসময় একটা বৃক্ষে পরিণত হয় তেমনি। যারা শিক্ষাকে সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে গ্রহণ করেছে, পরিশ্রুত হয়েছে, রুচিটা উন্নত করেছে, তাদের প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা আমি সবসময় লক্ষ করেছি। অন্যদিকে, যাদের মধ্যে রুচির অভাব ছিল, তারা যতই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকুন না কেন, তাদের তিনি এড়িয়ে চলতেন। একবার এক আলাপচারিতায় এক কবি স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কি তরুণদের রুচি অশুদ্ধ করে দিতে পারে। স্যার হেসে বলেছিলেন, যেহেতু এই মাধ্যমে সক্রিয় চিন্তার জায়গাটা কম, ফলে এটি সক্রিয়ভাবে কারো রুচি নষ্ট করতে পারে না, তবে রুচির ঘরে যেখানে যেখানে অন্ধকার আছে, তাকে আরো গাঢ় করে দিতে, রুচির অভাব থাকলে তাকে বাড়িয়ে একসময় ছোটখাটো একটা দুর্ভিক্ষও বাধিয়ে দিতে পারে।
আশির দশকের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের পাঠ্যসূচিতে যখন আমরা কয়েক তরুণ শিক্ষক কিছু পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলাম, যার মধ্যে ছিল থিওরি এবং সংস্কৃতি পঠনের অন্তর্ভুক্তি, মনে আছে কলাভবনের শিক্ষক লাউঞ্জে আমি এবং আমার সহকর্মী ফকরুল আলম স্যারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। স্যার যে শুধু জোর সমর্থন দিলেন তা নয়, কোন চিন্তাভাবনাগুলির দিকে বেশি নজর দিতে হবে তারও একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলেন। স্যারের পড়াশোনার ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। আমাকে যা তাঁর গুণগ্রাহী করেছিল, তা ছিল তাঁর উদারচিত্ততা। নতুন ভাবনা-চিন্তা, বিশেষ করে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ জানায়, অনেক সময় অস্বীকারও করে বসে, সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে প্রথমে বাজিয়ে দেখতে তাঁর আগ্রহ ছিল। পছন্দ না হলে তিনি হয়তো বলতেন, ‘নট মাই কাপ অফ টি।’ কিন্তু জেনেশুনে, পড়ে-বুঝে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন নতুন চিন্তা প্রকৃতই নতুন, নাকি কোনো পুরনো অসন্তোষের নতুন প্রকাশ অথবা আধা-সেদ্ধ কোনো ভাবনা। আমাদের পাঠক্রমে উত্তরাধুনিক সাহিত্য যোগ হলে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন তাঁকে দু-একটি উত্তরাধুনিক উপন্যাস দিতে, পড়ে দেখার জন্য।
উত্তরাধুনিকতা স্যারের চায়ের পেয়ালা না হলেও এর সম্ভাবনাগুলি তিনি স্বীকার করতেন। বিশেষ করে সংস্কৃতির উচ্চ-নিচ বিভাজনের বিপক্ষে এর অবস্থানকে।
স্যারের সঙ্গে দেশের বাইরে সভা-সেমিনারে অংশ নেওয়ার সুযোগ আমার কয়েকবারই হয়েছে এবং প্রতিবারই দেখেছি, অল্প কথায় অনেক মৌলিক বিষয়ে তিনি তাঁর চিন্তাগুলি সাজিয়ে পরিবেশন করতেন। ২০১১ সালের মে মাসে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে। ওই সেমিনারে স্যার যে-ভাষণ দেন, তার বিষয় ছিল ‘রবীন্দ্রনাথের দর্শন’। চমৎকার এবং প্রাঞ্জল ইংরেজিতে স্যার যে-কথাগুলি বলেছিলেন, তার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা এবং জাতীয়তাবাদ বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা যা পশ্চিমের প্রচলিত বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন এক পাঠ উপহার দিয়েছিল। বক্তৃতাটি শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, স্যার নিজে যে-আধুনিকতার চর্চা করতেন, তাতে সময়ের নির্যাসকে ধারণ করে এবং বাঙালিয়ানার নিরিখে তাকে ফেলে নিজস্ব একটি চরিত্র ও প্রকৃতি নির্মাণের ঐকান্তিকতাটাই ছিল মূল লক্ষ্য। এটিকে তিনি সমন্বয়বাদীও বলতেন, তবে তাতে নিজস্বতাটা যেন হারাতে না হয় সেদিকে নজর দেওয়ার ওপর জোর দিতেন। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের চিন্তায় কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রান্তের ওপর যে প্রাধান্য দেওয়া-নেওয়া, মিলন ও মেলানোর যে-উদ্দেশ্য, তাতে বহুসংস্কৃতির বিষয়টি নিশ্চিত হয়। স্যার বলতেন, রবীন্দ্রনাথ নিত্য প্রেরণাদায়ী। প্রেরণা দেওয়ার কাজটি স্যার নিজেও করেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে গিয়েছেন, এমন মানুষ মাত্রই তা বলবেন।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের জ্ঞান সাধনার একটি দিক ছিল বাঙালিকেন্দ্রিক। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বাঙালির বাঙালি হয়ে-ওঠা এবং কিছু বাঙালির বাঙালিয়ানাকে অস্বীকার করে – এবং অন্য কোনো পরিচয়কে সার্বিকভাবে ধারণ করতে না পেরে – নিরাবলম্ব হয়ে পড়ার বিষয়টি। আশির দশকে নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক সেলিম আল দীনের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা বাড়ে এবং তিনি আমাকে মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী করেন। বইপত্রের জোগানও তিনি দিতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জীবনে মধ্যযুগ নিয়ে একটা মোটামুটি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে-পড়াশোনার প্রয়োজন, তা করার মতো সময় আমার ছিল না। সেলিম আল দীনও পড়াতেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর সঙ্গে দেখা হতো কালেভদ্রে। এজন্য মধ্যযুগ নিয়ে আর কে আমাকে বিশদ বলতে পারেন, তার সন্ধানে নামলাম।
একদিন কলাভবন লাউঞ্জে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে দেখলাম কয়েক তরুণ শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর একটা চুম্বক-শক্তি ছিল মানুষকে, বিশেষ করে তরুণদের আকর্ষণ করার। একসময় শ্রোতাদের ভিড় কমলে রাজ্জাক স্যারের কাছে মধ্যযুগ নিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, ‘আনিসুজ্জামানের কাছে চইলা যান। সব উত্তর পাইবেন।’
সব উত্তর পাওয়ার জন্য প্রশ্নগুলিও সুনির্দিষ্ট এবং সুচিন্তিত হতে হয়, কিন্তু তা করার যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে যতবারই স্যারের সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে আলাপ হয়েছে, তিনি নিজেই যেন আমার জন্য প্রশ্নগুলি তৈরি করে সেগুলির উত্তর দিয়েছেন। স্যারের এই গুণটি আমাকে অবাক করত। কীভাবে যেন তিনি শিক্ষার্থীদের অভাবগুলি বুঝতে পেরে সেগুলি পূর্ণ করে দিতেন, তাকে কোনোরকম সংকোচ বা অস্বস্তিতে না ফেলে! তাঁর মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, যা ছিল তাঁর পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয়বস্তু, আমার পড়া ছিল। কিন্তু এরকম গবেষণায় যা হয় : যেটুকু অভিসন্দর্ভে – বা অভিসন্দর্ভভিত্তিক বইয়ে দেওয়া যায়, তার বাইরে অনেক কিছুই নোটের আকারে রয়ে যায়। অভিসন্দর্ভটি (এবং বইটি) অবশ্য ছিল সময়নির্দিষ্ট – ১৭৫৭ থেকে ১৯১৮। কিন্তু এটি পড়তে গিয়ে মুসলিম-মানস তৈরির বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি, বিশেষ করে শাহী আমল সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়ে। পরে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে স্যারের দু-একটি প্রবন্ধ পড়লাম। স্যারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমার ধারণা হয়েছিল, মধ্যযুগের বাঙালির যে বিশ্বদর্শন ছিল, তা থেকে আমাদের সময়ে এসেই যেন অনেক বাঙালি ঘরকুনো হয়ে গেল। মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমান কবি-লেখকরা নিজেদের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হয়েও ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে গ্রহণের মানসিকতাটা দেখাতে পেরেছেন, লোকজ প্রজ্ঞার সঙ্গে আহরিত সমকালীন জ্ঞানকে মেলাতে পেরেছেন। বহু-ধর্ম ও বহু-দর্শনের নির্যাসকে ধারণ করা, যাকে ইংরেজিতে syncretism বলা যায়, যা আদতে একটা সমন্বয় প্রচেষ্টা, তা মধ্যযুগের মুসলমান কবি-লেখকদের বিশিষ্ট করেছিল। এই প্রয়াসটি মধ্যযুগের বা তার পরবর্তী দুশো বছরের হিন্দু কবি-লেখকদের মধ্যে তেমন লক্ষ করা যায় না। স্যার এজন্য সৈয়দ সুলতান, চাঁদ কাজি বা দৌলত কাজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁরা যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ধরে রাখতে পেরেছিলেন, সে-কথাটা উল্লেখ করতেন। স্যারের সঙ্গে যে ক’বার মধ্যযুগ থেকে নিয়ে কুড়ি শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি – সংখ্যায় চার বা পাঁচবার হয়তো হবে – তাতে আমি এমন কিছু জেনেছি যা সাহিত্য-ইতিহাসের বইয়ে হয়তো পাওয়া যাবে না।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের পঠন-পাঠন ও আগ্রহের অঞ্চলগুলিতে শিল্পকলা যে অগ্রাধিকার পেত, সেটি যখন একসময় বুঝতে পারলাম, এ-বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা জানতে আগ্রহী হলাম। যারা স্যারের বাসায় গিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় অথবা গুলশানে, তারা জানেন পেইন্টিং ও ড্রয়িংয়ের একটি ছোটখাটো, কিন্তু সমৃদ্ধ সংগ্রহ তাঁর ছিল। কামরুল হাসান এবং সফিউদ্দীন আহমেদ থেকে নিয়ে তরুণ অনেক শিল্পীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। তবে শিল্পকলা নিয়ে লেখালেখিতে তাঁর সক্রিয়তা আমার চোখে পড়েনি। অনেক পরে কবি ও কালি ও কলম সম্পাদক আবুল হাসনাত আমাকে বলেছেন, শিল্পকলা নিয়ে স্যারের ন’টার মতো লেখা তিনি সংগ্রহ করেছেন। শিল্পীদের প্রদর্শনীপত্রে স্যার মাঝেমধ্যে লিখেছেন, প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষেও তাঁদের কাজ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। সেজন্য শিল্পকলার কোন বিষয়গুলি তাঁকে আকৃষ্ট করে, জানার একটা আগ্রহ ছিল। সেই সুযোগ হাসনাত ভাই-ই সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি তখন সংবাদ সাময়িকীর সম্পাদক, এবং এর একটা সংখ্যার জন্য আমাকে পটুয়া ঐতিহ্য নিয়ে কিছু লিখতে বললেন। তিনিই আমাকে পরামর্শ দিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে। একদিন স্যারের অনুমতি নিয়ে তাঁর অফিসকক্ষে গেলাম এবং সত্যিকার অর্থে ঋদ্ধ হয়ে ফিরলাম। স্যার বেঙ্গল স্কুল ও শান্তিনিকেতনের কলাভবন, পাহাড়ি চিত্রকলা, মোগল মিনিয়েচার এবং পটচিত্রের কালীঘাট ও বাংলাদেশে চর্চার ঐতিহ্য নিয়ে বললেন। এসব বিষয়ে তাঁর জানাশোনার একটাই কারণ ছিল : আগ্রহ, পড়াশোনা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অপূর্ব সমাবেশে সৃষ্ট উদ্যোগ, যা তাঁকে ঐতিহ্যের পর ঐতিহ্যে নিয়ে গেছে। একবার একটা সাহিত্য-সেমিনারে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলে এটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখার একটা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্যার নিজ থেকেই বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক স্বপন মজুমদারকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন যেন তিনি আমাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেন। তবে স্বপন মজুমদারের সঙ্গে প্রথম দিনেই পরিচয় হয়ে গেলে স্যারের চিঠি আর তাঁকে দিতে হয়নি। পরে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যে-বইটি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশ করে, যা ছিল রবীন্দ্রনাথকে ‘বাংলাদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি’, তাতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে তিনি আমাকে একটি লেখা দিতে বলেন। আমি সে-অনুরোধ রাখতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম।
শিল্পকলার একটি দিক নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হতো এবং তা ছিল এতে উপনিবেশবাদের প্রভাব এবং উত্তর-উপনিবেশী চিন্তা। পশ্চিমা শিল্পকলা নিয়ে স্যারের চিন্তাভাবনা আমার কখনো জানা হয়নি, যেহেতু আমরা কথা বলেছি বেঙ্গল স্কুল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চিত্রকলা নিয়ে। ২০০৪ সালে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবুল খায়ের লিটু যামিনী নামে একটি আন্তর্জাতিক আর্ট ম্যাগাজিন প্রকাশনা শুরু করেন এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। সম্পাদকমণ্ডলীতে আমিও ছিলাম। ফলে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের গুলশানের একটি অফিসে মাঝেমধ্যেই স্যারের সঙ্গে দেখা হতো। তাঁর এক বড় গুণ ছিল, যে-কাজই তিনি করতেন আন্তরিকতার সঙ্গে, নিখুঁতভাবে, তা করতেন। তাঁর আরেক গুণ ছিল নিয়মানুবর্তিতা। যামিনীর জন্য তিনি সপ্তাহে একদিন বরাদ্দ রেখেছিলেন। ম্যাগাজিনটি বেরুতো ইংরেজিতে, প্রথমে এটি ছিল ত্রৈমাসিক, পরে ষান্মাসিক, এরপর অনিয়মিত, একসময় এটি পাতা মুড়ে ইতিহাসে চলে গেল। ছাপা হওয়ার জন্য জমা নেওয়া প্রবন্ধগুলি স্যারকে আমরা দেখাতাম, তাঁর মন্তব্যের জন্য। তিনি এই উপমহাদেশ এবং আমাদের চিত্রকলা নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিলেন। আমাদের বলতেন, আমাদের শিল্পীদের পশ্চিমা শিল্পীদের অনুকরণ করা উচিত নয়, এতে মনের উপনিবেশমুক্তি ঘটবে না। বরং নিজেদের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে, যেমন দিয়েছিলেন জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান, একটা নিজস্ব শিল্পধারা তৈরি করা সম্ভব।
মনের উপনিবেশমুক্তি কথাটা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের বিশ্বাসে একটা বড় জায়গা নিয়ে ছিল। যেসব শিল্পী আধুনিকতার ঢেউটি গায়ে লাগিয়েও মূল ভূমিতে দাঁড়াতে পারতেন, তাঁদের তিনি প্রশংসা করতেন। তবে এই বিচারটি তিনি নিজের মধ্যেই রাখতেন, অথবা আমাদের মতো যারা একটা অ্যাকাডেমিক আগ্রহ থেকে তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করতাম, তাদের সঙ্গে ভাগ করতেন। নান্দনিক-নৈতিক কারণে নেহাত প্রয়োজন না হলে তিনি কারো মূল্যবিচারে যেতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এতে কোনো ব্যক্তির কাজের নিরপেক্ষ একটি মূল্যায়ন যতটা না হয় তার থেকে বেশি হয় বিচারকারীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অথবা কোনো পক্ষ গ্রহণের প্রতিফলন।
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মনেপ্রাণে একজন আধুনিক মানুষ ছিলেন – আধুনিক অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত, যুক্তিবাদী, ইহজাগতিকতার কাঠামোয় সমাজ ও সময়কে দেখতে আগ্রহী, পরিমিতিবোধসম্পন্ন, আবেগকে বুদ্ধির শাসনে রাখতে বিশ্বাসী এবং যুক্তির অভ্যস্ত এবং পরিশীলিত চর্চা ও রুচির নান্দনিকতায় একনিষ্ঠ একজন মানুষ। একই সঙ্গে আধুনিকতার যে কিছু পক্ষাবলম্বন থাকে, কিছু কাঠামোকে যে তা মহিমা দেয় এবং অনাধুনিক বিবেচনা করে ঐতিহ্যের অনেক অঞ্চলে বেড়া তুলে দেয়, সেসব নিজে তিনি যেমন পরিহার করতেন অন্যদেরও তা করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি শ্রেণি, বর্ণ ও বিত্তকে মূল্য দিতেন না, পুরুষতান্ত্রিকতার অনেক দাবিকে অস্বীকার করতেন এবং কোনো কাঠামোকে মানুষের ওপরে স্থান দিতেন না। এজন্য তাঁর সান্নিধ্যটা সকলের জন্য এত কাঙ্ক্ষিত ছিল। তিরাশি বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণকে তাই অকালপ্রয়াণই বলতে হয়। তাঁকে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল। মহামারি-উত্তর বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সমাজ ও শিক্ষার নতুন বিকাশের জন্য তাঁর দিকনির্দেশনার প্রয়োজন ছিল।
তবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যা রেখে গেছেন তা কাজে লাগাতে পারলে তাঁর প্রয়াণে যে ক্ষতি হয়ে গেল তা কিছুটা অন্তত কাটিয়ে ওঠা যাবে।
আমি নিশ্চিত এই স্মারক গ্রন্থটি ওই প্রয়াসে একটা সুন্দর ভূমিকা রাখবে।
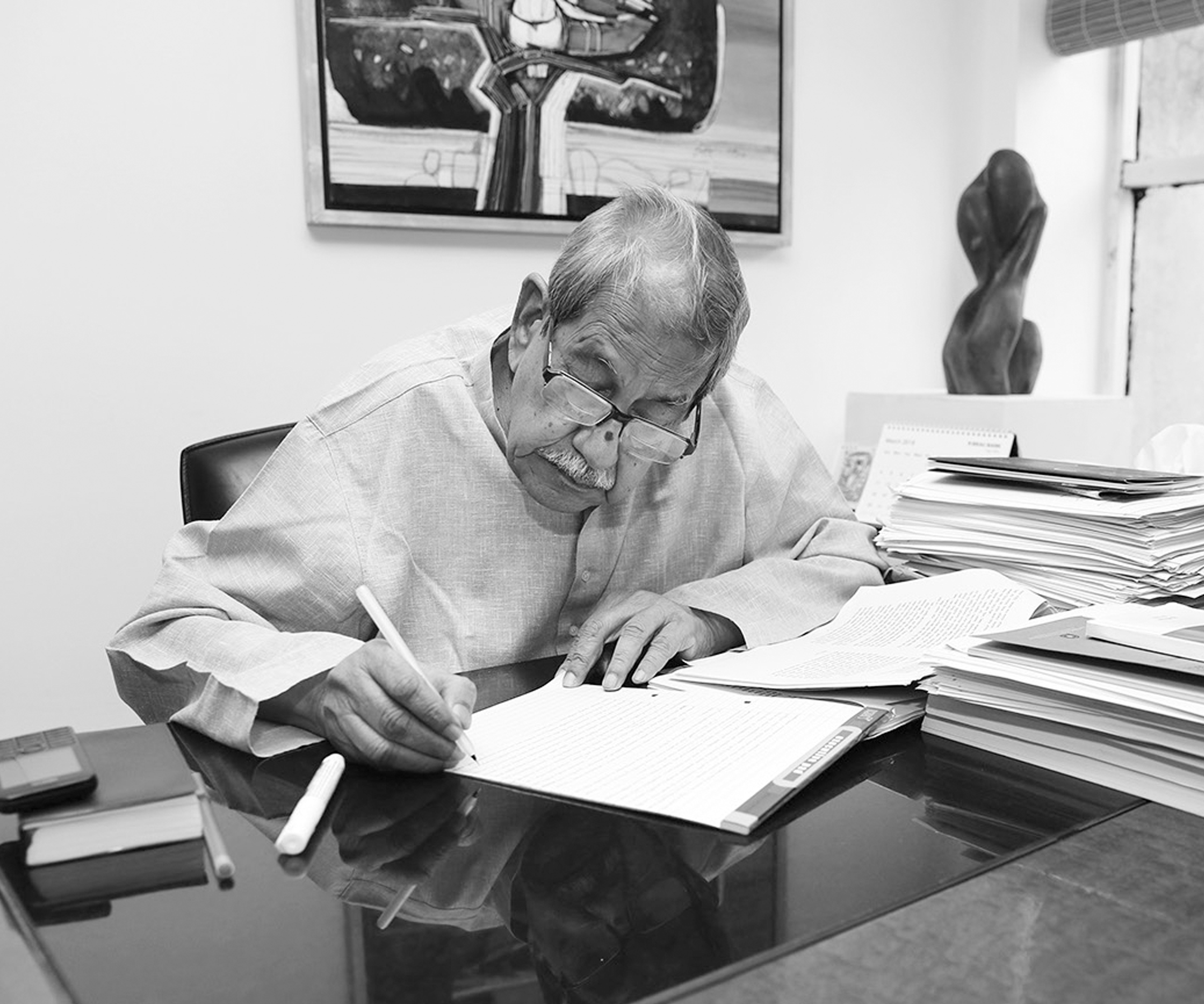

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.