তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতো অসীম রায়ের ডায়েরিও বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তো সেই ডায়েরিতে ষাটের দশকের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ লেখকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অসীম রায় প্রশংসা করে হাসান আজিজুল হকের কথা লিখেছিলেন। বেশ জোরের সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন যে, হাসানের ‘ভাষার উপর দখলটা বেশ ভালো।’ খুশিও হয়েছিলেন এইটা জেনে যে, তরুণ হাসান তো ‘আসলে বর্ধমানের ছেলে।’ সেই তরুণ হাসান, যাঁর গল্প কি না ছাপা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের এক্ষণের মতো পত্রিকায়। এ-কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, একেবারে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকেই হাসান পাঠক-সমালোচক থেকে শুরু করে অগ্রজ লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন আর তাঁর সেই সাহিত্যিক উদ্ভাসনের প্রক্রিয়া আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। উদ্ভাসিত সেই রূপটি, সেটা যেমন হাসানের ছোটগল্পে দেখা যায়, তেমনই তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধে। এমনকি জীবনের শেষবেলায় রচিত স্মৃতিকথার বিভিন্ন খণ্ডেও তার শিল্পসৌকর্য দেখতে পেয়ে আমরা বারেবারে মুগ্ধ হয়েছি।
দুই
শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় প্রস্তুতি আর পরিচর্যার যেমন একটা ব্যাপার থাকে, তেমনই থাকে আত্মসচেতনতার একটি ব্যাপার। সেই আত্মসচেতনতার সূত্র ধরেই আসে একজন লেখকের সাবালকত আর আত্ম-উপলব্ধি। বাংলা কথাসাহিত্যে হাসান আজিজুল হকের মধ্যে এই ব্যাপারটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একেবারে শুরু থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। এ-প্রসঙ্গে অসীম রায়ের কথা নানা কারণে বারেবারেই আমাদের মনে হতে থাকে। তিনি একজন লেখকের ‘প্রতিভার অস্তিত্ব’কে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর অন্বেষণ, তাঁর চিন্তার বিভিন্ন দিক, তাঁর নানাবিধ দ্বন্দ্ব – এগুলোও যে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, সেটি মেনে নিয়েছিলেন। এসব তো নানাভাবে হাসানের লেখকজীবনের বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখতে পাই। সেইসঙ্গে আরো দেখতে পাই, তাঁর সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তার একটি সাশ্রয়ী সমন্বয়। দেখতে পাই, বেগবান আবেগের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধির এক পরিশীলিত রূপায়ণ।
অসীম রায়ের মতোই হাসানও মনে করতেন যে, তাঁর লেখার উৎস হচ্ছে মানুষ। কোন মানুষ? না, একেবারে বাস্তব মানুষ। যে-মানুষ হাসানের চারপাশে ঘুরছে-ফিরছে-হাসছে-কাঁদছে-প্রতিবাদ করছে, সেইসব মানুষ। কায়েস আহমেদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসান আজিজুল হক বলেছিলেন, ‘আমার প্রতিটি গল্প আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো গল্প আমি লিখি না।’ হাসানের ‘খনন’ গল্প থেকে এক টুকরো উদ্ধৃত করছি – মুনীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, যাদের জমি নেই, তারাই খাল কাটার কাজে নিজেদের শ্রমটা খুব শস্তায় বেচে দিচ্ছে – এটা ঠিক। বাংলাদেশের প্রায় আধাআধি লোকের জমি নেই তা-ও ঠিক। কাজেই খালের ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে জমির মালিকদেরই লাভ। যে বেচারারা খাল কেটে মরলো তাদের কোনো লাভ নেই। এসব কথা ঠিকই। কিন্তু একথাটাও তো ঠিক যে, উৎপাদন বেড়ে যাবে। ধরুন, ধানের উৎপাদন যা আছে, তা যদি বেড়ে যায়, তাহলে গরিব মানুষের কোনো উপকার হবে না?
এ-কথার উত্তরে – শাহেদ শান্তভাবে বলে, কিন্তু যারা ফসলের মালিক নয়, তাদের ঘরে ফসলটা যাবে কী করে এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দে। ধানচালের এখন যা দাম আছে, ফলন বাড়লে তা অনেক কমে যাবে। তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু বল দিকিনি, দিনমজুরদের মজুরি তখন এখনকার মতো বেশি থাকবে না কমে যাবে?
সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে আশির দশকের শুরু পর্যন্ত একজন সামরিক শাসকের উন্নয়নের তত্ত্বকে এইভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন হাসান আজিজুল হক। পুরো গল্পটি নিবিষ্টভাবে পাঠ করলে বুঝতে পারা যায় যে, এরকম ক্রুদ্ধ-গল্প বাংলাদেশের সাহিত্যে খুব-একটা নেই, যেখানে ‘জাতীয় অর্থনীতি, গণতন্ত্র, ভেল্কিতন্ত্র, রাহাজানিতন্ত্র’ – সবকিছুকেই যেন লেখক তন্নতন্ন করে খনন করে চলেছেন। উন্নয়নের সেইসব তত্ত্বকে নতুন মোড়কে আজো আমাদের সামনে হাজির করা হয়। শুধু হাসানের মতো গল্পকার আজ নেই, যিনি আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনের মøানিমাযুক্ত নির্যাসকে শিল্পবৃত্তির স্বরূপে হাজির করবেন!
অন্যদিকে, হাসান তাঁর একাত্তরের স্মৃতিকথার শুরুতেই বলেছিলেন –
আমার জানা ছিল না যে পানিতে ভাসিয়ে দিলে পুরুষের লাশ চিৎ হয়ে ভাসে আর নারীর লাশ ভাসে উপুড় হয়ে। মৃত্যুর পরে পানিতে এদের মধ্যে এইটুকু তফাৎ। এই জ্ঞান আমি পাই ’৭১ সালের মার্চ মাসের একেবারে শেষে – ত্রিশ বা ঊনত্রিশ তারিখে। আগের রাতে একটুও ঘুম হয়নি। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় কি ঘটেছে, খুলনায় বসে তা জানার উপায় ছিল না এমনই লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল পথঘাট যোগাযোগের ব্যবস্থা।
আর তাই, হাসান যখন বলেন, ‘স্বীকার করি, গল্প লেখক হিসেবে আমি কিছুই প্রায় বানাতে পারি না। হ্যাঁ, বানানোর ব্যাপারে আমার অক্ষমতা আমি বারবার অনুভব করি।’ তখন সেটি আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। এরকমই অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই অসীম রায় তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘চারপাশের প্রত্যক্ষ যে-জগতে লেখক হাঁটেন, ফেরেন, কথা বলেন, সেই জগৎটাই যে তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে ও আসবে এ-অভিযোগ তিনি যে শুধু মাথা পেতে নেবেনই না বরং একথা বলবার চেষ্টা করবেন যে এই প্রত্যক্ষ জগৎটাকে মানসলোকের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁর লেখার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রেরণা।’ এটা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের একটা সাবালকত্বের লক্ষণ। আমরা বুঝতে পারি যে, টমাস মানকে (Thomas Mann : 1875–1955) অসীম রায়-হাসানের মতো লেখকেরাও স্বীকার্য করে নিতে পেরেছেন। তাঁর ‘আনা কারেনিনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৩৯) জীবনের প্রারম্ভ থেকে শেকড় অবধি যে-প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারটি টমাস মান জোরের সঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তাকেই হাসান আজিজুল হক একেবারে নিজের ধরনে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।
তিন
‘রাজহস্তী উদ্দাম নাচে’ – জীবন ঘষে যে-আগুনের আঁচ নিয়েছিলেন হাসান, সেখানে তাঁর লেখা পাঠ কে মাঝে-মাঝে তাঁকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয় যেন। আমাদের আরেক শক্তিমান কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদ, সে-কারণেই সম্ভবত, হাসানকে ‘ক্ষমাহীন বিশ্বের স্রষ্টা’ বলে অভিহিত করেছিলেন। ‘পাতালে হাসপাতালে’র গল্পের একজায়গায় লেখকের বিবরণে পাচ্ছি –
এককোণে জমিরুদ্দি দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘাড় গুঁজে আধশোয়া হয়ে রয়েছে। রাশেদ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তার ফোলা পা-টি একখণ্ড মোটা তামাটে কাঠের মতো পড়ে আছে। বোঝাই যায়, ওটা নড়ানোর ক্ষমতা নেই জমিরুদ্দির। রাতে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, নীল মাছিগুলো পথ ভুলে যায়নি। সকাল বেলাতেই এসে হাজির। রাশেদ একদৃষ্টে জমিরুদ্দির দিকে চেয়ে থাকে। মুখের রং-এর মতো তার দাড়িগুলোও ফ্যাকাশে। মোটা মোটা শক্ত গাঁটওঠা অশক্ত আঙুল এলিয়ে পড়েছে। রাশেদের ইচ্ছে হলো, প্রচণ্ড চিৎকার করে সে ওকে জিগগেস করে, এখানে কি করছো? এখানে কেন এসেছো মরতে? বোধহয় তার নিঃশব্দ চিৎকারের জবাবেই জমিরুদ্দির একটা চোখের পাতা দুবার কেঁপে উঠে তাকে জানিয়ে দেয় যে সে এখনো মরার সুবিধা করে উঠতে পারেনি।
কায়েস আহমেদ সংগত কারণেই হাসান আজিজুল হক সম্বন্ধে এমনটি বলেছিলেন, ‘জীবনকে এমন নির্বিকার, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় বোধকরি আর কেউ চিত্রিত করেননি গল্পে তাঁর মতো।’ এখানেই তাঁর কথার ইতি টানেননি কায়েস। তিনি আরো খানিকটা প্রলম্বিত টানে জানিয়েছিলেন, ‘সেইসব গল্পের জন্মদাতা হাসান আজিজুল হক, অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, সদাহাস্য, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লাজুকও – নিজের গল্পে বর্ণিত চরিত্রাবলী সম্পর্কে বললেন, জানেন, বাস্তবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য এমন করে লিখেছি, কিন্তু নিজের লেখা গল্পগুলো যখন পড়ি তখন মানুষগুলোর জন্য আমার চোখের পাতা ভিজে আসে।’
অসীম রায় খুব জোরের সঙ্গে একবার বলেছিলেন, ‘জীবনটাই যদি খুব প্রয়োজনীয়, সমৃদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ না ঠেকে তবে সাহিত্য-শিল্পে না যাওয়াই ভালো। চারপাশে যাদের মাঝখানে ঘুরি, তাদের অনুভূতি এমন ফিকে হয়ে গিয়েছে, এমন স্মার্ট হয়ে পড়েছে তাদের মেজাজ যে ছোটোখাটো ভালোলাগাগুলোও কেমন হারিয়ে গেছে।’ হাসানকে যে আমাদের কখনো-কখনো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, কেমন যেন নির্বিকার বলে মনে হয়, জীবনের প্রতি ক্ষমাহীন বলে মনে হয় – তার কারণ হচ্ছে – তিনি জীবনকে, মানুষের জীবনকে, সবসময়ই খুব ‘প্রয়োজনীয়, সমৃদ্ধ আর তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে মনে করতেন। সে-কারণেই মানুষের জীবনের পরাভবকে মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করতেন। সে-কারণেই দেখি, তাঁর গল্পে ‘মৃত্যু’ এসেছে নানাভাবে। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন, ‘আমার অনেক গল্পে ‘মৃত্যু’ এসেছে ঘুরেফিরে। আসলে ওসব এসেছে খুব স্বাভাবিকভাবে, জীবনকে ভোগ (ব্যাপক অর্থে) করতে-করতে, জীর্ণ হতে-হতে একসময় মৃত্যু ঘটেছে।’ হাসানের ‘আমৃত্যু আজীবন’ গল্পের শেষটুকু যখন পাঠ করি, দেখতে পাই – ‘করমালি খড়ের গাদার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচা-পাকা চুল দাড়ি ভ্রু চোখের পাপড়ি ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে কদাকার দেখাচ্ছে তাকে। রহমালি বাড়ির বাইরে এসে তাকে বুকে করে বৃষ্টির মধ্যে সবল পায়ে অশ্রুহীন চোখে ভিতরে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে।’
এভাবেই হাসানের গল্পের জায়গাজমিতে রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি মানবিক শুশ্রূষা নির্মিত হয়ে উঠেছে একেবারে ভেতর থেকে। আর তার ইশারা থেকেই এমন বাক্য রচিত হয় – ‘বৃষ্টি এখন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল।’ সে-কারণে হাসান যখন বলেন, ‘নেতিবাদী দর্শনে আমার কোনো বিশ্বাস নেই, কোনো দুর্বলতা নেই। আমি তার চর্চাও করি না, কোনো আকর্ষণও নেই তার ওপর। আমার আগ্রহ বরং জীবনবাদী দর্শনের ওপর। ‘দর্শন’ যদি আমার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে থাকে তা জীবনের গভীরে যাওয়ার অন্বেষায়।’ তখন তাঁর কথাগুলোকে মান্যতা দিয়েই আমরা সেই জীবনের গভীরতা সন্ধানের চেষ্টা করি।
চার
বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা খোলা চিঠি’তে বলেছিলেন, আমাদের ‘আত্মপ্রসাদ ধ্বংস করে দিয়ে ডস্টয়েভস্কি জাগিয়ে তোলেন আত্মজিজ্ঞাসা; এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা ভালোমানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ নিজেদের সাধু বলে জেনেছি।’ তারই সূত্র ধরে বুদ্ধদেব আরো বলেন, ‘কিন্তু ডস্টয়েভস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী বলেই জানে, তা জানে বলেই পুণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাদের জ্বলন্ত, এবং সেই হিশেবে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানুষ, চৈতন্যে উন্নত, এবং চৈতন্য মানেই আধ্যাত্মিকতা।’ আবার অন্যদিকে, অসীম রায়ের মতে, ‘লেখকের সৃষ্টি মানেই লেখকের কর্ম, তাঁর চৈতন্যের বিস্তার। লেখা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই তার পেছনে লেখকের সামাজিক অস্তিত্বের কথা উঠবে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামের কথা আসবে। কারণ কর্ম মানেই চৈতন্য।’ তাঁর বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করতে গিয়ে অসীম রায় জানিয়েছিলেন, ‘কর্ম মানে কে কত ঘণ্টা কাজ করে তা নয়। কর্ম মানে কে কতদূর নিজের চৈতন্য বিস্তার করতে পেরেছেন, ব্যক্তিকে ছাড়াতে পেরেছেন সমগ্রে এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছেন।’
বুদ্ধদেব বসু যে-চৈতন্যকে ‘আধ্যাত্মিক’ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তাকেই অসীম রায়, হাসান আজিজুল হকেরা কর্মময় জীবনের মুক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তে এসে তাঁরা উপনীত হয়েছিলেন যে, ‘এই চৈতন্যের মুক্তি সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যের মূলকথা।’ এখানে ব্যক্তির সসীম আর অসীম ক্ষমতাকে অসীম রায়ের মতো করে হাসান আজিজুল হকও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অনেকটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই অসীম রায় বলেছিলেন, লেখক যিনি, ‘তিনি সামান্যতম করুণা না দেখিয়েও আমাদের সীমাবদ্ধতাকে দেখিয়ে দেন।’ হাসানের মধ্যেও আমরা লেখক হিসেবে সেই আত্মপ্রত্যয় গভীরভাবে দেখতে পাই। উপলব্ধির সেই গভীরতা থেকেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘বিপ্লব হবে বা বিপ্লব এসে গেলো জাতীয় অবোধ আশাবাদ ‘জীবন ঘষে আগুন’-এ আমি প্রকাশ করিনি। … আমি বলতে চাই, ঐ অর্থে আমি কোনো আশাবাদী গল্পও লিখি না, হতাশাবাদী গল্পও লিখি না। আমি চেষ্টা করি, সমাজের গর্ভে যে সম্ভাবনাগুলো আছে সেগুলোকে ধরার। ‘জীবন ঘষে আগুন’ ঐরকম একটি চেষ্টা।’
হাসান সম্পর্কে এইটেই হচ্ছে আসল একটি কথা। সেটা হচ্ছে : তিনি আশাবাদী বা হতাশাবাদী লেখা লেখেননি। সারাজীবন ধরে তিনি লেখালেখির মধ্যে দিয়ে জীবনের সম্ভাবনাগুলোকে নানান মাত্রায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এখানে আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এইসব সম্ভাবনার শিল্পকে সামনে আনতে গিয়ে হাসান কোনো তত্ত্বকেই খুব বেশি প্রাধান্য দেননি। একটা সময় তিনি মার্কসবাদের প্রতি অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছিলেন, কিন্তু লেখালেখির ক্ষেত্রে ওই মতবাদকেও শিল্পের ওপরে স্থান দিতে চাননি। অর্থাৎ আমাদের বলবার কথাটা এই যে, তাঁর কোনো লেখাতেই ‘তত্ত্ব’ প্রধান হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যে জীবনের চেয়ে তত্ত্বের প্রাধান্য যখন বেশি দেখা যায়, তখন সেটি সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। অন্যদিকে হাসান আমাদের জানিয়েছিলেন, তিনি ‘যে-কোনরকম নিয়ন্ত্রণবাদের বিপক্ষে। এবং মার্কসবাদও তা শেখায় না। যা শেখায় তা হচ্ছে, কতগুলো বাস্তব পরিস্থিতিই ব্যাপকভাবে সমাজের গতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং লেখার বিষয়ও সমাজের সেই বিপুল প্রবাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।’ এসব শুধু হাসানের বেলাতেই নয়, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস (Gabriel Garcia Marquez : 1927–2014) তাঁর এক সাক্ষাৎকারে প্রায় ওই একই ধরনের কথা বলেছিলেন – ‘আমি চাই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে পরিণত হোক। … আমার চরমপন্থী বন্ধুদের অনেকেই মনে করেন যে লেখককে কী লিখতে হবে না-হবে তা নির্দেশ দিয়ে শেখানো উচিত। কিন্তু এতে অবচেতনভাবে তাঁরা সৃজনশীল রচনার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে নিজেরাই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করছেন। … একজন লেখকের দায়িত্ব – বলতে পারেন বিপ্লবী দায়িত্ব হল – ভালো লেখা।’ (মার্কেস : ১৯৮২; অনুবাদ : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস)। এসবেরই জের টেনে মার্কেস আরো জানিয়েছিলেন যে, ‘নিজের লেখা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। অনেকদিন ভেবে বুঝেছি আমার দায় শুধু আমার দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থাতে সীমাবদ্ধ নয়। সারা পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার দায় আমার। এর কোনও দিককেই আমি মাথায় তুলিনি আবার অবহেলাও করিনি।’ (মার্কেস : ১৯৮২; অনুবাদ : গৌতম সেনগুপ্ত)। এর সঙ্গে মার্কেস যুক্ত করেন এই মূল্যবান কথাটিও। তাঁর মতে, ‘লেখার মতো নির্জন পেশা আর একটিও নেই। এই অর্থে কথাটা সত্য যে আপনি যখন লিখছেন তখন কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারে না। তেমনি কেউ জানেও না আপনি কী করতে চান। সেখানে আপনি বাস্তবিকই একেবারে একা, বিচ্ছিন্ন – কেবল একটা শূন্য পাতা আপনার সামনে।’ এই কথাগুলো ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় হাসান আজিজুল হক যে কতবার বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। লেখালেখির ক্ষেত্রে এই যে একটা রাজনৈতিক-তাত্ত্বিক এবং আত্মিক সংকট, একে অনেকেই যথাযথভাবে সামাল দিতে বারেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। সেইটি খেয়াল করেই অসীম রায় বলেছিলেন, ‘শিশুর আনন্দ, বীরের আত্মোৎসর্গ, বৃদ্ধের স্মৃতি, শিল্পীর স্বধর্মে নিষ্ঠা, প্রেমের যন্ত্রণা, এগুলো তাদের শুদ্ধতায় এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। তাদের তীব্র energy-তে একসূত্রে গাঁথা। আমাদের চারপাশের জীবনে এই শুদ্ধতার বড় অভাব। অথচ এই শুদ্ধতার প্রেরণা না থাকলে লিখে কী লাভ?’ হাসান অবশ্য সেই সমস্যাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। কেননা, তাঁর চৈতন্যের একদিকে ছিল জীবনভাবনার বিভিন্নতার রূপায়ণের দক্ষতা আর অন্যদিকে সাহিত্যের প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা। অসীম রায়ের মতে, ‘শিল্পে নিষ্ঠা মানে ব্যক্তিত্বের বিক্রম।’ আর তারই জোরে লেখকের কল্পনা ও স্বপ্নের শিকড় হয় সুদূরপ্রসারিত ও দৃঢ়।’ সেই দৃঢ়তার বোধ থেকেই হাসান আজিজুল হক তাঁর সমকালকে নানাভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। কী-এক অসাধারণ আন্তরিক ঔদার্যে টমাস মান বলেছিলেন, ÔArt is the most beautiful, austerest, blithest, most sacred symbol of all supra-reasonable human striving for good above and beyond reason, for truth and fulness.Õ
সেই সুন্দর, আনন্দময়, পবিত্র বস্তুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প-সাহিত্যকে জীবনের সত্য এবং পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাসান আমৃত্যু সাধনা করে গিয়েছেন। এখানেই সাহিত্যিক হিসেবে হাসানের স্বকীয়তা আর মৌলিকত্ব। আর এখান থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর রচনায় কেন বারবার বিপ্লবী সংস্কৃতিকে বিপ্লবের বলিষ্ঠ অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত কারণগুলো বুঝতে খুব-একটা অসুবিধা হয় না।
পাঁচ
প্রখ্যাত দিনেমার দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ড (Soren Kierkegaard : 1813– 1855) তাঁর ঐকান্তিক উপলব্ধি দিয়ে জানিয়েছিলেন, A human being is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and eternal, of freedom and necessity.
মানুষের মধ্যে যে অসীম ও সসীম, যে অস্থায়ী ও শাশ্বত, যে-স্বাধীনতার সন্নিবেশের কথা কিয়ের্কেগার্ড বলতে চেয়েছিলেন, সেটি কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই নানান বাঁক নেয়। সে-কারণেই তাকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হয় প্রতি পদে। টমাস মানকে সামনে রেখেই অসীম রায় বলেছিলেন, ‘বাঁচার তাগিদেই জীবন যেমন বাঁক নেয় তেমনি শিল্পসাহিত্যও বাঁক নেয়। একটা পর্ব পার হয়ে আরেক পর্বে এসে দাঁড়ায় লেখক।’ জীবনের খুব গভীর থেকেই হাসানও বিশ্বাস করতেন যে, ‘শিল্পসাহিত্যে পুনরাবৃত্তি মানে লেখকের আত্মিক মৃত্যু। তার মানে জীবনের দিকে সে আর তাকিয়ে নেই, সে চোখ বন্ধ।’ কিন্তু হাসান তো আজীবন জীবনের দিকে তাকিয়েই নিবিষ্ট মনে সাহিত্যের চর্চা করে গিয়েছেন। সেজন্যেই তাঁর সাহিত্যকর্মে অর্থহীন পুনরাবৃত্তির চর্চা একেবারেই দেখা যায় না।
নিজেকে নতুন-নতুন বাঁকে নিতে গিয়ে হাসান যেমন তাঁর এক গল্প থেকে অন্য গল্পে বাঁক নিতে পেরেছিলেন, তেমনি তিনি আঙ্গিকের দিক থেকেও নানান বাঁকের অনুসন্ধান করেছিলেন। গল্পের জগৎ থেকে একটা সময় তিনি নিজেকে উপন্যাসের জগতে প্রসারিত করলেন। অসীম রায়ের মতো হাসান আজিজুল হক তীব্রভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, ‘শিল্প-সাহিত্যে সবসময় নতুনের বন্দনা করতে হয়। নিজে যে-জগৎ তৈরি করে, লেখক সে জগৎই ভেঙে বেরিয়ে যায়। তা না হলে একজায়গায় ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হয়।’ এই ঘুরপাকের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্যে সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন, তা হচ্ছে লেখকের আত্মসচেতনতা, যার কথা আমরা লেখার শুরুতেই বলেছি। আর সেইসঙ্গে এক নিবিড় আত্মজ্ঞান। আর তার ওপর ভর দিয়ে হাসানের যাত্রা উপন্যাস রচনার অভিমুখে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হাসান জানিয়েছিলেন – ‘যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো নিবিড় সংযোগ না থাকে, তাহলে উপন্যাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া অসম্ভব। এই কারণে আগুনপাখি লিখতে বসার পর, যখন দু-এক অধ্যায় লিখে ফেলেছি, নিজে সেই অংশটুকু পড়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম যে, নাহ, ভালোই তো এগোচ্ছে।’ আর তার কারণ সম্পর্কে হাসানের বিশ্লেষণটা মনে রাখার মতো একটি ঘটনা। তিনি বলেছিলেন, ‘প্রথমত এর প্রেক্ষাপট আমার দেখা ও চেনা; দ্বিতীয়ত, এর পরিপার্শ্বকে আমি যতটা নিখুঁতভাবে পারা যায় ধরতে পারছি, কিন্তু তা স্মৃতিকাতরতাতেও জর্জরিত হচ্ছে না।’ তারপরেও হাসানের মধ্যে সংশয় যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। তিনি তাঁর সেই ‘সংশয় কাটানোর জন্য পরিচিত কয়েকজনকে’ উপন্যাসটির একটি অধ্যায় পড়তে দিয়েছিলেন। হাসানের ভাষ্যমতে, ‘বেশির ভাগই বললেন, কেমন যেন লাগছে, বড় বেশি জটিল। শুধু আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সনৎকুমার সাহা খুব উৎসাহ জোগালেন।’ জোগানোরই কথা। কেননা, সনৎকুমার সাহাই তো একদিন হাসানকে উপলক্ষ করে লিখেছিলেন, ‘বিহাসে তাঁর [হাসান আজিজুল হক] ‘উজান’। ‘আগুনপাখি’ রচনা করেন তিনি এখানে। বিশ্ববিধানে কিছুই হাতে জমা পড়ে না। তার বিপরীতে যে পথ চলা, তাতেই পাওয়া-না-পাওয়ায় মিশে জীবনের সঞ্চয় একটু একটু করে গড়ে উঠতে থাকে। মানুষের মহিমা এইখানেই। এইটুকু। এমনকি কিছুই যদি না জোটে দিনের পর দিন, তবুও। আগুনপাখি পাখা মেলে।’ হাসান সম্পর্কে কী অসাধারণ সারগর্ভ উপলব্ধি সনৎকুমার সাহার! অবাক হতে হয়।
ছয়
হাসানের নিজের মতে, তাঁর আগুনপাখি একটি পারিবারিক গল্প। হাসান জানিয়েছিলেন, ‘পৃথিবীর বহু মহৎ উপন্যাস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক গল্প। ‘আগুনপাখি’ যদি মহাকালের বিচারে টেকে, তাহলে এ জন্যই টিকবে বলে আমার ধারণা। কারণ, একমাত্র নিজের পরিবারকেই আমি হাতের শিরা-উপশিরার মতো চিনতে পেরেছি।’
হাসান গল্প বলেছেন ঠিকই কিন্তু সেই অর্থে আগুনপাখি ঠিক জমাটি গল্প নয়। হওয়া সম্ভবও ছিল না। অমিয়ভূষণ মজুমদার সেই কবে আমাদের জানিয়েছিলেন, ‘উপন্যাস তত্ত্ব নয়। এবং বোধহয় সেজন্যই উপন্যাসের ভাষা বাক্যের পর বাক্য বসানো নয়। উপন্যাস গল্প নয় যে গল্পটা পাঠকের মাথায় ঢুকছে কিনা তা জানলেই ভাষা সম্বন্ধে সব জানা হলো।’ শুধু এইটুকুই নয়, আরো খানিকটা বিস্তারে গিয়ে অমিয়ভূষণ বলেছিলেন, ‘উপন্যাস বড় করে বলা গল্প নয় যে কেউ এ-বিষয়ে চালাকি করে বলবে উপন্যাস বড়ও বটে, গল্পও বটে।’ তাহলে উপন্যাস কী? কাকেই-বা আমরা উপন্যাস বলব? অমিয়ভূষণ বেশ খানিকটা ঘুরপাক দিয়ে আমাদের বলেছিলেন, ‘উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে একটা থিম যা আমাদের চোখের নিচে ফুটে ওঠে। একটা থিম যা হয়ে ওঠে। … থিম নামে এক জীবন্ত বিষয়ের ভাব।’ এবার আগুনপাখি নিয়ে আমাদের আর কোনো সংশয় থাকে না।
এই উপন্যাসে একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষার নিবিড় ব্যবহার সম্পর্কে হাসান তীব্রভাবেই জানিয়েছিলেন, ‘এটা খুব ভেবেচিন্তে করেছিলাম, এমনটা নয়। আকস্মিকভাবেই চলে এসেছে। আর এটাকে রাঢ়বঙ্গের ভাষা বলতেও আমার আপত্তি আছে। এটা আদতে আমার মায়ের মুখনিঃসৃত ভাষা। … উনি যেভাবে কথা বলতেন, আমার ফুফুরা বা চাচিরা তো সেভাবে বলতেন না।’ এই উপন্যাসের কেন্দ্রে কেন মাকে রাখলেন, তারও একটা দারণ জবাব দিয়েছিলেন হাসান। বলেছিলেন, ‘মায়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা তো নিছক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নয়, এটা হলো অস্তিত্বের সম্পর্ক। মা ছাড়া আমি তো নেই। কিন্তু রাঢ়বঙ্গের একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে ছেলেমেয়েদের কাছে মা ছিলেন নেহাতই একজন ‘মিসিং পারসন’।’ আর তারপরই হাসান যোগ করেছেন, ‘আগুনপাখির মাধ্যমে আমি দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে আমার মা ও তাঁর মতো হাজারো নারীর অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। তাঁদের যে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য – তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। উত্তম পুরুষে উপন্যাসের বয়ান নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ কারণেই।’ উপন্যাসে আমরা দেখি, ধীরে-ধীরে মায়ের ব্যক্তিসত্তার পুনর্জাগরণ যেন ঘটেছে। আর একেবারে শেষে এসে এক অতিলৌকিক বিস্ফোরণ যেন, যেখানে ব্যক্তিসত্তা আর সামাজিক সত্তার অপূর্ব সংমিশ্রণ –
আমি কি ঠিক করলম? আমি কি ঠিক বোঝলম? সোয়ামির কথা শোনলম না, ছেলের কথা শোনলম না, মেয়ের কথা শোনলম না। ই সবই কি বিত্তি-বাইরে হয়ে গেল না? মানুষ কিছুর লেগে কিছু ছাড়ে, কিছু একটা পাবার লেগে কিছু একটা ছেড়ে দেয়। আমি কিসের লেগে কি ছাড়লম? অনেক ভাবলম। শ্যাষে একটি কথা মনে হলো, আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি সবকিছু শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি।
এই যে একজন নারীর মুক্তিচিন্তা, যা শুধুই একজন নারীর হয়ে থাকেনি, তাতে আমরা যেন অনেক নারীর অংশগ্রহণ দেখতে পাই, দেখতে পাই তাঁদের মুক্তিচেতনার একটি স্পষ্ট আদল। এই মুক্তিচেতনার কথা জানাতে গিয়ে মল্লারিকা সিংহ রায় বলেছেন, ‘ওই মুক্তিচেতনার বিকাশের জন্য যে সক্রিয় সাহায্য প্রয়োজন, পারিবারিক ও সামাজিক বলয় তার কাঠামোটি তৈরি করে। চেতনা ও কাঠামোর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ এই আদান-প্রদানকে যথাযথভাবে বুঝে নিতে পারলে, যুগপরিবর্তনের অভিমুখগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব।’ হাসান যে কী বড়মাপের একটি সাহিত্যকর্ম আমাদের দিয়ে গিয়েছেন, সেটি আমরা এখনো অনেকেই ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। হয়তো, একদিন সেটি আমাদের বোধের অধিগম্য হয়ে উঠবে।
সাত
সাহিত্যে ভাষার ব্যবহারের তাৎপর্য আর তার অধিকার নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। কথাসাহিত্যিক অসীম রায় মনে করতেন, ‘ভাষা শুধু ভাসা ভাসা অস্পষ্টতার অর্থেই নয়। ভাষা ভাসা মানে এই ভাসন্ত জীবন্ত জীবনের গতিরই রূপক।’ এই দিকটাতে নজর দিয়েই তিনি আরো মন্তব্য করেছিলেন, ‘গতির কথা চিন্তা করলে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ শুধু বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। তা আমাদের পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীর সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিকাশে বা বলা যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের চৈতন্যের বিস্তারে।’ তিনি এরকম একটি মতেও বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন যে, ভাষার ‘এ-সমৃদ্ধি বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষের ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য।ে’ আর সে-কারণেই, তাঁর মতো, ‘আমাদের সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ভাষার শৃঙ্খলমুক্তি শুধু আমাদের ঔপন্যাসিকদের দায় না, তা সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের।’
হাসান অবশ্য ঠিক এভাবে বলেননি। আমরা জানি যে, ভাষা তাঁর সাহিত্যের একটি খুব উল্লেখযোগ্য জায়গা জুড়ে আছে। বাস্তবতার আরো গভীর স্তরে নেমে এসে তাঁর মনে হয়েছে যে, আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-ভাষা, যার গায়ে-গায়ে জীবনের উষ্ণতা লেগে রয়েছে, যা কি না অত্যন্ত জীবন্ত, তাকে শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও প্রবেশাধিকার দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।
হাসান আজিজুল হকের মতে, ‘লেখ্য-মান-মুখের ভাষা যত কাছে আসবে, তত তার প্রকাশ-শক্তি বাড়বে। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতির আলোচনা তত সাধারণের বোধসীমার মধ্যে ঢুকতে পারবে।’ ঠিক এসব কারণেই ভাষা নিয়ে হাসানের একেবারেই কোনো শুচিবায়ু ছিল না। বরং এই উপলব্ধিই তাঁকে আমাদের সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য ভাষাশিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।
আট
হাসান আজিজুল হকের রচনায় আমরা তাঁর স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মানুসন্ধানের নানান বিরল ঝোঁক দেখতে পাই। যার মধ্যে জীবনের ভিন্নমাত্রার অন্তর্গত সম্পর্ক স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। হাসানের ‘খুব ছোট্ট নিরাপদ নির্জন’ গল্পটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, লিখে হাততালি পাওয়া, স্বর্ণপদক জিতে নেওয়া, খ্যাতির চিৎকার – এসব তিনি ঠিক কী চোখে দেখতেন। লেখক তাঁর গ্রামে এসেছেন অসুস্থ বোনকে দেখতে। দুজনের কথাবার্তার এক পর্যায়ে খ্যাতিমান লেখক যেন মুখের অর্গল খুলে দেন। তিনি বলেন : ‘হিশেব করে দেখ, আমি এতসব চিরকালীন রচনা লিখে কি দেশের চার পয়সার সম্পদ বাড়িয়েছি? সমাজে যেসব বদমায়েশি চলছে, কোটি কোটি লোক কলে-পড়া ইঁদুরের মতো থ্যাঁতা হচ্ছে, আমি তাদের একজনেরও উপকারে আসতে পেরেছি? তাহলে এইসব মামদোরা কেন আমাকে নিয়ে লাফায়?’ এইভাবেই আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার ওপর ভর দিয়ে নিজের চারপাশটাকে দেখাতে চেয়েছেন হাসান। খানিকটা বিষাদ আর বিদ্রƒপের স্বরে লেখক তাঁর বোনকে বলছেন, ‘এখন আমি হচ্ছি একজন মহান সাহিত্যিক। আমাদের দেশের মহান দেশপ্রেমিক, মহান শিক্ষাবিদ, মহান বৈজ্ঞানিক সব একরকম। সবাই সমান অপদার্থ।’ শুধুই প্রশ্ন নয়, হাসানের এসব লেখার মধ্যে দিয়ে যেন জীবনের এক মর্মস্পর্শী উত্তরও আমরা পেয়ে যাই।
হাসান লিখেছিলেন, ‘একখণ্ড পাথর বাঁচেও না, মরেও না। শুধু থাকে। অনেক মানুষ তেমনি বেঁচেও নেই, মরেও নেই – শুধু আছে।’ এই ‘আছে’টাকেই তিনি জীবনের একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করতে চাননি কখনো। সেই কারণে হাসান মাঝে-মধ্যেই অদম্য হয়ে উঠতেন, সেটি তিনি হয়ে উঠতেন তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়েই।
নয়
যাকে বলা হয়, লেখকের আত্মতৃপ্তি, সেই ঝোঁকটা আমরা কখনোই হাসানের মধ্যে দেখিনি, দেখতে পাইনি। বরং তাঁর এই অতৃপ্তিই তাঁর সাহিত্যকর্মকে নানান বাঁক ফেরাতে সহায়তা করেছে, তাঁকে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। জীবনের এই অখণ্ডতা যে-কোনো সাহিত্যিকের পক্ষেই দুর্লভ। হাসান আমৃত্যু সেই অখণ্ডতার সাধনা করে গিয়েছেন।
দশ
এখন আমাদের আবার নতুন করে ‘হাসান আজিজুল হক’ পাঠের সময়। ১৫ই নভেম্বর, ২০২১। আমি অন্তত এখনই হাসানকে বিদায় জানাবো না।

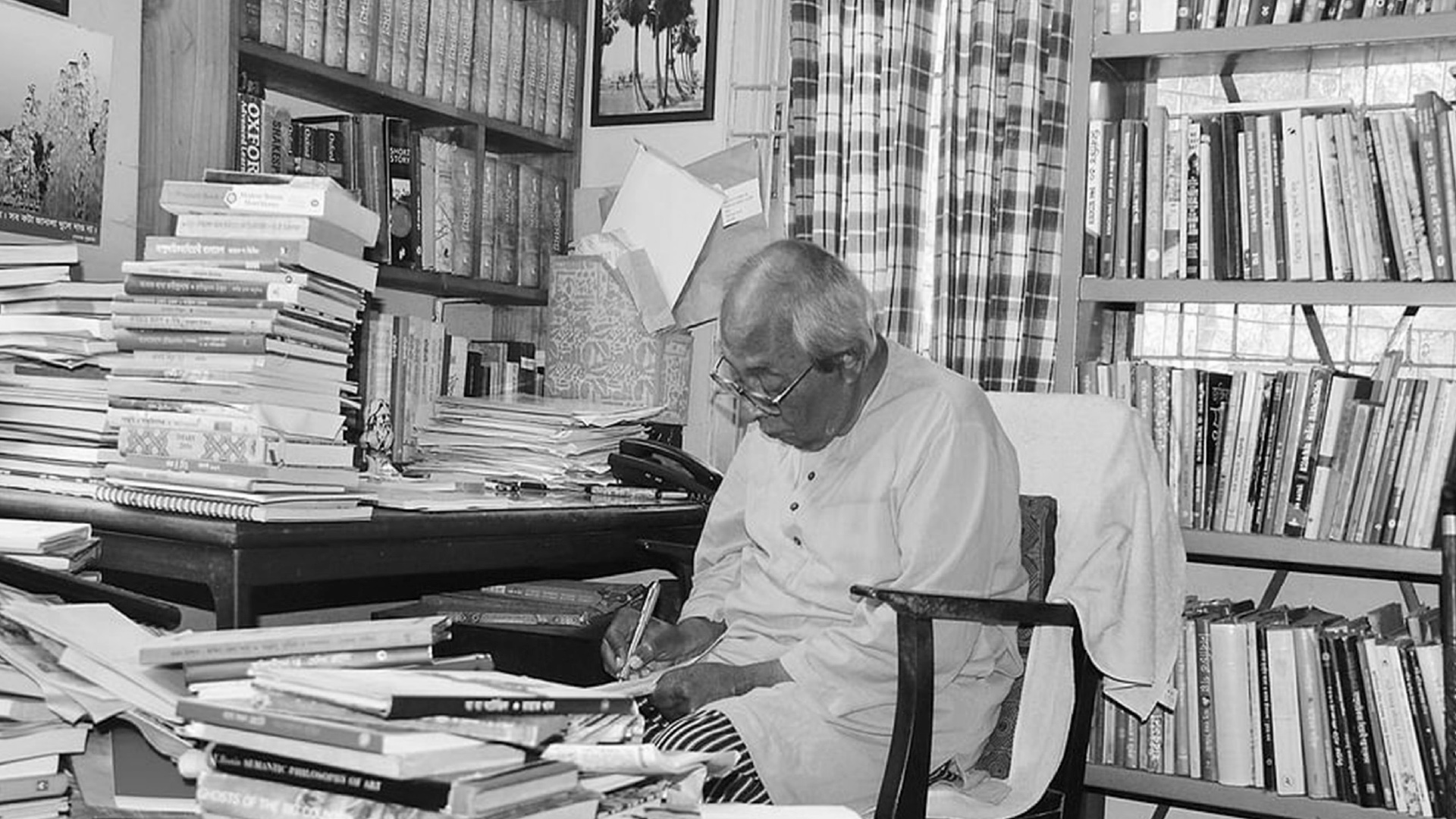
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.