অমিয়ভূষণ মজুমদারের বেশকিছু উপন্যাসে [দুখিয়ার কুঠি (১৯৫৯), মহিষকুড়ার উপকথা (১৯৭৮), হলং মানসাই উপকথা (১৩৯৩), সোঁদাল (১৩৯৪) কিংবা অগ্রন্থিত উপন্যাস বিনদনি (১৩৯২), মাকচক হরিণ (১৩৯৮)] অরণ্যপ্রাণ মানব-মিছিলের দেখা মেলে। মানুষ এবং প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর কথাসাহিত্য সেখানে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। গণমানুষ-অবলম্বী এসব উপন্যাসে গভীরভাবে অনুরণিত আরণ্যক জীবনের আদিমসত্তার সঙ্গে আধুনিককালের যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতার প্রবল দ্বন্দ্ব। পরিণতিতে ভয়ানক যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে অরণ্যচারী মানবাত্মা হয়েছে উন্মূলিত, শোনা গেছে তাদের আপাত পরাজয়ের বেদনার্ত কান্না। যদিও অরণ্য ও যন্ত্রজীবনের দ্বৈরথ রূপায়ণই তাঁর উপন্যাসের শেষ কথা নয়। লেখক আরো কোনো বক্তব্যের বীজ পাঠকচেতনার অন্তস্তলে রোপণ করতে চান। এই উপন্যাসগুলোতে তারই প্রকাশ ঘটেছে।
অমিয়ভূষণের উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলোকে কোনো বিশেষ ভৌগোলিক মানচিত্রে সীমায়িত করা কঠিন হলেও মোটাদাগে এসব অঞ্চল উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলেই চিহ্নিত করা যায়। প্রায় সব উপন্যাসেরই অঞ্চল চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক যে-কথা বলেছেন, তাতে রয়েছে অনির্দেশের স্পর্শ। আঞ্চলিকতা নয়, বরং উপন্যাসের অবয়বে একটা ‘লোকাল কালার’ দেওয়াই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। উপন্যাসের ভাষাতেও সেটি সুস্পষ্ট।
‘নিজের কথা’ প্রবন্ধে অমিয়ভূষণ নিজেই তাঁর উত্তরবঙ্গপ্রীতির কথা লিখেছেন :
উত্তরবঙ্গের উত্তরখ-ে আমার বাস। কোচবিহার প্রীতির কথা আগেই জানিয়েছি। … এই টেমপারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা, আরাম, উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে আমি জানি আমার মা যে জেলার মেয়ে, তোমরা নিষাদ, শবর, পুলিন্দ বলবে কিনা ভেবে দেখো, বা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর বোন, তাকে রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্য কলকাতার এক হাঁটু কাদায় গেঁড়িগুগলি তুলতে হয় বটে, কিন্তু তার কপালে সে-সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা হিরার মুকুট। … আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদেনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো … যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ।
উপর্যুক্ত বর্ণনায় উত্তরবঙ্গের গণমানুষের প্রতি অমিয়ভূষণের গভীর আবেগ ও ভালোবাসা স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যাবে। এই আবেগ তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই মনে করেন, ‘রাজকাহিনী নয়, গণকাহিনীই অমিয়ভূষণের নিজক্ষেত্র।’ অমিয়ভূষণ তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। তাঁর চাকরিজীবনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির অরণ্য-প্রকৃতি এবং জনজীবনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্য হয়েছিল সেই সময়, যখন তিনি এসব এলাকায় ডাকবিভাগের টাউন ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পালন করতেন। লেখকের শিক্ষক ঊষাকুমার দাস তাঁর দুখিয়ার কুঠি পাঠ করে সেই গাঢ় সংবেদনার প্রকাশ অনুভব করে মন্তব্য করেন : ‘ডাকঘরের চাকরিতে শহর থেকে দূরে এখানে ওখানে ঘুরে … ঐসব অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত অঞ্চলের প্রবহমান জীবনস্রোতকে প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছো, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছো, তোমার সাহিত্যিক প্রতিভায় এ দিয়ে গড়ে তুলেছো একটি অক্ষয় কথামালা।’ উত্তরবঙ্গ তাঁর পদচারণায় একদা মুখরিত ছিল বলেই হয়তো এসব অঞ্চলের জীবনাচরণের সূক্ষ্ম ও গভীর সংবেদনা অনায়াসে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে অরণ্যপ্রাণ মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পাঠককে যে-বার্তা তিনি পৌঁছে দিতে চান, সেটি জরুরি। বৈনাশিক যন্ত্রসভ্যতার প্রতিপক্ষে আরণ্যক জীবন আর কৃষি-সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যে প্রবল সংগ্রাম, সেটি রূপায়ণে অরণ্যজীবনপটে ক্রমবর্ধমান নগর-সভ্যতার ক্রূর ছায়াপাত প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল বিচিত্র অরণ্যবাসী মানুষের নিজস্ব জীবনাচারের প্রকাশ এবং সময়ের ক্রমরূপান্তরিত স্বরূপের উন্মোচন। কুচবিহার সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ বলেছেন, ‘কুচবিহারের আঞ্চলিক ইতিহাস নামমাত্র প্রয়োজন। কুচবিহারের যে বিভিন্ন জাতি লোপ পাওয়ার মুখে, নিজেদের নাম ভুলে যাওয়ার মুখে, এই জাতিগুলোকে চেনা দরকার।’ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সময় ও ব্যক্তি-অস্তিত্বের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব প্রকাশের পট হিসেবে এসব কারণেই তিনি বেছে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গকে।
অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলোর স্থানপট চিহ্নিতকরণে উপলব্ধি করা যাবে, দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে গদাধরপুর মূলত গদাধর নদীর নিকটবর্তী কুচবিহারের তুফানগঞ্জ শহরের আদলে কল্পিত এক মহকুমা শহর। অন্যদিকে মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসের পটভূমি কুচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চল। যদিও বলা হয়, মহিষকুড়ার মানচিত্র অমিয়ভূষণের মনোভূমে অবস্থিত। অন্যদিকে হলং মানসাই উপকথায় বেছে নেওয়া হয়েছে উখুণ্ডি নামক এক গ্রামকে। স্পষ্ট করে না বললেও হলং নদীর নামকরণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ-উপন্যাসে ব্যবহৃত পটপ্রান্ত উত্তরবঙ্গের। মহিষকুড়ার উপকথার মতো সোঁদালে তুরুককাটা গ্রামের ছবি মেলে, যে-তুরুককাটা কুচবিহার জেলার দিনহাটা অঞ্চলে অবস্থিত। এভাবেই উত্তরবঙ্গ সুচিহ্নিত তাঁর উপন্যাসগুলোতে।
দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে মহকুমা সদর গদাধরপুর আর গদাধর নদীর ওপারের দুখিয়ার কুঠি গ্রামের মানুষেরাই মুখ্য (প্রোটাগনিস্ট) চরিত্র। বিশেষ করে ভোট বা ভুটিয়া জাতিগোষ্ঠীর বিচরণকেই লেখক এ-উপন্যাসে অস্তিত্ববান করে তুলেছেন। রাজার সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ আর ডাকাতি কিংবা স্বাধীন ব্যবসা করে বেঁচে থাকা এই জনগোষ্ঠীর হাত থেকে বাঁচার জন্যই রাজা শরণ নিয়েছিলেন কোম্পানির। কোম্পানির হাত থেকে আত্মরক্ষা করে পালানো একটি ভুটিয়া দল অরণ্যে আত্মগোপন করে পরে গদাধরের তীরে একটি ভোট গ্রামের পত্তন করে। পরবর্তীকালে ভোটবস্তির প্রান্তিক মানুষগুলোর সঙ্গে আরো একবার রাজার প্রতিনিধিদলের লড়াই হলে তাদের নির্মূল করার শক্তিমত্তা দেখায় কেন্দ্র। কিন্তু প্রান্তিক গণমানুষের সংঘবদ্ধ শক্তি কখনো নিঃশেষ হয় না। কাজেই অমিয়ভূষণ সগৌরবে ঘোষণা করেন :
ভোটরা নির্মূল হলো। এ রকম মনে করার যুক্তি আছে তাদের বস্তির চারিপাশের গ্রামের তুলনায় তারা অগ্রসর ছিল। তাদের সভ্যতার কোনো নিদর্শন অবশ্য এ অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো বা তাদের সমাজের কোনো প্রথা বর্তমানে একান্ত আঞ্চলিক কোনো সংস্কারের গোড়ায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটা বিষয়ে তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন কখনো কখনো চোখে পড়ে। এদিকের ইতস্তত ছড়ানো গ্রামগুলিতে ভোট ছাঁদের মুখাকৃতি পাওয়া যায়। আর ভোট বস্তিটার সীমার মধ্যে পড়ে যে গ্রামটা গড়ে উঠেছিল সেখানে কিছুদিন আগেও হলুদ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের সন্ধান পাওয়া যেত। এই গ্রামেরই বর্তমান নাম দুখিয়ার কুঠি। … গ্রামের নাম যারা দুখিয়ার কুঠি দিয়েছিল তারা সকলেই বাইরের লোক নয়। সেই গ্রামেই এমন কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিল যারা ক্রমশ এই দুঃখের নামটাকে মেনে নিয়ে নিজেদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাস করত।
উপন্যাসে দুখিয়ার কুঠি গ্রামে রাভা, রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়েরও দেখা মেলে। তবে সমালোচক মনে করেন, ডাঙ্গর আই, মাতালু, কাঁকরু, রংবর, ফুলমতী – এরা এইসব সম্প্রদায়ের ঠিক কোনটির অন্তর্গত, সেটি উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। লেখক মনে করেন, আই হয়তো কোচ-মেচ কিংবা বাহে। এদের চেতনার চোখেই লেখক যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে ধ্বস্ত অরণ্য আর কৃষিসভ্যতার বিনষ্টিকে দেখতে চেয়েছেন।
অন্যদিকে, মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসে পুরনো মহিষকুড়া নদীর প্রবহমানতায় আড্ডা জমত বুনো মোষের, যাদের ধরতে শীতকালের শুকিয়ে যাওয়া নদীখাতে আসত ‘বেদেনি’রা। এরা ছিল যাযাবর। কাজেই তাদের স্থানীয় বাসিন্দা বলাটা প্রশ্নসাপেক্ষ। উপন্যাসের আদি নৃগোষ্ঠী হিসেবে যারা এখনো অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, তারা রাজবংশী। এখানে, একদিকে যেমন আসফাকের মতো অরণ্যপ্রাণ রাজবংশী মুসলমানের কথকতা রচিত, তেমনি চাউটিয়া বর্মণ বা তার পিতার মতো হিন্দু রাজবংশীরাও এ-এলাকার আদিপ্রাণ হিসেবে উপন্যাসে চিহ্নিত। সমালোচক উদয়শঙ্কর বর্মা মনে করেন, এ-উপন্যাসে ‘রাজবংশী মুসলমান সমাজের যেটুকু ছবি পাচ্ছি তাতে কোনো জনজাতির অভ্যাস-বিশ্বাস-সংস্কার নেই। … একটি নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ইতিহাসের আভাস আছে এখানে। ফান্দী চাউটিয়া, উচ্ছেদপ্রাপ্ত হালুয়া (বর্গাদার) আসফাক, বেদেনী কমরুন সবাই মিলে এই অঞ্চলের একটি বিলুপ্ত সময়কে তুলে ধরেছে।’ চাউটিয়ার পিতার মোষ ধরা ফান্দি-বৃত্তি তাদের আদিমসত্তাকেই প্রকাশ করে। আর এভাবে, বিপজ্জনক মোষ ধরার কাজকে কেন্দ্র করে এ-গ্রামের নাম হয়েছে ‘মহিষকুড়া’। উপন্যাসে কমরুন যাযাবর দলের প্রতিনিধি। এমনকি জোতদার জাফরুল্লার পিতা প্রসঙ্গেও আড়ালে উচ্চারিত হয় যে, তার পিতা ছিল ‘ভৈষ-বাউদিয়াদের দলপতি’।
হলং মানসাই উপকথায় যে-আদিম মানবসত্তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়, তাদের পরিচয় হলং নদ বা নদীর জন্মকথার সঙ্গে যুক্ত। উপন্যাসে উত্তরের আদিপ্রাণ মানুষের তুলনায় স্পর্ধিত সত্তায় অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে দক্ষিণ থেকে আগত বাঙালিরা। অরণ্য আর নদী ধরে চলা এই মানুষগুলো অমিয়ভূষণের উপন্যাসে ‘কখনো কোচ, কখনো রাভা, কখনো রাজবংশী বলে নিজেদের’ পরিচয় দেয়। তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে নিজেদের নানা নামে তাদের বিভক্ত করে ফেলার প্রবণতা। অমিয়ভূষণ মনে করেন, তারা আসলে একই জনগোষ্ঠী, যারা একত্র হয়েছিল। উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই তারা একক এক গোষ্ঠী গড়ে তুলে হলংয়ের পাড়ে বসতি গড়ে তুলেছিল।
এছাড়া সোঁদালে যে মানুষগুলোর দেখা মেলে, তারা কেউ কেউ সেই মাটির গভীরে শেকড়চারী মানুষ, কেউ বা বহিরাগত। তবে গ্রামগুলোর যেসব নাম মেলে উপন্যাসে, সেগুলো স্থানীয় মানুষের দেওয়া নাম। এ-উপন্যাসে মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠীকে লেখক তুলে এনেছেন, যাদের কথা বলতে গিয়ে অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেন :
ধান উৎপাদনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদিকে নির্ধারিত করে, সে তো এখানকার নানা অধিবাসীদের মধ্যে রাভাদের লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। তারা তো বলে, ‘নাং কোচা’ – আমরাই কোচ। আর গারো পাহাড়ের আদিবাসীরা শৌর্যেবীর্যে সকলকে ছাপিয়ে উঠতে থাকলেও (তারা তো তখন পশুপালক পশুশিকারীর স্তরে) পাহাড়ের গায়ে জুম চাষ ছাড়া কিছু জানত না। তারা এই সমতলবাসী কোচদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ধান চাষ শিখতে – এই ডাক থেকেই, রব থেকেই তারা রাভা। আর সেজন্যই ধানজমি আর রাভাকন্যা আর রাভাগৃহ, এক থেকে অন্যটা পৃথক হয় না। জমি আর কন্যা একই আত্মার দুই পৃথক রূপ, কন্যার গৃহও তাই। পুরুষ লাঙ্গলের ফলা হতে পারে; তারপর তো সে এদিক ওদিক চলে যাবে, কন্যা ছাড়া কে লালন করবে ধান! পুুরুষ জঙ্গল থেকে বাঁশ, কাঠ, ছন এনে ঘর তুলতে পারে, কিন্তু সেই ঘর যদি একটা রাভাকন্যার শরীরও না হয়, কোথায় আশ্রয় পাবে পুরুষ! সেজন্যই ধানের জমি আর ধান, গৃহ আর সন্তান সবসময়েই রাভাকন্যার, রাভাপুরুষের নয়। পুত্রই হোক অথবা কন্যা, মায়ের পরিচয়েই পরিচয়, মায়ের গোত্রই গোত্র। জমি ধ্রুব, গৃহ ধ্রুব, জননী ধ্রুব। এই ধ্রুবতার আশ্বাস ছাড়া ধান আর সন্তান ভালো হয়?
জমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যচারী হওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা এলো। যেহেতু অরণ্য এখন যন্ত্রসভ্যতার চাপে বিলীয়মান। এভাবে উপন্যাসের শুরুতে অরণ্যচারী মানুষের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেন অমিয়ভূষণ। রাভা, যারা কিনা আদিতে কোচ ছিল, তাদের অরণ্যপ্রাণ বিনষ্ট, যন্ত্রসভ্যতার স্ফূরিত শক্তির নেতিবাচকতায় তাদের বিহ্বলতা, বেদনা আর রূপান্তরিত সময়স্রোতের তীব্রতাকে লেখক এ-উপন্যাসে ধারণ করেছেন। মোন্নাথ বা মোদনাথ, মলগুঁ দাস, তিন্নি কিংবা পঙ্কিনী রাভা – এরা সবাই নিজের ভেতর প্রগাঢ়ভাবে অরণ্যকে লালন করে। তবে রাভাসত্তার ধীরগতির রূপান্তরিত স্বর শুনতে পান লেখক। অনুভব করেন কেমন করে শাহরিক চাহিদা তৈরি হচ্ছে তাদের সত্তায়। বিলুপ্তপ্রায় এক অসুর জাতির কথা উদাহরণ হিসেবে টানেন তিনি। এ-এলাকারই উত্তর অংশে বা সদর শহরের পশ্চিমে চলা পথ ফেলে স্পর্শ করা এক মহাবনে বুনো মানুষের গোষ্ঠী থাকত। অগম বনের অন্তস্তলের সেসব বুনোগোষ্ঠী, যারা অসুর বলে পরিচিত ছিল, কিংবা বনের শ্যামলতার সঙ্গে মিল রেখে একদা যারা শ্যামল সাঁওতাল নামে পরিচিত ছিল, অমিয়ভূষণ মনে করেন, সেই মহাবনে বাস করতে এসে তারা যেন জাত বদলে ফেলেছে : ‘অরণ্যের অধিবাসীরা ভয়ে ভয়ে দূরে চলে গেল, হাতি, গণ্ডার, মোষ, মানুষ। কিন্তু ধরাও পড়ে, পোষও মানে। সেই চা বাগানগুলোয় কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালী, মুণ্ডা সব মিলে একটা নতুন পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে।’ অমিয়ভূষণের প্রশ্ন হলো, ‘সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেল, কেউ জানে না?’ না জানার বিষয়টি বেদনার। আদিবাসী অরণ্যপ্রাণ মানুষের অস্তিত্ব বিলীনের নীরব কথকতা এভাবেই বাক্সময় করে তোলেন অমিয়ভূষণ। স্বরাজ গুছাইত মন্তব্য করেন :
আরণ্যক সভ্যতা ভেঙে গেলে সেখানকার মানুষ ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। মানুষ নিজেই বন্য থেকে পোষ্যবিশেষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজের অজান্তেই ‘পোষা মানবজাতি তৈরি’ করে। যেমন পার্বত্য প্রদেশের ‘চা বাগানগুলোতে কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী, নেপালি, মুণ্ডা সব মিলে একটা নতুন পোষা মানুষজাতি তৈরি হচ্ছে, হয়েছে।’
এই রূপান্তরপ্রক্রিয়া অমিয়ভূষণ শুধু অরণ্যসভ্যতার ভেতর দেখেননি, দেখেছেন সময় ও প্রকৃতির ভেতরেও। আর তাই দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে বাঁকা-ত্যাড়া মহকুমা শহরের ঘাসে ঢাকা চত্বরের বর্ণনায় শুধু বলেন, ‘দপ্তরের চারিদিকে ঘাসে ঢাকা ঢেউতোলা মাঠ। ঘাসগুলো দূর্বাজাতীয় কিন্তু রোদে পুড়ে শক্ত ও কর্কশ হয়ে যেন জাত বদলাচ্ছে।’ সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য আরো একটি বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই অমিয়ভূষণ মহকুমা শহরটির যে-বিবর্ণ ছবি আঁকেন, সেখানে তিনি ‘দেখাতে চাইছেন যে সমস্ত অনুপুঙ্খে অনভিজাত তুচ্ছতার চিহ্ন নিয়ে গড়ে উঠছে এক বিকল্প বাস্তব অবস্থানের খাঁটি লোকায়ত চলচ্ছবি। … পৌর সমাজের ভূগোল-ইতিহাস-প্রত্নকথা-সমস্তই অন্তেবাসীর মাপে পুনর্নির্মিত।’ অর্থাৎ তাঁর ভাবনায়, অমিয়ভূষণ কেন্দ্রশক্তিকে প্রান্তজনের দৃষ্টিতে দেখতে সচেষ্ট, যে-পর্যবেক্ষণে কেন্দ্রশক্তির আপাত আভিজাত্য ভেঙে গিয়ে অনভিজাত তুচ্ছতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই কেন্দ্রশক্তির আভিজাত্যবোধের পরিবর্তে তিনি দুখিয়ার কুঠির মাতালু, রংবর কি কাঁকরুর আঞ্চলিক জীবনবোধকেই মুখ্যভাবে রূপায়িত করতে চান।
অরণ্যের সবুজ এখন যন্ত্রসভ্যতার লোভের আগুনে দগ্ধ বলেই অনুজ্জ্বল আর কঠিন। প্রযুক্তি ও পুঁজিবাদের লোভের থাবায় আরণ্যক জীবনের বিনষ্টি, অরণ্যপ্রাণ মানবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনমূল থেকে বিচ্যুতি, কখনো তাদের শেকড়বিচ্ছিন্ন পরাজিত সত্তার হাহাকার, সেই সঙ্গে যন্ত্রসভ্যতা আর কৃষিসভ্যতার মধ্যকার দ্বান্দ্বিক লড়াই, উঠতি পুঁজিপতিদের কালো হাত ধরে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জাত ক্ষয়িষ্ণুতার নানা রূপ, অর্থাৎ সমকালের পটে তাদের অস্তিত্ব-সংকটের স্বরূপ অমিয়ভূষণের এই চারটি উপন্যাসে প্রবলভাবে মূর্ত।
ইতিহাসপাঠে উপলব্ধি করা যাবে, ভারতে আর্যদের আগমনে অরণ্যবাসী মানুষের ভূমিচ্যুতি ঘটে। ফলে, আর্য আর আদিবাসীদের ভেতর এক বিশাল ব্যবধান রচিত হয়। ‘আর্য-ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল’, সেই ব্যবধান আজো বিদ্যমান। পরবর্তীকালে এ-ব্যবধান আরো বৃদ্ধি পায়। আর্যদের আগমনের পর আদিবাসী সমাজে পরিবর্তমানতার সূত্রপাত ঘটলেও তার গতি ছিল বেশ ধীর। ব্রিটিশ শাসনামলে দ্রুততর প্রক্রিয়ায় ব্রিজ-রাস্তা কিংবা রেলপথের প্রসার – সরকারি জঙ্গলের সীমা নির্ধারণে অরণ্য সংরক্ষণের আইন, আদিবাসী অঞ্চলে খনির কাজের প্রসার, জমিসম্পর্কিত আইন ও ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন,
ঋণ-সম্পর্কিত আইন আদিবাসী জীবনে নানা সংকটের জন্ম দেয়।
অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে অরণ্যপ্রাণ আদিবাসী জীবনে অস্তিত্ব-সংকটের যে-বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন, তার ভেতর অরণ্যহীন এক আগ্রাসী সভ্যতার প্রতিচ্ছবিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ‘কীভাবে এই সুবিশাল অরণ্য ক্রমে সংকীর্ণ ‘রিজার্ভ ফরেস্ট’-এ রূপান্তরিত হয়েছে, … যে অরণ্য একদিন তাদের
মাতৃসম আশ্রয়স্থল ছিল, কীভাবে সেই অরণ্য তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে আশ্রয়হীন করে তোলা হয়েছে, তাদের বিশ্বাস-রীতি-জীবিকার পথ সঙ্কুচিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, …।’ অরণ্য সংরক্ষণ আইনের মধ্য দিয়েও আদিবাসী মানুষের অধিকার খর্ব হয়। ১৮৭১ সালে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলের অরণ্য ‘সংরক্ষিত জঙ্গল’ বলে ঘোষিত হওয়ার পর জঙ্গলের গাছ সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হতে থাকে। সংরক্ষিত হলেও অরণ্যে আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারবোধ বজায় থাকবে – এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কার্যত জঙ্গল বিভাগই এর বিরোধিতা করে। ধীরে ধীরে এই সংরক্ষিত জঙ্গল ‘খাস সরকারি জঙ্গলে’ পরিণত হয়। অরণ্যখেকো দুষ্টচক্রের বৃক্ষনিধন আদিবাসীদের অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এছাড়াও অরণ্যপ্রাণ আদিবাসীদের স্বভূমিচ্যুতি প্রসঙ্গে সমালোচক সুবোধ ঘোষ লিখেছেন :
ভারতের সামন্ততান্ত্রিক-আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুষ্ট তথা ইংরেজ শাসকবর্গের প্রশ্রয়ে জমিদার-মহাজন-পুলিশ, ঠিকাদার-আড়কাঠিদের অত্যাচার-খাজনা, শ্রমশোষণ ও তাদের জঘন্য স্বার্থপরতার শিকার আদিবাসীসমাজ ক্রমে ‘শ্রমদাস’-এ রূপান্তরিত। জমিদারদের শোষণ পীড়ন, প্রতারণা মূলত আদিবাসীদের অরণ্যকেন্দ্রিক ভূমিকে কেন্দ্র করেই। … অরণ্য-পাহাড়ে আজন্ম লালিত-পালিত আদিবাসীরা অক্লান্ত শ্রমে অরণ্য সাফাই করে কিংবা পাহাড় কেটে বসত গড়ে তোলে, তৈরি করে চাষাবাদের যোগ্য জমি। কিন্তু … তাদের … ‘ভুঁইহারি’ জমি … রক্তে ফলানো ফসল বিনিময় প্রথায় অপহরণ করতে দ্বিধা করে না বহিরাগত ‘ইলাকদাররা’। … আদিবাসী সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দিয়ে শোষণের মূল প্রোথিত করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। … আদিবাসীদের বিচরণক্ষেত্র বসত অঞ্চলের মধ্যে ইংরেজ রেললাইন বসিয়েছে, স্থাপন করেছে ‘নীলকুঠি’, ‘রেশমকুঠি’, মিশনারিরা গড়ে তুলেছে পার্বত্য এলাকায় এক এক করে তাদের ‘মিশন’। ঠিক এভাবেই জমির মালিকানার রূপান্তর, বেদখল ‘খুটকাট্টি’ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ বা বাস্তুত্যাগ, ‘মহাজন-জমিমালিক-ঠিকাদার’ ও সরকারি আমলাদের নির্লজ্জ শোষণ, ভূমিদাস প্রথার প্রবর্তন, আদিবাসী রমণীদের নিয়ে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করানো, স্বকীয় সংস্কৃতি ও তাদের সমাজবন্ধন-ধর্ম-অনুশাসন ভেঙে দেওয়া … ইত্যাদি কারণে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ‘আদিবাসীকৃষি বিদ্রোহ’ সংঘটিত হয়।
উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই আদিবাসী মানবচেতনায় অস্তিত্ব-সংকটের বীজ রোপণ করে।
যন্ত্রসভ্যতার ক্রমপ্রসারণকে অমিয়ভূষণ সময়ের ‘অনিবার্য সম্মুখবেগ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুখিয়ার কুঠি উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘মানুষের অনিবার্য সম্মুখবেগেও একটি বেদনা লুকানো থাকতে পারে, এর বেশি কিছু বলার নেই।’ শুধু দুখিয়ার কুঠিতেই নয়, অনিবার্য সম্মুখগতির পেছনে লুকানো বেদনা তিনি অনুভব করেছেন হলং মানসাই উপকথা, সোঁদাল আর মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসেও। অরণ্য ধ্বংসকারী সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে চারটি উপন্যাসেই তাই কালো পিচের পথকে প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন, ‘সভ্যতার ‘অগ্রগতি’ যে বর্গবিভাজনকে আরো প্রকট করে দিলো, কৌম সমাজের প্রেক্ষিতে বিষাক্ত আরো – তাতে ‘কালো নদী’র প্রতীকে উপস্থাপিত সড়ক কৃষক জীবনে কার্যত নিয়ে এলো অন্ধকার, বিপর্যয় আর আত্মিক অবলুপ্তি। অমিয়ভূষণ প্রতিবেদনে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি নানাভাবে পুনরাবৃত হয়েছে।’ নতুন আর পুরনো পথের তুলনার মধ্য দিয়ে লেখক সামাজিক আর অর্থনৈতিক রূপান্তরের আভাস স্পষ্ট করে তোলেন।
আত্মবিস্তারের তাগিদে অরণ্য যে কৃষিজমিতে পরিণত হচ্ছে, কিংবা কৃষিজমি যে পরিণত হচ্ছে সড়কে, তার বেশ কিছু প্রকাশ লক্ষ করা যাবে দুুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে। রাজধানী থেকে ‘দ্যাখ দ্যাখ করে এগিয়ে’ আসা এক পথ আরণ্যক জীবনে যেমন বুনে দিয়েছে অস্বস্তির বীজ, তেমনি কৃষিজীবী সমাজেও এনেছে এক অনিশ্চয়তার আতংক। সড়কের আত্মবিস্তারে আবাদি জমির ওপর আকস্মিকভাবে স্তূপীকৃত উঁচু প্রাকারের চাপে শিষসমেত কাঁচা ধানের ছড়ার নোয়ানো মাথা যেন যন্ত্রসভ্যতার কাছে কৃষিসভ্যতার পরাজয়কেই প্রতীকায়িত করে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের অস্তিত্বগত টানাপড়েনও উচ্চকিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসে অরণ্যপ্রাণ মাতালুর চোখে কৃষিসভ্যতা আর যন্ত্রসভ্যতার মধ্যকার পারস্পরিক বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে পুরনো আর নতুন পথের স্বভাবগত তারতম্যে :
নতুন সড়ক পুরনো পথ ধরে চলছে না। এ দুটির চালই যেন আলাদা। পুরনো পথ চলত এঁকেবেঁকে, দু’পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। জমির শস্য বহন যে করবে, সে কর্তব্য পালন করাই যার পরম গৌরব, সে জমিকে খাতির না-করে পারে না। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে মতি বোঝা যায় না। মনে হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক, সেটা জমি এবং ফসলকে খাতির করা নয়।
কালো সড়ক যন্ত্রসভ্যতা বিস্তারের প্রতীক; ‘কথাটা সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি। এক্ষেত্রে রাজপথের অগ্রগতিতে সভ্যতার গতিটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে।’ যদিও এই একই সড়ক হয়ে উঠেছে অরণ্যপ্রাণ আর কৃষিজীবী গণমানুষের শেকড়ছিন্নতারও প্রতীক। মাতালুর খালি পায়ের নিচে সদ্য-মাড়ানো ধানের শিষ প্রগাঢ় এক আবেগের জন্ম দেয়। লেখক মাতালুর নগ্ন পা আর মালতির দাদার জুতো পরিহিত পায়ের মধ্য দিয়ে কৃষিজীবী আর উঠতি পুঁজিপতির জীবনের মধ্যে ভেদরেখা টেনে দিয়েছেন। জুতো একটা খোলস, সভ্যতার চাকচিক্যের অংশকে উপন্যাসে ভাটিয়ারা ধারণ করেছে, যারা যন্ত্রসভ্যতার ধারক। তাই পথই শুধু পালটে যায়নি, এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে জুতোও। যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতা কালো নদীর রূপকে কৃষকজীবনে ভাঙন সূচিত করেছে। এটি প্রতীকায়িত করেছে কালের বৈনাশিকতাকেই।
কালো পথ নিয়ে এলো নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীন এক যন্ত্রজীবী সভ্যতা। প্রতিকারহীনতার বেদনায় মাতালু দুখিয়ার কুঠির গভীরে চারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বের মূলে টান অনুভব করে। এ যেন শেকড় ওপড়ানোর বেদনা তার। আদিবাসী কৃষিজীবী মাতালু, রংবর কিংবা কাঁকরুর বেদনা এজন্য যে, এ-পথ কৃষিজীবীদের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনেনি :
অনির্দেশ্যকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে এই কালো-পথ। ওরা নিজেরাই কি জানে এই পথ ওদের কোথায় নিয়ে যাবে? … যে আদিবাসীদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই এই পথের, তাদের ভাগ্যদোষেই যেন পথটা এত কাছে অবস্থান করছে। আর সে অবস্থানের ফলে গদাধরের জলের মতো এই কালো প্রবাহও তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে যাবে। কিন্তু গদাধরের গেরুয়া জল রক্তধারাকে মলিন করে না। তার প্রবাহ কালো নয়।
অরণ্য মানুষের জন্য শুশ্রƒষার। কালো পথের কলুষতা নেই তার। কালো পথ যেমন সভ্যতার জন্য জীবিকার জোগান দেয়, তেমনি কৃষিজীবী অরণ্যবাসী-মনস্তত্ত্বে তাদের শেকড়হীনতায়
অস্তিত্ব-সংকটের ঝুঁকি তৈরি করে; তৈরি করে অভাববোধ। কাঁকরুর চোখে এ-অভাববোধ যেন ‘বিশ্বজোড়া’। মানুষের সত্তায় এক বাণিজ্যিক লোলুপতার বীজ রোপণ করেছে এ-পথ। তাদের মনে হয়, ‘শহরের লোকের লোলুপতা … আকস্মিকভাবে বেড়ে উঠেছে। আর সে-লোলুপতার সঙ্গে … এই কালো সড়কের যেন কোথায় একটা ঐক্য ধরা পড়েছে, যে-সড়ক চলমান কোনো সত্তার মত গ্রাস করেছে তার জমি। সব ফুরিয়ে গেলে মানুষ খাবে নাকি তারা?’ সমালোচক শুভঙ্কর ঘোষ মনে করেন, এভাবেই অমিয়ভূষণ ‘সভ্যতার’ অগ্রগতির ‘শ্লেষাত্মক’ প্রকাশ ঘটিয়েছেন এ-উপন্যাসে। পথ যেমন গ্রাস করেছে জীবিকার উৎস, তেমনি শহুরে মানুষের সীমাহীন লোলুপতা কি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের মানবিকসত্তাকে গ্রাস করবে না? এরকম একটা অব্যক্ত প্রশ্ন থেকেই যায়। কালো পিচের পথের যেমন সর্বগ্রাসী লোলুপতা, ভাটিয়াদের কন্যা মালতির চোখেও যেন তেমনি এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। অমিয়ভূষণ মনে করেন, ‘এই
অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য।’ ভাটিয়াদের সম্পর্কে ডাঙ্গর আইয়ের মূল্যায়নটাও অনেকটা এরকম। আইয়ের পুরনো স্মৃতি থেকে উঠে আসে ভাটিয়া ও আদিবাসীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস :
কোনো একদিন কোনো এক বড় যুদ্ধে বিজয়ী ভাটিয়ারা শক্তির এমন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার কথা আর চিন্তা করেনি আদিবাসীরা। তারা পালিয়েছিল। ভাটিয়াদের রক্তে এখন আর সেই শক্তি নেই, কিন্তু নির্মমভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা জন্মেছে। যার ফলে বুঝে-না-বুঝে তারা নির্দয় ব্যবহার করে। আর সেই পলায়নের পর থেকে আদিবাসীদের স্বভাবের মূলেও একটা পলায়নের সংস্কার জন্মেছে। যদি উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তবে ভাটিয়ারা স্রোতস্বতী নদী, আর আদিবাসীরা সরোবর। বদ্ধ জল বলতে পারো; কিন্তু জলের নিচে যেমন পঙ্ক, জলের বুকে তেমন কহ্লার কুমুদও ফোটে দু-একটা। শান্তির কথা মনে হয় তার পাশে দাঁড়ালে। একদিন সুতীব্র গতি পারভাঙা নদী আবর্তে আবর্তে মকর কুম্ভীর নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত দেখে কোনো কবি বলতে পারে, নদীর চুম্বনে সরোবরের বুকে আলোড়ন জাগছে, তারপর এক সময়ে কুমুদিনীরা হারিয়ে যায়, সরোবরের চিহ্নমাত্র থাকে না। প্রবল নদী সেই সরোবরের সবটুকু আত্মসাৎ করে নেয়। নদীর গতিপথে সরোবর নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়।
ভাটিয়াদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার নিয়তির টানে আদিবাসীদের অস্তিত্বগত বিনাশ ও বিলুপ্তিকেই লেখক এখানে প্রতীকায়িত করেছেন। লেখক মূলত পুঁজিবাদী সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশমান অবস্থাকেই এখানে তুলে ধরেছেন। মুদ্রা কেমন করে কৃষিসভ্যতাকে আত্মসাৎ করে সেটি এখানে স্পষ্ট।
গদাধরপুরে ক্রমবিকশিত নগরসভ্যতার নির্মাণ-শ্রমিক ও মালিকের যাপিত জীবনের অনৈতিক আখ্যান ধীরে গ্রাস করে দুখিয়ার কুঠির অরণ্যপ্রাণ কৃষিজীবী জীবনকে। ব্রিজ তৈরিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শ্রমিক বস্তি, শ্রমিক উপনিবেশ।
অরণ্যগ্রাসী কৃষিজমির প্রতীকে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসে। উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই অমিয়ভূষণ আরণ্যজীবনে অনুপ্রবিষ্ট সভ্যতার বৈনাশিক রূপ আঁকতে চেয়েছেন। মহিষকুড়া গ্রাম লেখকের চোখে ‘বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ’সদৃশ, যেদ্বীপের চারদিকে অরণ্যের বুক চিরে রয়েছে সভ্যতার ছাপ – কালো পিচের রাস্তা। অরণ্যই গ্রামটির প্রধান পরিচয় ছিল এককালে, যখন এ অরণ্য মুঘল-তাতার-তুর্কির মতো বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করত এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা। একালে সেই বীর্যবন্ত অরণ্য তার আশ্রিতের হাত থেকেই নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। ‘মুঘল-তাতার-তুর্কি যার কাছে হার মেনেছিল সেই বন যেন সাধারণ মানুষের ভয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। … এখন সে অরণ্য মানুষের কব্জায়। তার বুকে, যেন এক শত্রুরাজ্যকে শাসনে রাখতে, লোহার শিকল পরানোর মতোই বা, কালো কালো পিচের রাস্তা সড়ক। … কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও কোথায় যেন এক চাপা অশান্তি ধিক্ ধিক্ করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন।’ উপন্যাসে বর্ণিত এই চাপা ক্ষোভ অরণ্যগ্রাসী যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে আদিম অরণ্যের। অরণ্য যে মানুষগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই আজ ‘লোভের লাঙ্গলে’ চাষের জমির জন্য তার উচ্ছেদ সাধন করেছে। সভ্যতার অগ্রগতি কখনোই কৃষকশ্রেণি বা অরণ্যবাসী বা সর্বহারাদের জীবনে মঙ্গল বয়ে আনে না। উন্মূলিত অরণ্য আর সর্বহারা উন্মূল মানবাত্মা যেন অমিয়ভূষণের সাহিত্যে একাকার – কেননা অরণ্যের মতোই তপোধীর ভট্টাচার্য মনে করেন, ‘ধনতান্ত্রিক আধুনিক সভ্যতার নির্মম অগ্রগতির পথে চোরাবালি তো তৈরি হয়েই থাকে বাতিল ব্রাত্যজনকে গ্রাস করার জন্যে।’
মহিষকুড়ার আসফাক তার অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে, ‘… বন কোথায় আর? … এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কি?’ এ-উপন্যাসে জাফরুল্লা যন্ত্রসভ্যতার প্রতিনিধি, যার লেলিহান লোভ একে একে গ্রাস করেছে অরণ্য, অরণ্যবাসী মানবাত্মার স্বপ্ন আর তাদের অস্তিত্ব। সমালোচক বিজিতকুমার মনে করেন, ‘জমির আকর্ষণ অরণ্যকে ধ্বংস করছে। … তাঁর জীবনবোধ কৃষি সভ্যতার মধ্যেও শোষণ আর শাসনের চরিত্র দেখতে পান। জাফরুল্লার কর্মচারীদের মধ্যে চাউটিয়া, আসফাক, ছমির, সাত্তার, নসির-এর জীবনযাপনের মধ্যে মজুমদার বুনতে থাকেন পোষমানা বুনো মানুষগুলিকে’ এবং এই আদিম-অরণ্যপ্রাণ মানুষগুলোর মুখনিঃসৃত নির্মোহ সত্যেই উন্মোচিত হয় জাফরুল্লার লোভী
মুখোশ :
জাফরুল্লাই বনের মধ্যে ঢুকেছে। আগে এদিকে কার কতটুকু জমি আর কতটুকু বন তার খোঁজ কেউ রাখত না। গাছ কেটে চাষ দিলেই হলো। কোন্ আমলা এতদূর এসে জমির মাপ দেখে খাজনা নেবে। সেইবার সেটেলমেন্ট হলো। আর তখন সেই এক কাননগো এসছিল। জাফরুল্লার বাবা ফয়জুল্লার সঙ্গে তার ফিস্ফাস ফুস্ফাস ছিল। এখানে ওখানে বনের মধ্যে ঢুকে বনের জমিকে চাষের জমি বলে লিখিয়ে কি সব করে গিয়েছে। … ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এদিকে কোথায় বন, কোথায় তার সীমা, কোথায় কার কতটুকু জমি কেউ জানত না। একবার বন এগোত, একবার চাষের খেত। বনই পিছিয়ে যেত বেশির ভাগ।
কেমন করে অরণ্যবাসী আদিমপ্রাণ শেকড়-বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণায় সংকটে পতিত এবং শেকড়সন্ধিৎসা হয়ে ওঠে তাদের যন্ত্রণামুক্তির একমাত্র হাতিয়ার – এ উপন্যাসগুলোতে সেই বিষয়গুলোর ওপরেই জোর দিয়েছেন অমিয়ভূষণ। লেখক এ-বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এক একটি চরিত্র বেছে নিয়েছেন, যাদের চোখে তিনি সময়ের-সভ্যতার এবং ব্যক্তিসত্তার ক্রমরূপান্তরকে ধরতে চেয়েছেন। আরণ্যক সভ্যতাকে আদিপ্রাণ মানুষের কেন্দ্র বিবেচনা করলে অনুভূত হবে, প্রযুক্তি ও যন্ত্রজীবন আরণ্যক মানবের শেকড়চ্যুতি ঘটিয়ে তাদের প্রান্তিক করে তোলে।
কালো পিচের পথ গ্রাস করেছে হলং মানসাই উপকথার কৃষিজীবী মানুষের অস্তিত্ব। মৃত্তিকার গভীরে চারানো শেকড় বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাও এনে দিয়েছে সেই কালো পিচপথ।
হলং নদ বা নদীর জন্মকথা দিয়ে হলং মানসাই উপকথা উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে, যেখানে এসেছে পাহাড় বা পাহাড়িদের জীবনপ্রসঙ্গ। একালের যন্ত্রসভ্যতাচারী মানুষের সঙ্গে শুরুতেই অমিয়ভূষণ পার্থক্য টেনে দেন অরণ্যচারী প্রাণের, যারা নদীকেই পথের প্রাণ ভাবত। অন্যদিকে অরণ্যপ্রাণবিনাশী সড়ক ধরেই বাঙালির চলাফেরা। হলং নদ যেখানে মানসাই নদীকে স্পর্শ করতে চায়, তার খুব কাছেই নব্য শহর হয়ে ওঠার ঝোঁকে ব্যগ্র এক গ্রাম ‘উখুণ্ডি’কে কেন্দ্র করেই এ-উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই অরণ্যময় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপ নির্লিপ্ত ও অনুপুঙ্খ দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপায়িত করেন :
… মাটি পুড়িয়ে ইট, এমন সে পোড়ানি যে মাটির হয় আগুনে রঙ। … পাথর পুুড়িয়ে চুন, পাথর পুড়িয়ে সিরমেট। তাই দিয়ে সড়ক, বাড়ি-ঘর। … সেই ইটের সড়কের উপরে ধোঁয়া ওঠা আগুনে গরম সেই এক, যাকে কালো আগুনও বলতে পারো। … পিচের সড়ককেই যদি ততো গরম বলা হয়ে যায়, সেই পথে ছোটা ফুটন্ত পেট্রলের বাসের আর আকাশের গায়ে বসানো ইলেকট্রিক তারের উত্তাপ বোঝাতে কোনো শব্দই অবশিষ্ট থাকবে না। … সভ্যতা আর আগুন কি প্রায় সমার্থক নয়? সুতরাং বাঙালিদের আগুন কি কোচ, কি রাজবংশীতেও ঢুকে পড়ছে। … এখন গ্রামগুলো নদী বরাবর বসে না, বসে সড়ক বরাবর আর যদি বা নদীর কাছে আসে সে সড়ক তবে তো কথাই নেই; যে গ্রামের মাঝ দিয়ে সে সড়ক সে গ্রাম তো ফুলে ফেঁপে শহর।
উখুণ্ডিও এমনই এক শহর। উঠতি এই শহর কাম গ্রামে চাষের জমিতে করাতকল, ধানকল, বয়লার, শিক্ষিত হওয়ার জন্য স্কুল, পঞ্চায়েত কি পুলিশের তাঁবু, এমনকি বিনোদনের জন্য তিনঘরের বেশ্যাপল্লিও মজুদ রয়েছে। অমিয়ভূষণ খুব সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরের রেখাগুলো টানেন। শুধু হলং মানসাই উপকথাতেই নয়, দুখিয়ার কুঠি কিংবা মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসেও রূপান্তরের এই চিত্র এঁকেছেন তিনি। যে-অরণ্য গণমানুষের শেষ আশ্রয়, যে-অরণ্য নিজের গহিনে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল, তারাই আজ লোভের হাত বাড়িয়ে চাষের জমির জন্য গ্রাস করছে তাকে। মাঝেমধ্যে আবার উলটোটাও ঘটে। প্রকৃতিও যন্ত্রসভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। বারবার মন বদলানো মোচড়-খাওয়া হলং নদী সড়ক আক্রমণ করেছে। ‘কখনো হলং তার কাঠের সাঁকোর পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, কখনো মানসাই চর ডুবিয়ে সরে এসে সড়ককে বিপন্ন করেছে। সড়ক সরলে দেখা যায়, এক-মাইল আধ-মাইল বাঁধানো সড়ক পড়ে থাকল আর নতুন আর পুরনো সড়কের মধ্যে বন জঙ্গল তৈরি হচ্ছে।’ কিংবা, ‘… পরিত্যক্ত পথটার ফুট পঞ্চাশ চওড়া, একশো ফুট লম্বা অংশ এখনও পিচে বাঁধানো। এই অংশটার দক্ষিণে সড়কটা কীভাবে ভেঙেছিল, সেখানে ইতিমধ্যে একটা বন গজিয়েছে।’ কাজেই অরণ্য তার চাপা ক্ষোভ থেকেই অগ্রসরমান সভ্যতাকে গ্রাস করে তার পুরনো রূপে ফিরে যেতে চায়। লোভের আগুনে যতই অরণ্য বা অরণ্য-অবলম্বী প্রাণের বিনাশ ঘটানো হোক না কেন, অমিয়ভূষণ মনে করেন, ‘বন পুড়িয়ে ফেলেও এখন আর তুমি কিছু করতে পারো না। বনের বিশ্বাসঘাতকতায় রাগ না ভয়, কোনটা বেশি হওয়া উচিত, তা কেউ বলতে পারবে না।’ কিন্তু তবু বনই আদিবাসী অরণ্যচারী প্রাণের আশ্রয়। ‘বন না থাকলে মানুষ কোথায় মুখ লুকাতো?’
হলং বন আর মানসাইঘাট শহরের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক রূপান্তরশীল সময়কে ধারণ করেন। সেই সময়, যখন আদিম অরণ্য যন্ত্রসভ্যতার জাঁতাকলে বন্দি। অরণ্য তার বীর্যবন্ত সত্তা নিয়ে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠেছে উঠতি শহর মানসাইঘাট। লেখক অরণ্য আর সভ্যতার দ্বন্দ্ব রূপায়িত করতে গিয়ে লিখেছেন, ‘বনের মধ্যে দিয়ে পুরনো সরু রাস্তা ছিল। পরে বাসট্রাকের সড়ক করতে গিয়েই বন কাটা হচ্ছিল। বারে বারে সড়ক সরতেই বন আবার তার পুরনো জমি দখল করছিল।’ এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রসভ্যতাই জয়ী হয়।
দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসের মতো মানসাই নদীর ওপর পাঁচ বছর ধরে ব্রিজ নির্মিত হচ্ছে, এই বছরপাঁচেকের পরিবর্তনের চিত্রচ্ছবি রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে :
উখুণ্ডির জীবনের ভারসাম্য ইতিমধ্যে নষ্ট হতে বসেছে। … সেখানে যে মানুষজনের ভিড় তার সংখ্যা উখুণ্ডির জনসংখ্যার পাঁচ-ছয়গুণ তো হবেই। হুড়হুড় করে একটা শহরই গড়ে উঠেছে। … সেখানে সব মানুষ যেন একই টানে কাজ করতে ছুটে চলেছে, অথচ কেউ কাউকে চেনে না।
কেউ কাউকে না চিনবার বিষয়টিতে কৌমজীবনের ভগ্ন স্বরই উচ্চকিত, যে-জীবনের সময়গুলোও খণ্ডিত (ঢ়বৎরড়ফ)।
সোঁদাল উপন্যাসেও সভ্যতার এই অনিবার্য সম্মুখবেগ লক্ষ করা যাবে। বড় গ্রাম কি শহর রূপান্তরের গন্ধ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। একটি মহকুমা শহরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটলেও এখানকার শহর আর গ্রামে তেমন ব্যবধান দেখানো হয়নি। বরং গ্রাম কিংবা শহর এখানে একইরকমভাবে পরিবর্তনশীল। এবং অরণ্যহীনতায় গ্রাম আর শহরের ভেতর আর কোনো আব্রু আড়াল থাকছে না। গ্রাম যে শহরের অভিমুখী, সেটিও উপন্যাসে স্পষ্ট করে দিয়ে লেখক লিখেছেন :
অন্ধকার, অন্তত আধো-অন্ধকার, সবুজ মেশানো কালচে অন্ধকার থেকে হলুদ-ধূসর-উজ্জ্বল সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে জেলাকে জেলা। আর সবই এই গত কয়েকটা বৎসরে। গ্রামগুলোর মধ্যে মধ্যে, গ্রাম আর শহরের মধ্যে এই অবস্থায় আড়াল, আবডালও থাকে না। গ্রামের লাগালাগা বন দূরের কথা, বনের সঙ্গে লাগালাগা দু-চার হাজার একরের ছোট বন ঠিক দু-বছরের মাথায় ধানখেত, পাটখেত, গ্রাম আর গঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কী অদ্ভুতভাবে, অলস, ভবিষ্যৎদ্দৃষ্টিহীন, আদিম মনের মানুষেরা ছিল এখানে।
আদিম মনের আরণ্যক মানুষেরাও আজ নিশ্চিহ্নপ্রায় কিংবা ক্রমপ্রসারমান সভ্যতার প্রভাবে মিশ্র এক সংস্কৃতির সন্তান হয়ে বেঁচে আছে, কিংবা অস্তিত্ব-সংকটে ভুগছে। অরণ্যবাসী মানুষ এককালে যে উদ্বেগহীন জীবনযাপন করেছে, ধীরে ধীরে সে-জীবনে কালো সড়ক এনেছে জটিলতা। এক অরণ্যঘন সমৃদ্ধ জীবন আজ অতীত বলেই হয়তো অমিয়ভূষণ নির্মূলপ্রায় অরণ্যের বর্ণনায় ‘ছিল’ শব্দ ব্যবহারে পুনরাবৃত্তি ঘটান। বন এখন মানুষের লেলিহান লোভে উজাড়। কেননা তারা তাদের লোভী সত্তায় লালন করেছে আরো বেশি খাদ্যের নিরাপত্তা। লেখকের ভাষায় :
এক মেহগ্নি থেকে আর এক তেমন মেহগ্নি হতে দুশো বছর লেগে যেতে পারে, একটা বন হতে হাজার বছর লেগে যায়। একটা ধানখেত তৈরি হয় এক বছরে। এক মরসুমে হাজারটা ধান আনে। এই আবিষ্কার থেকেই তো মানুষ মানুষ হলো। যদি এক মুঠো ধান লাগালে গোলা ভরে ওঠে … বনের মধ্যে কোদালের জুমচাষের চাইতে বন হাসিল করে লাঙ্গলের চাষ অবশ্যই ভালো।
এভাবেই অরণ্য উচ্ছেদ হয়ে যায়। রাভাগোষ্ঠীর ভূমিকেন্দ্রিক অস্তিত্ব-সংকটও মূর্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসে। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন :
অমিয়ভূষণ রাভা উপজাতির অস্তিত্বের সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। রাভা উপজাতি কীভাবে ক্রমবিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা দেখানোই তাঁর অভিপ্রায়। সর্বাধিক সংকট হলো ভূমির অধিকারের সংকট। আদিবাসীরা একসময়ে মনে করতেন আকাশ, মৃত্তিকা, অরণ্য, পর্বত, নদী, প্রান্তর – এসবের কোনো মালিক নেই। সকলের ব্যবহারের জন্যই এইসব। তাই ভূ-সম্পত্তির অধিকার এবং সেই অধিকারের ভাগাভাগি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ মানবসভ্যতার বিবর্তনে দেখা গেল বিত্তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভূ-সম্পত্তি। জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। জমি অধিকার করবার জন্য লোলুপ হয়ে ওঠে সম্পত্তি-সন্ধানী মানুষে। আদিবাসীরা বহুদিন পর্যন্ত এসব বুঝতেন না বলে যে কোনো জায়গায় সুবিধামত ফাঁকা জমি কিনে নিয়ে গড়ে তুলতেন কুঁড়ে ঘর, চাষ করতেন, বংশবৃদ্ধি হত। কিন্তু এভাবে অধিকার কায়েম করা যায় না। তাঁদের কোনো জমির পাট্টা নেই। তাই তাঁরা সহজেই হয়ে গেলেন ভূমিহীন। সরল মানুষগুলিকে কখনো উৎখাত করে, কখনো সামান্য কিছু টাকা দিয়ে তাঁদের উদ্বাস্তু করে দেয় লেখাপড়া জানা মানুষ। এভাবেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, শবর এবং রাভা – সকলেই হারিয়েছেন তাঁদের জমি।
মোন্নাত অরণ্যসভ্যতা থেকে কৃষিসভ্যতা আর কৃষিসভ্যতা থেকে যন্ত্রসভ্যতার এই ক্রমরূপান্তর অনুভব করতে পারে। তার উপলব্ধি, ‘ধান উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে পরিবর্তন আসে।’ ধান উৎপাদন পদ্ধতিতে অরণ্য কেটে চাষের জায়গা হলো। উত্থান ঘটল কৃষিসমাজের। আবার লাঙলের পরিবর্তে যন্ত্র এলে ক্ষয়িষ্ণু
কৃষিসমাজের স্থলাভিষিক্ত হলো যন্ত্রসভ্যতা। যন্ত্রসভ্যতায় অরণ্যহীনতা রাভা সমাজের পুরুষকে করে তোলে কর্মহীন। কারণ রাভা সমাজে নারীরাই জমির মালিক। নারীর শরীরের শান্তি পেতে রাভা পুরুষেরা তাদের কাজে সহায়তা করে। যখন সেই নারীই নেই, তখন পুরুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে অরণ্য। কিন্তু সভ্যতা এখন অরণ্যগ্রাসী। কাজেই রাভা পুরুষেরা অস্তিত্ব-সংকটে পতিত, নিরাশ্রয়। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগ সোঁদাল উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ‘বন অথবা বনের পাশের জমিকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা তার আশ্রয় হয় নারী না হয় বন।’ সমালোচকের এ-মতের সঙ্গে একমত পোষণ করা দুরূহ। কারণ সভ্যতার আশ্রয় কখনো বন হতে পারে না। বরং প্রকৃতিকে বিনাশের মধ্য দিয়ে সভ্যতা তার কলেবর বৃদ্ধি করে। বলা যেতে পারে, ক্রমপ্রসারমান যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে বিনষ্ট আদিপ্রাণ মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠে অরণ্য, কিংবা অরণ্যগন্ধী নারী। সোঁদালে যেমন তিন্নি। সোঁদালের হলুদে জড়ানো তিন্নি অরণ্যের আরেক নাম।
অরণ্যবাসী মানুষের প্রান্তিকতম যাপিত জীবনের ছবি ধরা পড়েছিল এ-উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোন্নাতের চোখে। অরণ্যে চলতি পথে বনবিভাগের দয়ায় প্রাপ্ত কুঁড়েগুলো দেখে মোন্নাত উপলব্ধি করেছিল, তারা আর বনের মানুষ নয়। ‘বনবিভাগের দয়ায় পাওয়া ছোট ছোট জমিতে তারা মকাই ফলায়, নিজেদের হাতের তৈরি কাঠ, খড়, বাঁশের তৈরি বাড়িতে হলুদ আর শীর্ণ হয়ে হয়ে বাস করে।’ আদিবাসী যারা, তাদের সত্তায় এখন শহুরে গন্ধ। মৈচন্দ্রের মেজ ছেলেও মনে করে, কৈচন্দ্র আর রাজবংশী নেই, সে এখন সাহেব। পিচঢালা সড়কের হাত ধরে তাই আধুনিকতার আগমন ঘটে – বনবাসী আদিম মানুষ হয় শেকড়হীন।
বাংলা সাহিত্যে যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনের চিত্র শুধু অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্যেই উঠে আসেনি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক (১৩৩৯), মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার (১৯৭৯) উপন্যাসের কথা। আরণ্যক উপন্যাসে বর্ণিত আজমাবাদ-লবটুলিয়া-ফুলকিয়া-সরস্বতী কু-র ঐন্দ্রজালিক সৌন্দর্যের রহস্যময়তাও একসময় সভ্যতার ক্রমপ্রসারণে ধ্বংস হয়। সত্যচরণ যে-অরণ্যদেবীর শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছিলেন, নিজের হাতেই তার সৌন্দর্য হরণ করতে গিয়ে বেদনার্ত হন তিনি। প্রকৃতি দেবীর মোহনীয়তার পাশাপাশি সভ্যতার কুৎসিত মুখ তাকে ক্লান্ত করে :
প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়া ঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান কত স্বপ্নভূমি জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল একদিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।
নাড়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র।
সত্যচরণের গাঢ় উপলব্ধি সভ্যতার অনিবার্য অগ্রসরমানতা ‘ধরণির মুক্তরূপ … কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া’ বস্তিতে পরিণত করেছে। উপন্যাস শেষে তাই প্রায় অবলুপ্ত অরণ্যের কাছে নতজানু প্রাণে তার ক্ষমা প্রার্থনা, ‘হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়।’ কিন্তু অরণ্য কি আদৌ ক্ষমা করে? যার বুকের ওপর দিয়ে ‘হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝরঝর করে লরি-ট্রাক, কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে’ – তার বুকে কী চাপা অশান্তির আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে না? অমিয়ভূষণ উপলব্ধি করেন, অরণ্যের ‘কোথাও এমন আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানবগোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করে।’ অরণ্য তাঁর কাছে অবচেতন মনের মতো জটিল, রহস্যময়। তবু সেই রহস্যঘন অরণ্যে এক চিলতে অস্ফুট আবেগের মতোই আরণ্যক মানুষ তার জীবন গড়ে নেয়। মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসে যেমন কালো মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অরণ্য-প্রকৃতিতে বাস করে রচনা করে নেয় বেঁচে থাকার আশ্রয়-অবলম্বন, সে-অরণ্য মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীলদের কাছে আদিমাতা। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় সেই আশ্রয়দাত্রীকে কর্ষণের নামে ধর্ষণ করে জমিদার-মহাজন-দিকু-বেনে-আড়কাঠি সাহেব। তবু ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী বিশ্বাস করেন, বীরসার মতো অরণ্যপ্রাণ মানুষ ‘অরণ্যকে ছিনিয়ে নেবে দিকুদের কাছ থেকে দখল। অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে।’ এই অশুচিতা দূর করার আকাক্সক্ষা মুণ্ডাপ্রাণে প্রবল। কারণ ‘অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।’ শুধু অরণ্যের অধিকার উপন্যাসেই নয়, চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর উপন্যাসেও ধানীর বক্তব্যে একই বেদনার অনুরণন ঘটেছে। ধানীর মনে হয়, ‘জঙ্গলটা কাঁদত। তারে বলত,
দিকুতে-মালিকে-সাহেবে – সব মিলে মোরে অশুচ, লেংটা, বেবস্তর করে দিয়াছে…।’ মহাশ্বেতা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অমিয়ভূষণ এভাবেই আরণ্যক জীবনের বিনষ্টির চিত্র রূপায়িত করেন উপন্যাসে।
আদিপ্রাণ আরণ্যক মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব-সংকট প্রকাশ করতে গিয়ে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিক রূপের নানা মাত্রা স্পষ্ট করে তোলেন। যন্ত্রসভ্যতা আদিপ্রাণ মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস ও যাপিত জীবনের শান্তি বিনষ্ট করে তাদের সত্তায় লোভ-সংশয়-হতাশার বীজ রোপণ করে। আদিপ্রাণ মানুষের জীবনে জড়িয়ে থাকা অরণ্য বিনষ্ট হয় যন্ত্রসভ্যতার লোভের লাঙলে। ফলে তারা শেকড়বিচ্ছিন্নতার স্বাদ পায়। অস্তিত্ব-সংকট আরো গাঢ় হয় তখন। সময়ের প্রবল অভিঘাতে রূপান্তরিত সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে কেউ কেউ সমূলে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, কেউ-বা সেই প্রবল আঘাতের ঘাত-প্রতিঘাত উতরে গিয়ে অরণ্য আর স্বসংস্কৃতি আঁকড়ে আদিপ্রাণ ধরে যন্ত্রসভ্যতার বৈনাশিকতার বিরুদ্ধে তাদের মৌন লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটায়। অরণ্যই হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র আশ্রয়। অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে বৈরী সময় আর সভ্যতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো প্রবল অস্তিত্ববান এসব আদিপ্রাণ মানুষের জীবনকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে মাতালু আর কাঁকরুর নিরন্তর লড়াই, অরণ্যের উত্তরাধিকার ধারণে চন্দানির অরণ্যে যাপিত জীবন, লেদু মিঞার আত্মোৎসর্গ, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নে মোন্নাতের অরণ্যে আশ্রয়-অন্বেষণ কিংবা অরণ্যহীনতায় আব্রুহীন ধর্ষিত তিন্নির শহর-অরণ্য-রাজনীতি আর পুঁজিবাদী-অর্থনীতির বিনষ্ট মুখাবয়বের সঙ্গে নীরব দ্বন্দ্ব কিংবা নির্বীর্য আসফাকের সত্তায় প্রগাঢ় বীর্যবান মোষের আরণ্যকস্বর – অমিয়ভূষণের এসব উপন্যাসকে প্রাণ দিয়েছে। অরণ্য আর কৃষিসভ্যতার বিরুদ্ধে আত্মসর্বস্ব যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার, আরণ্যক আদিপ্রাণের বিরুদ্ধে উঠতি পুঁজিপতিদের আগ্রাসন, রাজনীতির কলুষিত মুখাবয়ব কিংবা রূপান্তরিত অর্থনীতির আগ্রাসনে মূল্যবোধ-বিশ্বাস-যাপিত জীবনের পরিবর্তন – এ সবকিছুর মিথস্ক্রিয়ায় অমিয়ভূষণ মূলত সময়কেই ধারণ করেছেন। সেই ক্রমরূপান্তরিত সময়ের অভিঘাতে আদিপ্রাণ মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের প্রগাঢ় স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে এইসব উপন্যাসে।

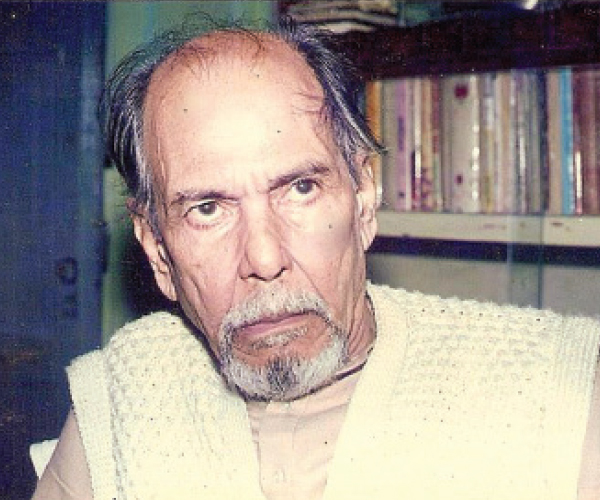
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.