সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সকলেই যে দার্শনিক তা মোটেই নয়, এমনকি দর্শনের আনুষ্ঠানিক ছাত্রমাত্রেই যে ওই রকমের একটা দাবি রাখতে পারবেন তাও নয়, তবে এটা খুবই সত্য যে সব মানুষের ভেতরেই এক ধরনের দার্শনিকতা থাকে, কম আর বেশি। এটি নিহিত রয়েছে মানুষের চিমত্মাশক্তির ভেতরেই। এমনকি যিনি বলেন, এবং অনেকেই বলেন সেটা অধিকাংশ সময়েই, যে কিছুই বুঝলাম না, তিনিও একটি দার্শনিক উক্তিই করেন, না-বুঝে। বুঝবার যে-চেষ্টা সেটাই প্রাথমিক স্তরের দার্শনিকতা। একটু উঁচু স্তরে উঠলে চেষ্টার দার্শনিক পরিচয়টা ধরা পড়ে যায়। দর্শনের স্বভাবটা আরো পরিষ্কার হয় ওই চেষ্টাটা যখন কেবল পৃথিবীকে বুঝবার আগ্রহের ভেতরে আটকা থাকে না, পৃথিবীকে বদলাবার চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। বুঝবার এবং বদলাবার চেষ্টাটা বুদ্ধিজীবীরাও করে থাকেন। পার্থক্যটা বোধ করি এইখানে যে, দার্শনিকেরা একটি বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলেন, বুদ্ধিজীবীরা সেটা যে সবসময়ে করেন তা নয়। বুদ্ধিজীবীরা যা না করলেও পারেন দার্শনিকদের জন্য সেটা করা বাধ্যতামূলক। দার্শনিকেরা সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকেন, এমনকি যাঁরা সমেত্মাষের প্রবক্তা তাঁরাও। অসমেত্মাষই চিমত্মার জন্ম দেয়।
নিজে আমি দর্শনের খোঁজখবর অল্পস্বল্প পেয়েছি। তা থেকেই বুঝেছি এই বিদ্যা কত প্রয়োজনীয়, আকর্ষণীয় ও গভীর। আমার দুঃখ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি বিদ্যাটি অধ্যয়ন করতে পারি নি। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, ক্লাসরুমে পড়া এবং নিজে নিজে পড়ার ভেতর বিস্তর পার্থক্য। যথার্থ পাঠ আসলে সামাজিক পাঠ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমার পাঠ্য ছিল সাহিত্য। পড়তে গিয়ে পদে পদে টের পেয়েছি যে সাহিত্য মহৎ হয় তার ভেতরকার দার্শনিকতার কারণে। বিশ্বে এ-পর্যন্ত এমন কোনো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি যার ভেতরে গভীর দর্শন নেই। লেখকমাত্রেই একজন অঘোষিত দার্শনিক।
তা দর্শনের আসল ব্যাপারটা কী? পৃথিবীকে বুঝবার যে-চেষ্টার কথা বলছি তারই অপর নাম হচ্ছে জ্ঞানের অন্বেষণ। আর সেই অন্বেষণটা আসে কৌতূহল থেকে। কৌতূহল জিজ্ঞাসা তৈরি করে দেয়। জ্ঞান এগোয় জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়ন থেকে। জ্ঞান সেভাবেই বস্তু সংগ্রহ করে থাকে। অধ্যয়নও এক ধরনের অভিজ্ঞতা বইকি, এবং অধ্যয়ন কেবল যে গ্রন্থের হয় তা নয়, হয় জগতেরও।
দর্শনে যুক্তি থাকে। যুক্তি ছাড়া দর্শন খোঁড়া; এক পা সে এগোয় না, এগোবে বলে ভরসাও করে না। সংগৃহীত তথ্যগুলো জ্ঞান হয়ে ওঠে যুক্তির আনুকূল্য ও পারম্পর্য পেলে। চিমত্মাগুলো তখন বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে চলে যায়। দর্শন সাধারণীকরণ করে। বিশেষের ভেতর সে নির্বিশেষের সন্ধান পায়, আবার নির্বিশেষকে প্রয়োগ করে বিশেষের ক্ষেত্রে। আরোহণ ও অবরোহণ দুটোই চলে, পাশাপাশি। আর এইখানেই টের পাওয়া যায় যে সাহিত্য থেকে দর্শন আলাদা। সাহিত্য কাজ করে বিশেষকে নিয়ে। বিশেষ সময়ের নির্দিষ্ট মানুষ, তার অভিজ্ঞতা ও অনুভবই হচ্ছে সাহিত্যের বিচরণক্ষেত্র। কিন্তু এই বিশেষের ভেতর অকাতরে নির্বিশেষ চলে আসে। সেজন্যই তো আমরা বলতে পারি যে, সাহিত্য সর্বজনের ও সর্বকালের। কিন্তু সাহিত্য তার কালেরই সর্বপ্রথমে। নিজের কালের বাস্তবতাকে সে নিজের মধ্যে ধারণ করে। আর ওই বাস্তবতার ভেতর সমকালের চিমত্মা, ধ্যান-ধারণা সবই এসে যায়। অর্থাৎ আসে দর্শন। এক কথায়, সাহিত্যিক যা করেন তা হলো তাঁর সময়ের তো অবশ্যই, আগের কালের দর্শনকেও নিয়ে আসেন নিজের সৃষ্টির ভেতরে। দর্শনের সাহায্য না পেলে সাহিত্যিকের রচনা সাড়া দেয় না, সাড়া ফেলে না; হাল্কা হয়, উড়ে যায়, উবেও যায়। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে দর্শন অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে এবং একটা নিজস্ব অবয়ব ও রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। গভীর ও স্থায়ী হয়।
এই গভীরতা মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করে থাকে। দার্শনিকেরাই বলেছেন এ-কথা যে, মানুষকে চিনতে হলে চিড়িয়াখানাতে বানরের খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বেশ একটা সুবিধা হয়। দেখা যাবে বানরটি কেমন অস্থির; খাঁচার বাইরে যা কিছু ঘটছে তাতেই সে চঞ্চল হচ্ছে। দর্শক কিন্তু স্থির হয়ে দেখছেন। মানুষ যে স্থির থাকতে পারে তার কারণ মানুষের ভেতরে বস্তু থাকে। আর ওই বস্তুটাকে যদি দর্শন বলি তাহলে এমন কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না।
অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তুলনাটা যখন এলোই তখন এই বিরূপ ধরণিতে মানুষ কেন টিকে আছে, অন্য অনেক প্রাণী কেন বিলুপ্ত হয়ে গেল সেই প্রসঙ্গটা আসতে পারে। যেমন ডাইনোসর। অতিকায় প্রাণী। অনেক কাল টিকে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নি। কেন যে পারে নি সেটা ডাইনোসরের চেহারার দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে। গাছের ডালে সে থাকে নি ঠিকই, তবে তার গলা ছিল লম্বা, মাথাটা খাটো, হাত ছিলই না। গলা লম্বা হয়েছে খাদ্যের অন্বেষণে; মাথা খাটো, কারণ বুদ্ধির চর্চা নেই; ওদিকে আবার হাতের ব্যবহার একেবারেই জানে না। শেষমেশ বেচারা তাই নিশ্চিহ্নই হয়ে গেল। মানুষ টিকে আছে কারণ তার মসিত্মষ্ক আছে, হাত আছে, সে হাতিয়ারের ব্যবহার জানে, সে সৃষ্টিশীল। কিন্তু এই মানুষ কি শেষপর্যন্ত টিকবে? এ প্রশ্নটা একালে বেশ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গটিতে একটু পরে আমরা আবার ফিরে আসবো।
সৃষ্টিশীলতায় মানুষ অন্যসকল প্রাণীকে ছাড়িয়ে গেছে। মাকড়সার বুনন, পিঁপড়ের সঞ্চয়, মৌমাছির স্থাপত্য, সবই আয়ত্তে তার; সবকিছুকে ধারণ করে মানুষ ক্রমাগত বড় হয়ে উঠেছে নিজের চিমত্মাশক্তি ও কল্পনাশক্তিতে। এই শক্তি তার জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই সে মানব সভ্যতার সৃষ্টি করতে পেরেছে। এবং নিজেও বদলে নিয়েছে নিজেকে, চলার পথে।
বিজ্ঞান এক সময়ে ছিল না, দর্শনই তখন বিজ্ঞানের কাজটা করতো। তারপর বিজ্ঞান এসেছে, এবং বিজ্ঞান ও দর্শন স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান চলে গেছে বিশেষ ক্ষেত্রে, মনোযোগ দিয়েছে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে। দর্শন অক্ষুণ্ণ রেখেছে তার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রটিকে। এক কথায় বিজ্ঞানীরা বিশেষজ্ঞ হয়েছেন, দার্শনিকেরা সেটা হন নি।
বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন বিশ্ব গভীর এক সংকটের মধ্যে পড়েছে। মানুষের নিজের জগৎ ও প্রকৃতির জগৎ উভয়েই ভীষণ অসুস্থ। প্রকৃতি রুষ্ট; তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, সে প্রতিশোধ নিচ্ছে – নীরবে ও সরবে। নীরবে বরফ যাচ্ছে গলে, সমুদ্রপৃষ্ঠ উঠছে উঁচু হয়ে, ভূপৃষ্ঠের নিম্নাঞ্চল যাবে পানির নিচে ডুবে, আবার মহাসমুদ্রের কিছু কিছু অংশ যাচ্ছে মরে। অভাব দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির। তপ্ত হয়ে উঠেছে ধরিত্রী। মারাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে বিশ্বজলবায়ুতে। সশব্দে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস। বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন। তাঁরা ভাবছেন, এভাবে চললে সভ্যতা তো অবশ্যই, মানুষই হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
বিজ্ঞানীরা রোগটা দেখছেন। পরিষ্কারভাবে লক্ষণগুলো টের পাচ্ছেন। কিন্তু রোগটা যে কী তা বলছেন না। হয়তো সংকোচ করছেন, হয়তো ভাবছেন কথাটা অভদ্র শোনাবে। নিজেদের ভেতরকার ভদ্রতাতেও বাঁধছে। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা অতদূর যেতেও অভ্যস্ত নন। দার্শনিকেরা কিন্তু যান। তাঁদেরকে যেতেই হয়। নইলে তাঁরা দার্শনিক হবার যোগ্যতা হারান। এবং দার্শনিকেরা বলবেন, না-বলে পারবেন না, যে রোগটার নাম হচ্ছে পুঁজিবাদ। তা রোগটাকে না চিনলে তার চিকিৎসা হবে কী করে?
পুঁজিবাদ মুনাফা বোঝে, মুনাফা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। মুনাফার লিপ্সায় সে মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে। পুঁজিবাদ যুদ্ধ বাধায়; ছোটখাটো যুদ্ধ এবং বিশ্বমাপের যুদ্ধ। একটি নয়, দুই-দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সে ইতিমধ্যেই বাধিয়ে সেরেছে। তার মহোৎসাহ মারণাস্ত্র তৈরিতে এবং মাদকের ব্যবসাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ পুঁজিবাদী আমেরিকা তখন তার সদ্য-উদ্ভাবিত আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। নিহত হয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ, পঙ্গু হয়েছে লাখ লাখ। আমেরিকার উদ্দেশ্যটা কী ছিল? মূল উদ্দেশ্য ভয় দেখানো। তা ভয় দেখাবে কাকে? পুঁজিবাদী জার্মানি ও জাপান তো তখন আর রণক্ষেত্রে নেই। ভয় দেখিয়েছে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়াকে। যে-রাশিয়া ততদিনে বুকেপিঠে ঠেলে হটিয়ে দিয়েছে পুঁজিবাদীদের শিরোমণি ফ্যাসিস্ট নাৎসিদেরকে, সেই রাশিয়াকে। আমেরিকা ভয় দেখিয়েছে তার আপাত-মিত্র কিন্তু সম্ভাব্য-শত্রম্ন অপরাপর পুঁজিবাদী শক্তিগুলোকেও। ক্ষতি যা হবার সবটাই হয়েছে নিরীহ মানুষের।
আরো একটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যই বাধত। মুনাফালিপ্সা বসে থাকতো না। পশুকে আমরা জন্তু বলি, মুনাফালোভী পুঁজিবাদীরা কিন্তু জন্তুরও অধম। জন্তুর ক্ষুধা তৃপ্তি মানে, জন্তু আহার শেষে ঘুমিয়ে পড়ে বা ঘুরে বেড়ায়। পুঁজিবাদীরা সর্বদাই ক্ষুধার্ত, সর্বক্ষণ তারা আহার খোঁজে, তৃপ্তি কাকে বলে জানে না। যত খায় তত তার ক্ষুধা বাড়ে। পাকস্থলী স্ফীত হয়। এই স্ফীতি নিয়ে তার কোনো লজ্জা নেই। তৃতীয় একটি বিশ্বযুদ্ধ যে লাগে নি, তার কারণ ভয়। পারমাণবিক অস্ত্র কারো একার হাতে নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতেও আছে; ভয়টা তাই পারস্পরিক। কিন্তু স্থানীয় যুদ্ধ ও ছায়াযুদ্ধ হরদম চলছে। উদ্দেশ্য দখলদারি; ভূমি, বাজার ও জ্বালানি দখল। উদ্দেশ্য অস্ত্র ও মাদক বিক্রি। সেইসঙ্গে ক্ষমতার বলয়কে সম্প্রসারিত করা।
পুঁজিবাদ বর্তমানে সভ্যতার শেষ স্তর। ধাপে ধাপে এগিয়েছে সে। কিন্তু সামনে এগোবার পথ তার জন্য এখন অবরুদ্ধ। এক সময়ে পরিবার ছিল না, রাষ্ট্রও ছিল না। সেই আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ছিল না। ছিল সাম্য। মানুষ গাছ থেকে ফল পেড়ে, ঝর্ণা থেকে মাছ ধরে খেত। তারপরে বুদ্ধি, হাত ও হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষ নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করেছে। উন্নতি নিয়ে এসেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বুদ্ধিতে ও পেশিতে কেউ কেউ ছিল অগ্রসর, তারা নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এসেছে দাস সমাজ, তারপরে সামন্ত সমাজ, সর্বশেষে পুঁজিবাদী সমাজ। এদের পরবর্তীটি পূর্ববর্তীটির তুলনায় অনেক উন্নত। পুঁজিবাদের উন্নতি ও প্রাচুর্য তো অতি আশ্চর্য। রূপকথার মতো।
কিন্তু এই যে উন্নতির ধারা, এর ভেতরে অব্যাহত রয়েছে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা। যারা মালিক তারা অন্যদেরকে খাটিয়েছে। উৎপাদন করেছে মেহনতিরা, ভোগ করেছে মালিকেরা। দাস সমাজে দাসমালিক, সামন্তসমাজে ভূমির মালিক, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির মালিক, কর্তৃত্ব ছিল এদেরই। উৎপাদনকারীরা বঞ্চিত হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজ এখন তার তৎপরতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। বঞ্চিত মানুষ – নিজেদেরকে যারা শতকরা ৯৯ জন বলে দাবি করে, তারা শতকরা একজনের শাসন মেনে নেবে না। কারণ মেনে নেওয়ার অর্থ অমানবিক জীবন যাপন করা। পুঁজিবাদ কতটা যে নৃশংস হতে পারে তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে মিয়ানমারে, মুনাফালোভীরা সেখানে গণহত্যা চালাচ্ছে। রহিঙ্গাদেরকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে বলে ঠিক করেছে। জ্বালিয়ে মারছে, পুড়িয়ে মারছে। এবং গণধর্ষণ করছে। এমন ঘটনা একাত্তরে বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি।
পুঁজিবাদীরা পৃথিবীকে আজ ধ্বংস করতে উদ্যত। নিজেদের সুবিধাদানকারী ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যত প্রকারের ছল, বল ও কৌশলের যত প্রকার প্রয়োগ সম্ভব সবই করেছে। ছলনা করেছে আধুনিকতার, বিজ্ঞাপন দিয়েছে উন্নতির। বলপ্রয়োগ করেছে আইনের, মজুদ রেখেছে বিভিন্ন বাহিনী। সবকিছুর পেছনেই উদ্দেশ্য মেহনতিদেরকে অধীনে রাখা, বিদ্রোহ করতে না-দেওয়া। বিদ্রোহীদেরকে আটকে রাখবে, বাড়াবাড়ি দেখলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, শারীরিকভাবেই। উল্টোদিকে সে আবার অধিকার দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়নের, ছুড়ে দিয়েছে কিছু কিছু উচ্ছিষ্ট। বলেছে গণতন্ত্র দিয়েছে। গণতন্ত্র মানে ভোট; বলেছে, এখন তো ভোট আছে সকলেরই, সকলেই এখন সকলের সমান। কিন্তু সমাজে মানুষ তো সমান নয়, তারা তো শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভক্ত। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র মানে যে টাকার থলির গণতন্ত্র, সে যে ক্ষমতায় বসায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো শেয়ানা ও বিপজ্জনক পাগলকে, সে যে পথ করে দেয় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের স্বঘোষিত প্রচারক নরেন্দ্র মোদিকে ক্ষমতায় বসবার, পুঁজিবাদ সেই সত্যটিকে সামনে আনে না। হিটলার ও মুসোলিনি উভয়েই কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাহলে?
সভ্যতার বস্তুগত অগ্রগতিতে বিশেষ প্রকার ভূমিকা ছিল বিভিন্ন উদ্ভাবনার। বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎ, ইলেক্ট্রনিক্স, এরা বৈপস্নবিক উদ্ভাবনা; কিন্তু সবাই পুঁজিবাদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং পীড়ন ও বঞ্চনার কারণ হয়েছে মেহনতি মানুষের। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথ্যজগতে অত্যাশ্চর্য বিপস্নব এনে দিয়েছে; কিন্তু এই বিপস্নব আবার তথ্যসাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধির, এমনকি তথ্যসন্ত্রাসেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদীরা তথ্য তৈরি করে, তথ্য বিকৃত করে, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে ফেলে। সকল কা-ই ঘটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করবার জন্য, এবং মেহনতিদেরকে দমন করবার অভিপ্রায়ে। তারা পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করে, চেষ্টা চালায় মানুষকে পণ্যমুখী ও ভোগবাদী করে তুলবার, মানুষ যাতে করে বাস্তবিক জগতের দুঃখ-দুর্দশা এবং বস্তুগত বৈষম্যের দুর্বিষহ সত্যটাকে ভুলে থাকতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ চালু করে এখন মানুষকে অসামাজিক করে তুলবার চেষ্টা চলছে। যোগাযোগ মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, ঘটছে ছায়ার সঙ্গে ছায়ার; এবং দ্রম্নত মন্তব্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের সমেত্মাষ ও আত্মপ্রচারের সুখ দুটোই পাওয়া যাচ্ছে, অতিসহজে। ওদিকে বাড়ছে বিচ্ছিন্নতা। তথাকথিত ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ভুলিয়ে দিচ্ছে রিয়াল ওয়ার্ল্ডকে। বড় করবার নাম করে পৃথিবীটাকে ছোট করে দেবার কাজ চলছে, মহোৎসাহে। এমনকি নিজের ঘরও নয়, নিজের হাতের ফেসবুক এবং মোবাইল ফোনকেই মনে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ জগৎ। বৃহৎকে আটক করে ফেলা হচ্ছে ক্ষুদ্রের ভেতর। জগৎকে ভুলে থাকবার এ এক আশ্চর্য নেশা, অদ্ভুত মোহ। হাসছে অন্তর্যামী; তার ব্যবসা জমছে ভালো, ভাবছে সে, তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা আসছে কমে।
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমকে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ দক্ষতায়, কিন্তু শ্রমিককে ঘৃণা করে সর্বাধিক পরিমাণে। ভয়ও করে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে যন্ত্রে পরিণত করতে চায়। শুকিয়ে আধমরা করে রাখে; মারে না, কারণ মারলে কাজে লাগবে না। অধুনা সে চাইছে শ্রমিককে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে। রোবটকে সজীব করে তুলছে, তাকে বুদ্ধিবৃত্তি সরবরাহ করছে। রোবটকে দিয়ে অনেক সুবিধা। সে কাজ করবে নীরবে, ট্রেড ইউনিয়ন করবে না, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে যাবে না; মজুরি সে চাইবেই না। বিদ্রোহের আশঙ্কা একেবারেই নেই। সকল বিবেচনাতেই রোবট হচ্ছে আদর্শ শ্রমিক। এই শ্রমিকের ব্যাপারে নব্য-পুঁজিবাদী চীনকে দেখা যাচ্ছে সর্বাধিক আগ্রহী। চীন চাইছে আমেরিকাকে জব্দ করবে। তার দেশে শ্রমিকের অভাব নেই; কিন্তু রোবট পেলে আরো সুবিধা। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চীন তাই কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বিধানেও ভয়ংকরভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন দেখা দিলে পুঁজিবাদীরা বরং যন্ত্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, শ্রমজীবীকে হটিয়ে দিয়ে।
সবকিছু মিলিয়ে মানুষের সভ্যতা এখন সত্যি সত্যি একটি ক্রান্তি-মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে। যেভাবে চলছে সেভাবে চলবে না, চলতে পারবে না।
প্রশ্নটা হলো পরিবর্তনটা কোন দিকে ঘটবে? বিকল্পটা কী? পুঁজিবাদের বিকল্প তো পুঁজিবাদ হতে পরে না। দাসব্যবস্থা, সামন্তব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতর শত শত বৎসর ধরে বিকশিত ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থাটি আজ তার চরম পরিণতিতে এসে পৌঁছে গেছে। তার পক্ষে এখন আর দেবার কিছুই নেই, ধ্বংস ছাড়া। এখন নতুন ব্যবস্থা আনতে হবে। সে-ব্যবস্থাটা ব্যক্তিমালিকানার হতে পারে না। দুই কারণে। প্রথম কারণটি বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয়টি মানবিক। মানুষের ইতিহাস এগোবে, যাবে সে সামনের দিকে, সেই অগ্রযাত্রায় ব্যক্তিমালিকানা হচ্ছে প্রধান প্রতিবন্ধক। এই বন্ধন ছিন্ন না করলে ইতিহাস সামনের দিকে যেতে পারবে না। আর ইতিহাসের পক্ষে তো পেছনদিকে যাবার কোনো উপায়ই নেই, সে তো ফেরত যাবে না সামন্তসমাজে, কিংবা দাসসমাজে; থাকতে পারবে না যেখানে সে আটকা পড়েছে সেখানেও; অচল হলে তো ভেঙেই পড়বে, আপনা থেকেই। চলতে হলে তাকে যেতে হবে সামনের দিকে। সর্বোপরি মুনাফার প্রশ্নে উন্মত্ত পুঁজিবাদ আজ যে ধরনের উন্নতি ঘটাচ্ছে তা এই গ্রহে মানুষের অসিত্মত্বের জন্য জ্বলন্ত হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী উন্নতি আরো এগোলে মহাবিপর্যয় দেখা দেবে। উন্নতির এই ধারা থেকে বিশ্ব আজ অব্যাহতি চায়।
দ্বিতীয় কারণটি মানুষের বিক্ষোভ। মালিকের সংখ্যা অতি অল্প। বঞ্চিতের সংখ্যা অনেক। এই অনেক মানুষ বহুযুগ ধরে অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ করেছে। সাময়িকভাবে জয়ীও হয়েছে, কিন্তু সে-জয় টেকে নি; নানা কায়দাকৌশল ও আপোসরফার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিমালিকানার ব্যবস্থাটাই টিকে গিয়েছে। খুব বড় একটা ঘটনা ছিল ফরাসি বিপস্নব। কিন্তু মেহনতি মানুষকে সে মুক্তি দিতে পারে নি; সে বরং সুবিধা করে দিয়েছে ধনীদেরকেই। রুশ বিপস্নব অবশ্য পেরেছিল। এই বিপস্নবের পরে ব্যক্তিমালিকানাকে হটিয়ে দিয়ে সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে নতুন ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক এই আদর্শ রাশিয়ার বাইরে বিশ্বের অন্যদেশেও চলে গিয়েছে; এবং বেশ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কিন্তু বাইরে থেকে পুঁজিবাদীদের আক্রমণ ও ভেতরে আমলাতান্ত্রিকতার তৎপরতা, এই দুয়ের চাপে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নতুন ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে গেছে। তাই বলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যে পতন ঘটেছে তা নয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপযোগিতা বরং আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে, বৈশ্বিকভাবে বিশ্ব জুড়ে মানুষ এখন পুঁজিবাদের বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে। চূড়ান্ত বিচারে পুঁজিবাদের বিপক্ষে দাঁড়ানোর অর্থ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানো। পুঁজিবাদের পতন এখন তাই সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিশ্বজুড়ে আভাস পাওয়া যাচ্ছে গৃহযুদ্ধের, এবং সেটা হয়তো খোদ আমেরিকাতেই চরম আকার ধারণ করবে। আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে একদা যে-আমেরিকা সমাজতন্ত্রকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেই সমাজতন্ত্র মনে হচ্ছে নির্ভয়ে চলে আসবে পুঁজিবাদের ওই রাজধানীতেই। পুঁজিবাদ এখন তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। কামড়াতে চায়।
দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখলে এটা অস্পষ্ট থাকবে না যে, পুঁজি এবং শ্রমের দ্বন্দ্বটাই এখন বিশ্বজুড়ে প্রধান দ্বন্দ্ব। এক সময় ছিল যখন কারণ ও কার্যের সম্পর্কটাকেই চালিকাশক্তি মনে করা হতো। কার্যের পেছনে কারণ থাকে, কারণই কার্যের জন্ম দেয়, এটা জানা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশেষভাবে জানা হয়ে গেছে আমাদের যে, স্থায়ী সত্যটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব, কার্যকারণ মিথ্যা নয়, কিন্তু দ্বন্দ্বই প্রধান, দ্বন্দ্ব চলছে কার্যকারণের ভেতরও। অসংখ্য দ্বন্দ্ব রয়েছে ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে; দ্বন্দ্ব রয়েছে ব্যক্তির নিজের ভেতরেও। দ্বন্দ্বের কোনো অভাব নেই। সকল দ্বন্দ্বই আসলে ক্ষমতার। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবতায় একেক সময় একেকটি দ্বন্দ্ব অন্যসব দ্বন্দ্বকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে, এবং অন্য দ্বন্দ্বকেও প্রভাবিত করে। আজকের পৃথিবীতে প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের, অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে সামাজিক মালিকানার। এ লড়াইয়ে সামাজিক মালিকানাকে অবশ্যই জিততে হবে, নইলে আমাদের প্রিয় এই গ্রহের অসিত্মত্বই বিপন্ন হবে, যে-সতর্কবাণী বিজ্ঞানীরা দেওয়া শুরু করেছেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।
উদারনীতিকেরা আছেন। তাঁরা ভদ্রলোক, সংস্কার অবশ্যই চান, কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন চান না। তাঁরা আপোসপন্থী, এবং মধ্যস্থতাকারী। মধ্যস্থতা করে ব্যক্তিমালিকানাকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু বিশ্ব আজ আর মধ্যপন্থার জায়গাতে নেই, চরমপন্থী হয়ে গেছে। ভাগ হয়ে গেছে সে প্রতিক্রিয়াশীলে ও প্রগতিশীলে। রক্ষণশীলরাও প্রতিক্রিয়াশীলদের দলে পড়ে। সমন্বয় ও সংরক্ষণ মোটেই এক জিনিস নয়, দুয়ের ভেতর বিস্তর পার্থক্য। উদারনীতিকেরা সমন্বয়ের কথা বলেন, কিন্তু আসলে যা চান সেটা হলো সংরক্ষণ।
উদারনীতিতে তাই কুলাবে না। উদারনীতিরও নিজস্ব একটা দর্শন আছে বৈকি, কিন্তু দার্শনিকেরা উদারনীতিক হতে পছন্দ করেন না, যদিও দার্শনিকদের কাছ থেকেই উদারনীতির ধারণা এসেছে, উদারনীতির প্রচার ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। উদারনীতির প্রবক্তারা তাঁদের সময়ে প্রগতিশীলই ছিলেন, তখন তাঁদের ভূমিকা ছিল রক্ষণশীলতার বিপক্ষে; কিন্তু চরমপন্থী বর্তমান বিশ্বে তাঁদের পক্ষে সে-ভূমিকা পালন করাটা অসম্ভব।
উদারনীতিকদের তৎপরতায় ক্ষুদ্র দ্বন্দ্বগুলো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ওদিকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানেই চলছে নানা ধরনের সহিংস যুদ্ধ। তবে আসল যুদ্ধটা সমাজবদলেরই। সেটাকে আড়াল করার জন্যই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বড় হয়ে উঠতে। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করে তোলাটা, বৃহৎকে আড়ালে সরিয়ে রাখার চেষ্টারই অংশ বটে। দূষণ ঘটেছে উৎসে, শাখা-প্রশাখার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভটা কী? লাভ হচ্ছে না; একমাত্র লাভ আত্মপ্রসাদের।
কিন্তু মানুষ তো পরাজয় মানে না, মানবে না। পৃথিবীকে সে ধ্বংস হতে দেবে না। সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে সে অবারিত করবে। ওই সৃষ্টিশীলতা এখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ব্যক্তিমালিকানার যাঁতাকলে। ফুঁসছে, বের হয়ে যেতে পারছে না। মুক্ত হলে পৃথিবীকে সে কেবল রক্ষাই করবে না, বদলেও দেবে। প্রাচুর্য আসবে। সংকট থাকবে না বিতরণে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অভাব। সম্পদের অপচয় ঘটবে না মারণাস্ত্র তৈরিতে। মাদকের ব্যবহার অতীত ইতিহাসে পরিণত হবে। কাজ থাকবে সকলেরই; থাকবে অবসর, এবং প্রচুর আনন্দ। শিল্পকলায় ও নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে পৃথিবী।
পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের এই ক্ষেত্রটিতে দার্শনিকদের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য। কারণ, আমরা জানি, অন্যরা যেখানে ক্ষুদ্র ও বিশেষকে দেখেন, দার্শনিকেরা সেখানে দেখেন সমগ্রকে ও নির্বিশেষ সাধারণকে; সেইসঙ্গে দেখেন স্বাতন্ত্র্যকেও। সত্মূপ দেখেন না, দেখেন সজীব সম্মিলন। তাঁরা কেবল দেখেন না, বুঝতেও চান। বিদ্যমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট নন বলেই তাঁরা বুঝতে চান কী ঘটছে এবং কেন ঘটছে। তাঁদের বিবেচনা কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র নয়, বিবেচনা সমগ্র বিশ্ব।
দার্শনিকতার অর্থ উদাসীনতা বা অন্যমনস্কতা নয়, আত্মসমর্পণ তো অবশ্যই নয়, দার্শনিকতার অর্থ পরিবর্তনের স্বার্থে, যুক্তির সাহায্যে জীবন ও জগৎকে বোঝার চেষ্টা। দার্শনিকরা তর্ক করেন না, বিতর্ক করেন, তবে তাঁদের মূল আগ্রহ আলোচনাতে। দার্শনিক অবস্থানে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে, থাকতেই হয়, কিন্তু নিরাসক্তি যে থাকে তা নয়। তাঁরা নিজ নিজ মতের পক্ষে দাঁড়ান। শক্তভাবেই দাঁড়ান। সে মত অনেক সময়েই প্রচলিত চিমত্মা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলে যায়। যে জন্য সময় সময় তাঁদেরকে কঠিন বিপদে পড়তে হয়েছে। বিজ্ঞানীরাও যে সর্বদা হাততালি পান তা নয়, তাঁরাও সংকটের মুখোমুখি হন। কিন্তু তাঁরা আপোস করে ফেলতে পারেন, যেমন গ্যালিলিও করতে পেরেছিলেন; কিন্তু দার্শনিকেরা সেটা করতে পারেন না, তাঁরা অনমনীয় থাকেন, এবং থাকতে গিয়ে প্রাণ পর্যন্ত দেন। যেমন এথেন্সে সক্রেটিস দিয়েছেন, পরে ইংল্যান্ডে দিয়েছেন টমাস মোর। ইংল্যান্ডেরই আরেক দার্শনিক উইক্লিফ, তাঁরও বিপদ ঘটেছিল। উইক্লিফ যিশু খ্রিষ্টের আদর্শের অনুসরণে ধর্মযাজকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকার বিরুদ্ধে কথা বলতেন, এবং এমনকি এমনও মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে পাপের ফল; তাঁর সময়ের যে কৃষকবিদ্রোহ হয়েছিল সেটিকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন, এবং বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ করে ধর্মযাজকদের একচেটিয়া ব্যবসাতে হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর জন্য তাই একের পর এক বিপদ এসেছে। ধর্মযাজকরা তাঁর বিচার করতে চেয়েছে। উইক্লিফ ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপক, গির্জার আক্রমণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে; শেষ পর্যন্ত পারত কি না কে জানে, কেননা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও উচ্চকক্ষ তাঁর বিচার করতে চেয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিলেন সময়মতো মারা গিয়ে। কিন্তু তাঁর মরদেহের হাড়গুলো রক্ষা পায় নি, ক্যাথলিক গির্জার কর্তারা কবর খুঁড়ে সেগুলো বের করে পুড়িয়ে নিজেদের গায়ের ঝাল মিটিয়েছে। ইটালির দার্শনিক ব্রম্ননোর ভাগ্য তুলনায় কম প্রসন্ন ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর উইক্লিফের চিমত্মাধারাকে যদি বলা যায় কমিউনিজমমুখী, তাহলে ষোড়শ শতাব্দীর ইটালির দার্শনিক ব্রম্ননোকে বলতে হবে বস্তুবাদী। তিনি মনে করতেন এবং বলতেনও যে পৃথিবীটা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় বস্তুর সমাহার। তাঁর চিমত্মার মধ্যে এও ছিল যে, মানুষের ধ্যানধারণা বস্তুগত অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর ধারণা ছিল, জ্ঞানের কোনো সীমা নেই, এবং অনপেক্ষ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ব্রম্ননো অধ্যয়ন করতেন, ঘুরে ঘুরে প্রচারও করতেন। ঘোরাঘুরির ভেতরে থাকলেই ভালো করতেন, ভুল করে চলে এসেছিলেন ভেনিসে; সেখানে গির্জার কর্তারা তাঁকে আটক করে এবং আগুনে পুড়িয়ে মারে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দার্শনিকদের যখন প্রাণ দিতে হয়েছে তখন সেটা ঘটেছে তাঁদের আবিষ্কারের জন্য নয়, আবিষ্কারের রাজনৈতিক তাৎপর্যের কারণে। তাঁদের আবিষ্কার বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলেছিল। গ্যালিলিও যে বিপদে পড়েছিলেন সেটাও ওই রাজনৈতিক কারণেই। তাঁর জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাইবেলে প্রদত্ত ও যাজকদের প্রচারিত তথ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল। আবিষ্কারটা যদি বিজ্ঞানীদের জগতে আটক থাকতো তাহলে ধর্মব্যবসায়ীরা তাঁকে উপেক্ষা করতো, কিন্তু তিনি তাঁর আবিষ্কারকে উন্মোচিত করেছিলেন ইটালীয় ভাষায়, ফলে ওই জ্ঞান সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে যাবে এমন বাস্তবিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সূর্যকেন্দ্রিকতা-বিষয়ক তত্ত্ব তাঁর আগে কোপারনিকাস আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীরা সে-ঘটনাকে গুরুত্ব দেয় নি, কারণ তাঁর তত্ত্বটা লেখা হয়েছিল পোল্যান্ডের সাধারণ পাঠকদের জন্য অগম্য ল্যাটিন ভাষায়।
তাহলে উপসংহারে আসা যাক। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন দর্শনপাঠের খুব একটা দাম ছিল না, কাজে লাগবে না এই বিবেচনাতে। কাজ
মানে বিদ্যমান ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে আয়-উপার্জন করা। দর্শনের পাঠ এই সুযোগ-বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এমন ভরসা ছিল না। দর্শনের দাম এখন মনে হয় আরো পড়ে গেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অবস্থান সুবিধাজনক নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সে প্রায় অনুপস্থিত। তুলনায় বরং এক সময়ে দর্শনেরই অংশ ছিল যে মনোবিজ্ঞান তার দাম বরং বেড়েছে। তা দাম যাই হোক দর্শনের মূল্য থাকবেই। দাম পড়াটাই বরং মূল্যবৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। বস্তুতান্ত্রিকতার রোগ বাড়লে দার্শনিক চিকিৎসার মূল্যবৃদ্ধি তো ঘটবারই কথা। মূল্যবৃদ্ধির এই আবশ্যকতার কথাটা ইউরোপের মধ্যযুগের এক দার্শনিক বোইথিউস (৪৭৫-৫২৫) আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন তাঁর একটি গ্রন্থে, নাম যার দর্শনের সান্তবনা। ওই সান্তবনায় তাঁর প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়ে গিয়েছিল। সেটা ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণে। রাজা অভিযোগ এনেছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহের। প্রাণদ-াদেশ কার্যকর হবার আগ পর্যন্ত বোইথিউস সময় পেয়েছিলেন মাত্র একবছর। সময়টা তিনি কান্নাকাটি, প্রার্থনা, বিষণ্ণতা ইত্যাদির মধ্যে কাটান নি, কাটিয়েছেন দর্শনের সান্তবনা নামের ওই গ্রন্থটি লিখে। বই তিনি আগেও লিখেছেন; গণিত ও সংগীতের ওপর তাঁর জরুরি লেখা আছে, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন ধ্রম্নপদী গ্রিক দর্শন-সাহিত্যের। কিন্তু পরিষ্কারভাবে দর্শনের ওপর মৌলিক গ্রন্থটি লেখেন ফাঁসির হুকুম ঘাড়ে নিয়ে।
দর্শনের সান্তবনা গ্রন্থটি পেস্নটোর সংলাপের আদলে লিখিত। দর্শন একজন মহিলা। লেখক কথা বলছেন দর্শনরূপী এই মহিলার সঙ্গে। দর্শন তাঁকে সান্তবনা দিচ্ছে। ধর্মের কথা বলে নয়, পরকালে স্বর্গসুখ প্রতীক্ষায় রয়েছে, এমন প্রতিশ্রম্নতি দিয়েও নয়। সান্তবনা দিচ্ছে এ-কথা বলে যে, জগৎ পরিবর্তনশীল, চক্রাকারে আবর্তিত, ভাগ্যের উত্থান-পতন আছে, বিষয়সম্পত্তি মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী; স্থায়ী হচ্ছে সদ্গুণ। বোইথিউস নাসিত্মক ছিলেন না, কিন্তু তিনি পাপ-পুণ্যের কথা ভাবেন নি, ভেবেছেন শুভ-অশুভের কথা, ভেবেছেন প্রজ্ঞা-চর্চার কথা। তাঁর জগৎটিতে বন্ধুত্ব হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক। কুসংস্কার ও ভোগবাদিতা দুটোই পরিত্যাজ্য। মূল কথাটা হলো, মৃত্যু তো অনিবার্যই, আগে আর পরে; তাই জীবনকে কাজে লাগানো চাই সদ্গুণের চর্চায়, জ্ঞানের অন্বেষণে এবং মানবিক সম্পর্ক সমৃদ্ধকরণে। সেটা করলে অস্থিরতা থাকবে না, মৃত্যুকেও ভয়ংকর বলে মনে হবে না। সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে এই বোধ থেকে পাওয়া যাবে প্রশান্তি। এসব বক্তব্য তিনি রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য। লোকে তা পড়েছে, প্রভাবিত হয়েছে। ধর্মশাসিত ভুবনে বসবাস করে দার্শনিক চিমত্মার জন্য তিনি শক্ত একটা ভিত্তিভূমি করে রেখে গেছেন; দর্শনকে আলাদা করেছেন ধর্মতত্ত্ব থেকে। এমন বিদ্রোহ দার্শনিকরা করে থাকেন। করাটা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। শান্তভাবেই করেন। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রভাবশালী এই দার্শনিক বিদ্রোহ।
মুনাফালিপ্সু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দর্শনের দাম কমাতে পারে ঠিকই, কিন্তু মূল্য কমাতে পারবে না কিছুতেই। দর্শন কেবল যে সান্তবনা দেবে তা নয়, দেবে পথের দিশাও। পথের দিশাটা আজ খুবই প্রয়োজন, কেননা বিভ্রান্তি সৃষ্টির আয়োজনে জগৎ এখন মুখর ও ভরপুর। জগৎ খুবই অসুস্থ, তার দার্শনিক চিকিৎসা অত্যাবশ্যক। r

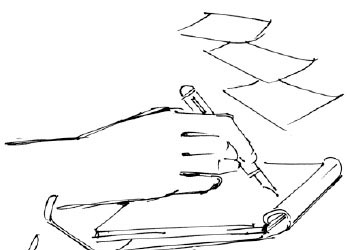
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.