আমাদের নয় ভাইবোনের মধ্যে রবিউল ভাই ছিলেন সবার বড়। আমরা সবাই তাঁকে ‘মিয়াভাই’ বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন আমাদের প্রাণভোমরা। তাঁর মধ্যেই ছিল যেন আমাদের সকলের জীবনীশক্তি। আজ তিনি নেই, তাই আমরা যেন এখন জীবন্মৃত। মনে হয় জীবনের সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেছে, যেন সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁর প্রতি ছিল আমাদের অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আমাদের সকল ভাইবোনের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। মানসিকভাবে তাঁর ওপর আমরা বরাবরই নির্ভরশীল ছিলাম। কারণ খুঁজতে গিয়ে এটাই মনে হয়েছে যে, এতো ভাইবোন ও বিধবা মাকে ফেলে বাবার অকালমৃত্যুর পর তাঁর ভূমিকা ছিল পিতার মতো। তাঁরই ছায়াতলে আমাদের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা ও বড় হওয়া। তাই ছোটবেলা থেকেই তাঁর ওপর নির্ভরশীলতা শুরু হলো আর শেষ হলো তাঁর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন আমাদের মাথার ওপর একটা ছাদের মতো। তাঁর মৃত্যুর পর মনে হলো হঠাৎ করে ছাদটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে আমাদের হৃদয়টাও যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল। আমার কাছে বড়ভাই রবিউল হুসাইনের মৃত্যুপরবর্তী অনুভূতি অনেকটা এরকম। সত্যি কথা বলতে কী, এখন পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আসতে পারিনি, যদিও এর মধ্যে প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সর্বদা এক অব্যক্ত গভীর বেদনা আর অব্যাহত কান্নামিশ্রিত যুগলবন্দির কবলে আমাদের পুরো পরিবার মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত প্রায়। সবাই দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাঁকে শেষ রক্ষা করতে পারিনি। প্রায়ই নিজেদের দোষারোপ করি এই ভেবে যে, তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না।
বড়ভাইয়ের লেখা এক কবিতার শিরোনাম ছিল – ‘ভুলেও ভুল ক’রে ভোলা কি যায় তারে’। সত্যিই তাঁকে কখনোই ভোলার নয়। এজন্য ভাইবোনদের নিয়ে পারিবারিক আলোচনার মধ্যে বারেবারে তিনি এসে পড়েন। মনে হয় তিনি যেন আগের মতোই আমাদের মাঝেই আছেন, কথা বলছেন, গল্প করছেন, হাসি-তামাশা করছেন, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন – সবই যেন বরাবরের মতন। উপস্থিত না থেকেও তিনি যেন অতিমাত্রায় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে।
তাঁর শৈশবস্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে মনে পড়ে আমাদের কুষ্টিয়া মফস্বল শহরের থানাপাড়ার দোচালা টিনের কাঁচা বাড়িঘরের কথা। ১৯৫২ সালের দিকে বাবার কেনা সেই বাড়ি থেকেই যাত্রা শুরু। যদিও বাবার চাকরির সুবাদে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, গাংনী, দামুড়হুদা প্রভৃতি জায়গায় তাঁকে থাকতে হয়েছিল। তাঁর দুরন্ত শৈশবের স্মৃতি আমার মনে পড়ে। কুষ্টিয়া শহরের গড়াই নদীর পাশেই ছিল আমাদের বাড়ি। বাড়ি থেকে হেঁটে নদীতে যেতে মাত্র ১০ মিনিট সময় লাগতো। গড়াই হচ্ছে পদ্মার শাখা নদী, যা কুষ্টিয়া শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত ও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। গড়াই নদী ছিল যেন আমার বড়ভাইয়ের প্রাণ। গোসল করা, সাঁতার কাটা, ডাইভিং দেওয়া, নদীর পাড়ে নোঙর দেওয়া সারি সারি বিভিন্ন আকারের নৌকার মাচার ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া – আরো কত কী। নদীতে বালুচর জেগে উঠলে তো কথাই নেই। সারাটা দিন সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকাল পর্যন্ত নদী ও বালুচরে খেলাধুলা করে সময় কাটাতেন। রৌদ্র ও পানিতে থাকার কারণে সারাশরীর পুড়ে কালো করে দেরিতে বাড়িতে ফিরে মায়ের বকুনি ও মার খাওয়া ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।
বড়ভাইয়ের দুরন্ত কিশোরবেলার আর একটা ক্ষেত্র ছিল খেলার মাঠ। ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হকি, দৌড়ানো, সাইক্লিং ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। ক্রিকেট বা ভলিবল খেলতে তাঁকে দেখিনি কখনো। একবার সাইকেল রেসিংয়ে প্রথম হয়ে একটা ‘হারিকেন বাতি’ প্রাইজ পেয়েছিলেন। হকি খেলতে গিয়ে বলের আঘাতে সামনের পাটির একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। এর জন্য বাবার বকুনি ও বেদম মার খেতে হয়েছিল। পরের দিন দাঁতটা বাঁধাই করে ফেলেছিলেন।
এরকম আরো অনেক ঘটনা মনে পড়ে তাঁর দুরন্ত কৈশোরের। ক্রমে ক্রমে আরো বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁকাআঁকি, গল্প-কবিতা লেখার মধ্যে ডুব দিলেন। কুষ্টিয়া মুসলিম হাইস্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনে ভাইয়ের একটা গল্প ছাপা হয়েছিল। গল্পের নাম ছিল ‘সন্তানহারা’। শ্রেষ্ঠ গল্পের প্রাইজ জুটলো ভাইয়ের কপালে। গল্পটা পড়ে আমার মা কেঁদে ফেলেছিলেন। এটা একটা বিয়োগান্তক গল্প ছিল। কুষ্টিয়া কলেজে পড়াকালীন সময়ে একটা স্টাডি ট্যুরের প্রোগ্রাম হয়েছিল। স্থানটা সুন্দরবন নাকি দর্শনা সুগার মিল, ঠিক মনে নেই। ট্যুর প্রোগ্রাম শেষে ট্যুরের ওপর একটি ভ্রমণকাহিনি লিখে জমা দেওয়ার আহ্বান জানালো কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেবারও বড়ভাই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রাইজ পেলেন একটা বই। বইটির নাম ছিল ‘মহাকাশে অভিযান’। বইটি অনেকদিন বাসায় রাখা ছিল। এখন আছে কি না জানি না। এই সময় থেকেই তিনি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা পাঠাতে থাকেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর কোনো গল্প-কবিতা সংবাদপত্র ছাপাতো না। তাই সে আমার বড়বোন ‘লাইলী হোসেনে’র নামে নানা গল্প-কবিতা ও তাঁর আঁকানো বিভিন্ন ছবি পাঠাতে শুরু করলেন। এবার কাজ হলো অর্থাৎ সংবাদপত্র লাইলী হোসেনের নামে গল্প, কবিতা ও ছবি মাঝে মাঝে ছাপাতে লাগলো। এরপর থেকে তিনি আমার বোনের নামে সাপ্তাহিক বেগম, ললনা, দৈনিক ইত্তেফাকের ‘মহিলা পাতায়’ নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। চিত্রালী ও সচিত্র সন্ধানীতেও মাঝে মধ্যে দু-একটা কবিতা-গল্প লিখে পাঠাতেন এবং তা কালেভদ্রে ছাপা হতো। কখনো কখনো ঈদসংখ্যাতেও ছাপা হতো।
কুষ্টিয়া শহরের রেনউইক ময়দানে প্রতিবছর ডিসেম্বরে মাসব্যাপী শিল্পপ্রদর্শনী হতো। সেখানে ভাইয়েরা কয়েক বন্ধু মিলে স্টল ভাড়া করে তাঁদের বিভিন্ন শিল্পীবন্ধুর আঁকা পেইন্টিং প্রদর্শন ও বিক্রি করতেন। আমি তখন বেশ ছোট, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তাম। এই প্রদর্শনীতে নানা ধরনের কাপড়-চোপড়, খেলনা, সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত হয় এমন বিভিন্ন প্রকার হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাটি, ঘড়া-কলস ও নানা রকমের বাসনকোসন পাওয়া যেত।
এছাড়া ছিল মজাদার খাদ্যদ্রব্যের সমাহার। হোটেল-রেস্তোরাঁয় ফুচকা-চটপটি, চা-শিঙাড়া, পরোটা, লুচি, ভাজি ইত্যাদিও পাওয়া যেত। আরো পাওয়া যেত কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি। মেলার আরেক পাশে প্রদর্শিত হতো সার্কাস, যাত্রা, ম্যাজিক, বিভিন্ন প্রকার লটারি, হাউজি ইত্যাদি।
মোহিনী টেক্সটাইল মিলস ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বৃহৎ কাপড়ের কল ছিল। তাদেরও একটা বড় স্টল থাকতো। আরো থাকতো যজ্ঞেশ্বর মিল কর্তৃক তৈরি হেভি মেটালের আখ মাড়াইয়ের স্টলসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির স্টল। জি.কে. (গঙ্গা কপোতাক্ষের) প্রজেক্টের বিরাট স্টল ছিল। বড়ভাই প্রায় প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে যেতেন আর বিভিন্ন স্টলের প্রদর্শিত বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। তবে যাত্রা, সার্কাস, হাউজি, ম্যাজিক ইত্যাদির প্রতি তাঁর খুব একটা আকর্ষণ ছিল না ।
স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে অনেক কথায় মনে পড়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মিয়াভাই তথা রবিভাই সম্পর্কে। কুষ্টিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ঢাকাতে পাড়ি জমান। ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হন। সেখান থেকে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে ঢাকা হলো তাঁর নতুন ঠিকানা।
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে পড়াকালে ক্লাসের পর তিনি এক কনসাল্টিং ফার্মে ড্রাফটসম্যান হিসেবে পার্টটাইম কাজ করতেন। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হতো তাঁকে। বাড়ি থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা না নিয়ে নিজে আয় করে তাঁর এই পড়াশোনার খরচ চালাতেন। আবার এই পার্টটাইম কাজের জন্য যখনই বেতন পেতেন তখন মাকে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতেন।
ভাইয়ের মুখ থেকে একবার শুনেছিলাম একসময় এমন দিনও গেছে সকালে নাস্তা বা দুপুরে ভাত খাওয়ার পয়সা ছিল না তাঁর। এই অবস্থায় ক্লাসে যাওয়ার আগে পেট ভরে দুই-তিন গ্লাস পানি ঢক্ঢক্ করে পান করতেন। তারপর সারাদিন না খেয়েই ক্লাস করতেন। এই কথাগুলো পরবর্তী সময়ে যখন তাঁর মুখ থেকে শুনতাম, লক্ষ করতাম তাঁর দুচোখ পানিতে চিকচিক করছে।
সত্যি আমাদের পরিবার বা মা-ভাইবোনদের জন্য তাঁর বিশাল অবদান মোটেই ভোলার নয়। আমার মেজোভাই (চাঁদ ভাই) সে-ও তখন ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। সে বরাবরই মেধাবী ছাত্র ছিল। সে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট উভয় পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল।
বড় দুই ভাই ঢাকায় একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন আর বাকি আমরা তখন কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করছি। মেজোভাই ছাত্র হিসেবে মেধাবী হওয়ার সুবাদে স্টাইপেন্ড পেতেন এবং সেই সঙ্গে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এক কর্নেলের ছেলেকে পড়াতেন অর্থাৎ প্রাইভেট টিউশনি করতেন। সেখান থেকে যে-বেতন পেতেন তার থেকেও প্রতিমাসে মাকে কিছু কিছু টাকা পাঠাতেন। এতে বিধবা মায়ের পক্ষে বাকি সাত-আট ভাইবোনসহ সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় আমার বাবার অকাল মৃত্যু ঘটলো। মা দিশেহারা হয়ে গেলেন। এতো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। কবে আমার ছেলে দুটো পাশ করে বেরোবে আর কবেইবা তাঁর ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে তুলবে? – তিনি সারাক্ষণ এই চিন্তা করতেন। এর মধ্যে আমার ডাক্তার চাচা এগিয়ে এলেন। তিনি বড়ভাইদের পাশ করার আগ পর্যন্ত আমাদের ভরণপোষণের জন্য প্রতিমাসে অর্থসাহায্য করে গেছেন। তিনি আমার বাবাকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সময়োচিত সাহায্য না পেলে আরো বিপদ হতো। এজন্য আমরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।
অবশেষে সবই হলো ধীরে ধীরে। আমরা সব ভাইবোন পড়াশোনা শেষ করে যার যার কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছি। একে একে সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি।
এটা না বললেই নয় যে, আমাদের বড় দুই ভাইয়ের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় এটা সম্ভবপর হয়েছিল। আমাদের পারিবারিক বন্ধনও অটুট ছিল শুধু তাঁদের জন্যেই। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ছিল শুদ্ধ ও চির অম্লান। দূরে বা কাছে যেখানেই তাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন।
ভাবি মারা গেলে মিয়াভাই আরেকবার ধাক্কা খেলেন। একমাত্র পুত্র রবীনই তাঁর সবকিছু, তাঁর পৃথিবী, তাঁর দুই নয়নের মণি। কিন্তু ভাবির মৃত্যুর পর তিনি অফিসের কাজে, বাইরের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ও অন্যান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর জড়িয়ে পড়লেন। ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধি।
শেষের দিকে অধিক ব্যস্ততা একদিকে তাঁকে যেমন উজ্জীবিত করে রেখেছিল, অন্যদিকে তাঁর শরীর, মন ও পুত্রের দিকে কিছুটা হলেও অবহেলার একটা ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। মহৎ ও সৃষ্টিশীল মানুষেরা হয়তোবা এমনটিই হয়ে থাকেন। তা না হলে পৃথিবীতে সৃষ্টির এতো ছড়াছড়ি হতো না।
রবি অবশেষে পশ্চিম গগনে অস্তগামী হলো। তারই পড়ন্তবেলার রৌদ্রের রাঙা শেষ আলোকছটা আমাদের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অতঃপর সস্নেহে বুলিয়ে মাখিয়ে দিয়ে তিনি যেন টুপ করে ডুব দিয়ে চলে গেলেন আর বলে গেলেন, ‘আমি গেলাম রে … ভালো থাকিস তোরা … শুধু আমার রবীনকে দেখেশুনে রাখিস।’ যাবার সময় তাঁর এই বার্তাটি সমগ্র আকাশে-বাতাসে, মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে অনুরণিত হতে লাগলো ও একসময় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।
বড়ভাই রচিত পূর্বোল্লিখিত কবিতাটা দিয়েই লেখাটির পরিসমাপ্তি টানলাম।
ভুলেও ভুল ক’রে ভোলা কি যায় তারে
পেয়েও পায়নি যারে কী হবে মনে ক’রে
ভুলেও ভুল ক’রে ভোলা কি যায় তারে।
কোথাও যায়নি সে তবে কি আশেপাশে
ঘাসের সঙ্গী হ’য়ে আছে সে সুখে শুয়ে।
যে-জানে সে-ই জানে মনেরও গহন
কোণে
কী কথা কওয়া হয় গোপনে অতিশয়।
দূরের সাক্ষী যারা নিকটে আসে তারা
নিকট দূরে যায় দূরকে কাছে পাই।
আকাশের মেঘপটে ফুল এক নীল
ফোটে
যে-ফুল ফোটে দূরে তাকে ছুঁই কী
ক’রে।
পেয়েও পাইনি যারে কি হবে মনে ক’রে
ভুলেও ভুল ক’রে ভোলা কি যায় তারে।
* তাইমুর হোসেন – রবিউল হুসাইনের সেজোভাই।
[কিছু কথা : মাস দুয়েক ধরে বাবাকে অনেক ব্যস্ততায় সময় কাটাতে দেখতাম। বড় চাচু কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনকে নিয়ে লিখতে আমার বাবাকে অনুরোধ করেছিলেন কালি ও কলম সম্পাদক কবি আবুল হাসনাত। লেখালেখির অভ্যাস আমার বাবা বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্ক্রিপ্টভর্তি কাটাছেঁড়া করতে করতে রাতের পর রাত জেগে চলতো বাবার স্মৃতি রোমন্থন আর সেই স্মৃতিকে শব্দে রূপদান। আমার ছোট চাচু খালিদ হোসেন এবং তাঁর একমাত্র মেয়ে শেনিন এই লেখাগুলো সাজাতে আব্বুকে সহায়তা করতো। অতঃপর বাবা লেখাটা শেষ করে পহেলা নভেম্বর হাসনাত আংকেলকে ইমেইল করে দিলেন। কিন্তু হাসনাত আংকেল তো কোনো রিপ্লাই করছেন না। ফোনে কলটাও আংকেল রিসিভ করলেন না। একটু পর কেউ একজন বাবাকে কল করে জানালেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসনাত আংকেল না-ফেরার দেশে চলে গেছেন। আমি জানি না, বাবার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল এই খবর শুনে। এর ঠিক আগের দিনই বাবারও করোনা টেস্ট করা হয়েছিল। বাবার কাশি ছিল কয়েকদিন ধরে। হাসনাত আংকেলের মৃত্যুসংবাদ জানার পরপরই আমরা অনলাইনে রিপোর্ট পেলাম – আমাদের বাবা-মা দুজনেই করোনা পজিটিভ। অতঃপর এভারকেয়ার হসপিটালে টানা ১৪ দিন ধরে জীবনের কঠিনতম যুদ্ধটি শেষ করে আমার বাবা নিজের শরীর নামধারী খোলসটিকে ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এলেন, ১৪ই নভেম্বর, ২০২০।
আত্মা বা রুহ হলো একধরনের শক্তি। বিজ্ঞান বলে, শক্তিকে সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যায় না, শক্তির রূপান্তর ঘটানো যায় শুধু। রূপান্তরিত হয়ে সেই শক্তি আরো ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের বাবা টিআইএম তাইমুর হোসেন, কালি ও কলম সম্পাদক কবি আবুল হাসনাত আংকেল আর আমাদের বড় চাচু কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন এখন আরো কয়েকগুণ বেশি ঋদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা এখন আর অতি সাধারণ নশ্বরের কাতারে পড়েন না। আমরা তাঁদের পারলৌকিক শান্তি কামনা করি।
– লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর দুই সন্তান নাভিদ ও নোভা।]

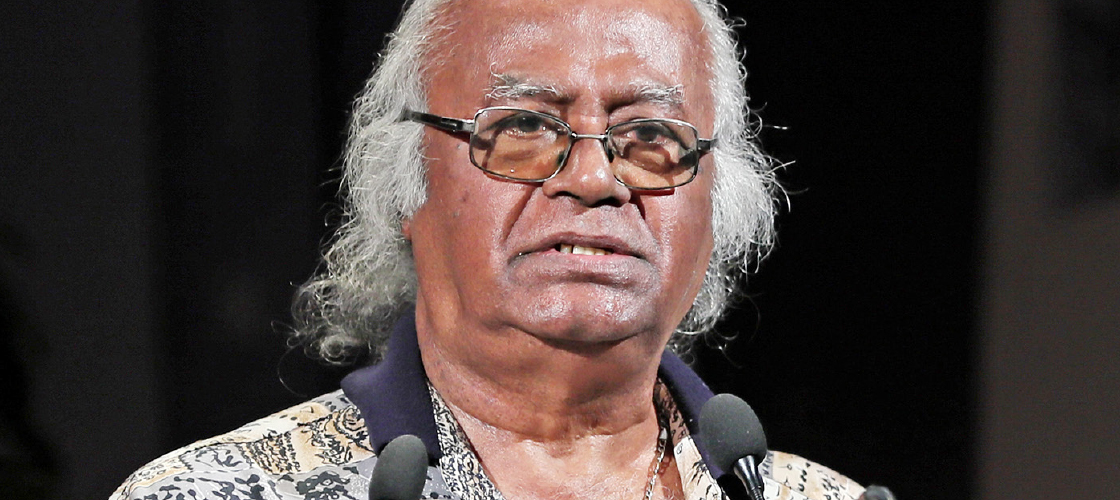
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.