পাঠশালা থেকে ইস্কুল, যেন এক লাফ। শহরের যে-প্রান্তে তখন আমাদের বাস তার সন্নিকট ছিল পাঠশালা। একটু এঁকেবেঁকে সেই পায়েচলা পথ – কিঞ্চিৎ বেতবনের পরেই এক সদ্যকাটা পুকুরপাড়, তারপর সিধে এক মাঠমতো বিস্তারের ধার ঘেঁষে গিয়ে বড়োরাস্তায় ওঠা, উঠে ডাইনে এগোলেই ওই টিনে-ছাওয়া চারচালা বাড়ি, যার নাম কিশোরীমোহন পাঠশালা। বারান্দায় কি পাঁচটে দরজা, নাকি একটাই? কিন্তু ঢুকে পাঁচটে শ্রেণি? প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম মান, দ্বিতীয় মান, তৃতীয় মান; তবে অন্তর্বর্তী কোনো দেয়াল দেখছি না স্মৃতিতে। কিন্তু তোমাকে এক-এক বছরে এক-এক ধাপ পেরোতে হবে। ‘দেখে যেন মনে হয় সৈন্য চলেছে পা ফেলে’ এক পদ্যের টুকরো, যার আগে ছিল ‘বর্ষায় ভরপুর নদী চলে তালে তালে’ (নদী নিয়ে পদ্য কি অনেক বালকেই একবার লিখে ফেলে না?)। পাঠশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈন্য দেখার গল্প আগে বলেছি।
ইস্কুল শহরের আরেক প্রান্তে। পাঠশালা মীরাবাজারে, আর ইস্কুল দাড়িয়াপাড়ায়। যেতে হয় অনেকটা পথ হেঁটে – সোবহানিঘাট থেকে ধোপাদিঘির পাড় হয়ে বন্দরবাজার পেরিয়ে জিন্দাবাজারও পেরিয়ে গিয়ে, তার বড়ো চৌমাথায় বাঁয়ে মোড় নিয়ে খানিক এগিয়ে আবার ডাইনে গেলে তবেই দাড়িয়াপাড়া। ইস্কুলের নাম ‘রসময় মেমোরিয়েল হাই স্কুল’, প্রতিষ্ঠা
১৯৩০-এ। ‘ন্যাশনাল স্কুল’ হিসেবে শুরু হয়েই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাম নেয় ‘প্যারীমোহন একাডেমী’, কিন্তু আবার অচিরেই জমিদার রসময় চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর পুত্রদের অর্থে লালিত হয়ে নাম পাল্টায় এই সরকারি সাহায্যবিমুখ বিদ্যালয়। শহরের অন্য স্কুলের তুলনায় তা খানিক গরিবই। খেলার মাঠ নেই। খেলতে গেলে যেতে হয় একটু দূরের এক বড়ো মাঠে। আর রোজ তা হয়েও ওঠে না। তাছাড়া যে-পথ দিয়ে যেতে হয় তার একটা অংশ ঈষৎ গা-ছমছমে – সিভিল হাসপাতালের লাশকাটা ঘরের পিছনে সেটা। একা একা যেতে আমাদের অনেকেরই সাহসে কুলোত না। যেতে হলে এক দল জুটোতে হতো তিন-চারজনের। তবে খেলাধুলোয় আমি একেবারেই পোক্ত ছিলাম না। অবশ্য স্কুলটিম ম্যাচ খেললে তা দেখতে যেতাম। নিজে যা একটু-আধটু খেলেছি তা পাড়ায়। এবং হারজিতের খেলায় বেশি হারতামই। তবে খেলা নানা রকমেরই ছিল – কপাটি বা ডাংগুলি যেমন, তেমনি গোল্লাছুট গোছের কিছুও, আবার বাতাবি লেবু লাথিয়ে লাথিয়ে ফুটবলের স্বাদ মেটানো।
সম্প্রতি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতাভ দেব চৌধুরী, কবি, তার শিলচরের নিবাস থেকে এক ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছে – আমারই বালকবেলার। নব্বইতে পৌঁছে ন-বছর (?) বয়সের ওই ছবি দেখে একটু আশ্চর্য লাগছে। ওই অতীত আর এই বর্তমানকে পাশাপাশি রাখলে কেমন হয়! নিতান্তই আত্মকূণ্ডয়ণ, নাকি, যুধিষ্ঠিরপ্রোক্ত ‘শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি’ সত্ত্বেও, মর্ত্যসীমার এক সপাট উপলব্ধি? নিত্যপ্রিয় ঘোষের মতো ‘ঠিকানা খাট’ বলবার সাহস আমার নেই। রণজিৎ গুহ শুনেছি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, ‘কী নিয়ে এখন ভাবছেন’-এর উত্তরে বলেছিলেন, ‘জীবন’। তেমন ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অতীত।
বেশ কটা বাড়িতে বসবাসের স্মৃতি আছে আমার বাল্য-কৈশোরে। তবে একটি সোবহানিঘাট পাড়ায়, যার চৌমাথায় ছিল একদিকে এক পুলিশ ফাঁড়ি ও অন্যদিকে শশীদার মুদিদোকান ও তার লাগোয়া পুকুর। চৌমাথার তিনটি রাস্তা কাঁকরবিছানো – দক্ষিণে, পুবে ও পশ্চিমে – উত্তরেরটি মাটির, তবে শক্তপোক্ত। দক্ষিণেরটি গিয়ে উঠেছে ধোপাদিঘির পাড়ের পিচের রাস্তায়। পশ্চিমেরটি গিয়েও উঠেছে ধোপাদিঘি অতিক্রান্ত উত্তরগামী ওই রাস্তাতেই (ওটাই সিলেট-শিলং হাইওয়ে, এবং ঠিক শহর ছাড়ালেই ওর পাশে পড়বে মুরারিচাঁদ কলেজ যা পাল্লা দেয় গৌহাটির কটন কলেজের সঙ্গে)। এবং পুবেরটি থেকে ডাইনে ঢুকে গেছে কাষ্ঠঘর পাড়ার রাস্তা, আর সেই সংগম পেরিয়ে গিয়ে তা শেষ হয়েছে চালিবন্দরে, যেখানে আছে এক বালিকা বিদ্যালয়। চৌমাথার দক্ষিণ-পশ্চিম মোড়েই ছিল সেই জামগাছ যা আমার সেজদা স্বচ্ছন্দে চড়তেন ও চড়ে হেমমামার বকুনি খেতেন। জামগাছের দক্ষিণে এক টিনে ছাওয়া কিন্তু মাটিলেপা ও ফিকে রং-করা বাখারির দেয়ালওলা একফালি বাড়িতে আমরা কিছুদিন ছিলাম। তা সংলগ্ন দোমহলা টিনের চালেরই কিন্তু ইটের বাড়ির আউটহাউস গোছের। তার উঠোনে পায়চারি করতে করতে আমি কবিতা মুখস্থ করছি, মনে আছে। আর, ও-বাড়ির একটু খ্যাপাটে (?) চৌধুরীমশাই তাঁর এক-হাতে-এক-অতিরিক্ত-আঙুলসহ-জন্মানো শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে ‘নম্বরমারা চৌধুরী’ বলে উঠোনের অন্যপ্রান্তে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, তাও মনে আছে। সেই ইটের বাড়ির ওপাশের ইটের বাড়ির একাংশের পরে কিছুদিন আমরা ছিলাম। সেটা কি যুদ্ধকালীন কোনো সময়ে যখন ব্রহ্মদেশ থেকে দেওয়া নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা, লুকিয়ে শোনা যেত রেডিওতে? এর মেঝে একটু লালচে ছিল। দেয়াল কি ঈষৎ হলদে? এরই এক পার্টিশন-করা ঘরে কি একবার সরস্বতীপুজোও করেছিলাম, যার জন্য কোনো পুরুতের দরকার পড়েনি, আর যার পরের দিন সকালবেলা গুনে গুনে ১০৮ বার ‘শ্রীশ্রীসরস্বতৈঃ নমঃ’ লিখেছিলাম?
রাস্তার উল্টোদিকের দুটো বাড়ির দ্বিতীয়টার স্মৃতিও খানিক আছে আমার, যার সামনেই পাড়ার পুকুরঘাট। সেই বাড়ির লাগোয়া এক গলির ভেতর আমাদের সুপ্রভা মাসিমার খালি বাড়িতেও বোধকরি কিছুদিন আমরা ছিলাম। কোনটা আগে কোনটা পরে ঠিক মনে নেই। তবে বিত্ত আমাদের কোনোকালেই তেমন ছিল না। আমার জন্মের অনেক আগেই আমার বাবা, ‘অসহযোগ’-এর আহ্বানে, তাঁর সরকারি কাজ (অ্যাসিস্টেন্ট স্কুল ইনস্পেকটরশিপ) বর্জন করে, বিএল পড়ে নিয়ে আইনব্যবসায় শুরু করেন, তবে তাঁর স্বভাবনম্রতা ও সত্যবাদিতার কারণেই হয়তো সম্মান পেলেও পসার জাঁকিয়ে তুলতে পারেননি। বাড়িঘর নিয়ে কোনো বিলাসের প্রশ্নই আমাদের বস্তুত ছিল না। সোবহানিঘাটের যে-বাড়ির স্মৃতি আমার সর্বাধিক তা পাড়ার উত্তর প্রান্তের, উল্লিখিত মাটির রাস্তার ধারে – গারো পাহাড়ের টুরা-বাসী পিডব্লুইডি-তে কর্মরত আমার বড়ো জামাইবাবু তাঁর দুই বড়ো মেয়েকে আমাদের সঙ্গে সিলেট শহরে রেখে পড়ানোর জন্য এই ছোটো বাড়িটা কিনে নেন। এর দুদিকে ছিল একই মাপের দুটো বাড়ি – যেন-বা তিন বাড়ির এক দ্বীপ। লাগোয়া এক বেতবন, যার ওপার দিয়ে ওই মাটির রাস্তাটা ঘুরে চলে গেছে। প্রথম বাড়িতে থাকতেন তিন ভাই – সারদা-বরদা-অন্নদা। তাঁদের রাঁধুনির ছেলে প্রেমময় ছিল মৃগীরোগী – চোখ আকাশে তুলে হাঁটত। আর, তাঁদেরই গৃহভৃত্য পঞ্চাশের দাঙ্গায় বাজারে ছুরিকাহত হয়ে মারা যায়। তৃতীয় বাড়িতে থাকতেন তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে আমাদের ভগিনীপ্রতিম জ্যোতির্ময়ের মা। জ্যোতির্ময় এষ আমার সেজদা অনন্তর বয়সী, তাঁরই মতো কমিউনিস্টও। আমার অবশ্য ভাব ছিল তার ছোটো ভাই যাদুর সঙ্গে। পড়ুয়া ছেলে, মৃদুভাষী। ওই বাড়ি থেকেই যে পুলিশ সেজদাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তা অন্যত্র বলেছি। তবে যা বলিনি তা, ওই বাড়িরই বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে একবার আমাদের দু-একজনের প্রথম যৌনবোধের অঙ্কুরোদ্গম হয়।
সোবহানিঘাটের এই প্রান্তের এক খাঁড়ি মতো ছিল একটি ছোটো পাড়া। জয়সাগর নামের দিঘির নিমিত্ত তা জয়নগর। আমাদের গৃহত্রয়ে পৌঁছবার আগেই মাটির রাস্তাটি থেকে একচিলতে পথ পুবে চলে গেছে ওই দিঘিতে। সেই পথের দু-ধারে গুটিকয় বাড়ি। আর লম্বাটে দিঘির দুই পাড়ে আস্ত দুই সার বাড়ি। নিতান্ত পায়েচলা পথে হেঁটেই, হয়তো কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে, তাদের দ্বারবর্তী হতে হয়। দু-পাড়ের দুই শেষ বাড়িকে মনে হতো স্বর্গের কাছাকাছি – সামনে ওই অতটা জল আর পুবের জানলার ওপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত! এই দিঘির পশ্চিম পাড়েই এসে ভিড়ত নদীর হাওয়া বয়ে আনা সেই জ্বালানিকাঠ বিক্রিওলা ডিঙিগুলো যাদের কোনো একটা চুরি করে নিয়ে আমাদের কারো কারো ভাঙাচোরা নৌকাভ্রমণের গল্প আগে করেছি। এই দিঘির জলে সাঁতার কেটে স্নান অবশ্যই লোভনীয়, কিন্তু তার চাইতেও লোভনীয় ওই চৌর্যোত্তর নৌকাভ্রমণ।
আমাদের ওই গৃহত্রয়ের মধ্যম গৃহবাসের এক মুখ্য স্মৃতি আমার ম্যালেরিয়ার। ধুধু জ্বর। সেইসঙ্গে সব যেন কেমন একটু দুলছে, ওই আলনাটা তো বটেই, এমনকী মাথার ওপরের ছাদও। আর কুইনিন! তার তেতো স্বাদ কি কখনো ভোলা যায়! এখনকার ক্লোরোকুইন নয়, আদত কুইনিন। এবং ম্যালেরিয়া কি একবার ধরলে ছাড়ে সহজে! অন্য স্মৃতি, খাটে গুটোনো বিছানায় হেলান দিয়ে – চেয়ার-টেবিলে বসে নয় – বই পড়ার কথা, কোথাও একবার বলেছি। এবং সেই ভিখারিণী – যে সিলেটের ঐতিহাসিক গণভোটের আগে হিন্দু পাড়ায়/ বাড়িতে গিয়ে বলত, ‘গণভোটে পাশ করিয়ে গড়তে থাকো হিন্দুস্থান, মরুক্ শালার পাকিস্তান’ আর মুসলমান পাড়ায়/ বাড়িতে গিয়ে বলত, ‘গণভোটে পাশ করিয়ে গড়তে থাকো পাকিস্তান, মরুক্ শালার হিন্দুস্থান’ – বলেছি তার কথাও। হলোও সেই গণভোট ৬ই জুলাই ১৯৪৭-এ; আর দেশভাগের পরে আমরা পাকিস্তানবাসী হলাম। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। আমাদের স্বাধীনতাদিবস হলো ১৪ই আগস্ট। আমি কি কৈশোরে পা দিলাম?
দেশভাগ যে তখন সবটা বুঝে উঠতে পেরেছিলাম তা নয়। কে যেন খানিকটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, হ্যাঁ, এক জামাইবাবু – এক জ্যাঠতুতো দিদির স্বামী, অমর দত্ত, যাঁর মতো স্মিতভাষী খুব সহজে মেলে না – শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে নেমে যাঁদের গ্রামে এক ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার কল্পজগৎ এই অভিনব সময় কীভাবে মোকাবিলা করবে সেই ভাবনা থেকেই বোধকরি বলছিলেন। অবশ্য তার আগে একটা মন্বন্তর ঘটে গেছে : ডালভাত যে কী মহার্ঘ তা খেতে বসে টের পেয়েছি। যুদ্ধকালীন ব্ল্যাকআউটও অন্ধকারের আপেক্ষিকতা বাড়িয়ে দিয়েছে। এও যে বড়ো হওয়া, তা কি কিছু কিছু বুঝতে পারছিলাম না? মন্বন্তর ও ব্ল্যাকআউটের পরের বড়ো ঘটনা গান্ধীহত্যা যার খবর আমাদের ‘পাণ্ডববর্জিত’ মফস্বলে এসে পৌঁছেছিল ঢ্যাঁড়া পিটোনোর মতো করে। তা আগে বলেছি। এবং শুনে আমার কমিউনিস্ট দাদা কী বলেছিলেন (‘মানুষটাকে মেরে ফেলল’ – সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘হিন্দুধর্মে বাধেনি’ থেকে খুব দূরের নয় তা) তাও বলেছি। নিবন্ধপাঠকের কাছে আমার এই ঘনঘন পুনরুক্তির জন্য মার্জনা চাইছি।
আমরা থাকি সদর সিলেটে, আর জ্যাঠামশাইরা থাকেন মৌলভীবাজারে। মৌলভীবাজার তখন সদরের মতোই মহকুমা। আরো তিনটে মহকুমা ছিল সিলেট জেলায় : সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জ। (করিমগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন একটা অঞ্চল গণভোটে অসমে [তথা ভারতে] থেকে যায়।) সুনামগঞ্জের ছাতকে ছিল এক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সুরমা নদীর পাড়ে এক বিয়েতে একবার স্টিমারে করে ছাতক গিয়েছিলাম মনে আছে। সেখানে এক সমবয়সী ছেলের সঙ্গে ভাব হয় – এতটাই যে অনুষ্ঠানশেষে সে যখন অসহায়ের মতো আসরের এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ল তখন তাকে পাহারা দিতে থাকলাম, যতক্ষণ না তার খোঁজে বড়োরা এলেন। সিলেট ফিরে এসে আর তাকে মনেই ছিল না। মৌলভীবাজারে অনেক চা-বাগান ছিল। তার একটাতে প্রায়ই ছুটিছাটাতে গিয়ে থাকতাম। নাম করিমপুর। আমার ছোটো জ্যাঠতুতো দাদা সেখানে কাজ করতেন। আমাদের গ্রামের বাড়িতে যে-দুর্গাপূজা হতো তা একসময় সেখানে উঠে আসে (আমাদের সিলেটের বাড়িতেও একবার তা হয় এবং সদ্য-কমিউনিস্ট আমার দাদাদের ভক্তির অভাবে বাবা বোধকরি একটু ক্ষুণ্নই হন)। করিমপুরে আমার দু-তিন বন্ধুও জোটে। আবার অদূরেই ছিল পিসিদের গ্রাম। তারা জমিদার। পুজোয় ছেলেরা থিয়েটার করত। একবার তাদের কর্ণার্জুন-এ আমি বৃষকেতুর পার্ট করেছিলাম। নির্বাক। তা থেকেই কি না, নাকি সোবহানিঘাটের প্রতিবেশী অন্নদাবাবুর গ্রামোফোনে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সিরাজউদ্দৌলা শুনে শুনে, আমাকে একবার থিয়েটারে পায়। অবশ্য আমার দৌড় ছিল সুনির্মল বসুর বন্দীবীর।
করিমপুর ছাড়া আরেকটা চা-বাগানেও বেড়াতে গেছি। কাজুরিছড়া। আমার দ্বিতীয় জামাইবাবু সেখানে কাজ করতেন। তাঁর দাদা, কুলাউড়া হাইস্কুলের হেডমাস্টার, নগেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন এক বিরল শিক্ষক। বাড়ির ছেলেমেয়েদের নাম রাখতেন খুব যত্ন করে : সৌমিত্রি বা দেউটি বা রণজী। বাল্যকালের আরেকটা স্মৃতি মামাবাড়ি – আসলে মা-র মামাবাড়ি-যাওয়া। বর্ধিষ্ণু গ্রাম পঞ্চখণ্ড (করিমগঞ্জ মহকুমাভুক্ত), আর বড়োমামা প্রমথনাথ দাস এক অর্থে আদর্শ জমিদারও।
বড়োমামা-ছোটোমামার ও তাঁদের দিদি, আমার শিলংয়ের (সুপ্রভা) মাসিমার মা, অর্থাৎ মা-র মামিমা, তখনো বেঁচে। আবার, পঞ্চখণ্ডেই যে প্রথম হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে দেখি, সে-কথা আগে লিখেছি – মামাদের মামাতো (?) ভাই, ডাকনাম লালু। সিলেটে তাঁর কুসুমদিদির বাড়িতেও কি দু-একবার আসেননি আমাদের লালুমামা? বড়োমামা তো মাঝে মাঝেই আসতেন, কুসুমদিদির স্বামী ‘উকিলবাবু’র সঙ্গে নানা পরামর্শও করতেন। ছোটোমামাকে দেখেছি মুখ্যত করিমগঞ্জ শহরে। সেখানে মামাদের একটা পুকুরওয়ালা বাড়ি ছিল। ছোটোমামার দুই ছেলে সেখানে স্কুলে পড়ত। বড়ো সন্তু (সুকান্ত), পরে জেনেছি, আমার যাদবপুরের সহপাঠী-সহকর্মী বন্ধু মানবের (সন্তুর ‘টোগো’) সহপাঠী ছিল। ছোটো, শক্তি, অকালে মারা যায়।
মা-র এক বোন ছিলেন, নাম স্নেহ। থাকতেন মৌলভীবাজারে। তাঁর ছেলে সুনীল ঘোষ – আমাদের সুনীলদাদা – ছিলেন এক প্রিয় কথা-বলিয়ে আমার। নানা বিষয়ে আগ্রহ, আবার রসেরও ঘাটতি নেই। আমার কৈশোরের কিছু প্রফুল্ল মুহূর্ত কেটেছে তাঁর সান্নিধ্যে। আমার মাকে তাঁর বাবা রাজচন্দ্র গুপ্ত কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মা-র মুখেই একটা প্রবাদ শুনতাম, ‘কত রবি জ্বলে, কে বা আঁখি মেলে।’ আর, মনে আছে মা দিনান্তরণের হিসেব করছেন, ‘বুধে বুধে আট’; প্রথমে একটু অবাক লাগত, পরে বুঝতাম, হ্যাঁ, উভয়েই তো ভুক্ত। তাঁর অকালমৃত ভাইয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মধুকে (মধুসূদন গুপ্ত) একসময় আমাদের বাড়ি আনিয়ে নেওয়া হয়। আমার মামাতো ভাই আমার ছোটো ভাইয়ের মতো বড়ো হতে থাকে। সে পরে ভারতীয় নেভিতে যোগ দেয় এবং দীর্ঘদিন নৌবাহিনীভুক্ত হয়ে থাকে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডুবুরি হিসেবেও সে বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
এখন যাকে ‘আবৃত্তি’ বা ‘বাচিক শিল্প’ বলা হয় তাতে আমার দক্ষতা না থাকলেও, কবিতা পড়ে শোনানোর এক প্রবণতা ছিল। মাঝে মাঝে তার ডাকও আসত – সব কিশোর তো আর পাঠ্যের বাইরে কবিতা পড়তই না, পড়ে শোনানো দূরের কথা। ভরসা সেই রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতাই। কমিউনিস্ট দাদাদের বন্ধুরাও স্নেহ করতেন। পুরান লেনের দত্তবাড়ির রাণুদা, বারীনদা (তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে), হেনাদি বা সেনবাড়ির আশুদা, শান্তাদি। তাঁদের ছোটোভাই সৌমেন তো আমার বন্ধুই ছিল। আবার জিন্দাবাজারের বর্মণ স্টুডিয়োর অজিত বর্মণ (আমার ধনদা অনাদির বন্ধু, খুব সিগারেট খেতেন) ও অবনী বর্মণ (সেজদা অনন্তর বন্ধু)। ধনদা যেখানে কাজ করতেন, সেই মডার্ন বুক ডিপোতে যখন ছাড়পত্র এসে পৌঁছল, তখন এই কিশোরের কী উত্তেজনা! ‘দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কথা/ আমি যে বেকার পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা’র সুকান্ত, ‘কিশোর কবি’। আমি খানিক ছাত্র ফেডারেশন করি, ছাত্রকল্যাণের এক মন্ত্র আওড়াই, সুকান্ত আমার কবি হবে না তো কার কবি হবে!
এ-বছরই কোথায় যেন দেখলাম ১৯৫০-এর ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে যে-নৃশংস গুলি ও লাঠিচার্জ করা হয়েছিল, ‘খাপড়া দিবস’ হিসেবে তার স্মরণ করা হচ্ছে। আহতদের তালিকায় সেজদা অনন্ত দেবও আছেন, তাঁকে সোবহানিঘাট থানার পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল একটু পরোক্ষভাবে, মানে পুলিশ তাঁকে ধরতে আসেনি, এসেছিল তাঁর কমিউনিস্ট-বন্ধু মকসুদকে ধরতে। তখন পূর্ব পাকিস্তানে পার্টি বেআইনি। থানায় ফিরে গিয়ে পুলিশ জানায়, মকসুদকে পাওয়া যায়নি, কিন্তু অন্য একজনকে পাওয়া গেছে। তাঁকেই ধরে আনতে আদেশ দেয় থানা। আমার মনে আছে, আমি সেদিন স্কুলের সরস্বতীপূজা কমিটির তরফে এক মিটিংয়ে ছিলাম। আমাকে কেউ সেখানে বাড়িতে পুলিশ আসার খবর দেয়। আমি রিকশো নিয়ে ছুটে এসে জানি, তারা সেজদাকে ধরতে আসেনি। আমি ফিরে যাই। এভাবে যে ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ ফের এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে, তা ভাবতেও পারিনি।
১৯৫০-এ আমি ক্লাস টেন-এ। এক বছর পরেই ‘ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ঢাকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসব। বিষয় যতদূর মনে পড়ছে : বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল। একটা অতিরিক্ত বিষয় নেওয়া যেত, তাতে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৩০ বাদ দিয়ে মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হতো। সেই বিষয় আমার ছিল অ্যাডিশনাল ম্যাথেমেটিকস। টেস্ট পরীক্ষার পর বোর্ডের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কিছুদিন সময় পাওয়া গিয়েছিল। শহরে না থেকে ওই সময়টা আমি এক গ্রামে গিয়ে কাটাই। নাম মনে পড়ছে না সেই গ্রামের – কুলাউড়া স্টেশনে নেমে খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। বাবার এক সম্পর্কিত ছোটো ভাই, প্রাণেশ কর (এতদিন পরেও তাঁর চেহারা জ্বলজ্বল করছে), কুলাউড়া হাইস্কুলে পড়াতেন, যে-স্কুলের হেডমাস্টার নগেন্দ্র চৌধুরীর কথা ওপরে বলেছি। প্রাণেশকাকা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। যত্নের অভাব ছিল না সেই ‘অজ্ঞাতবাসে’। সাহচর্য পেয়েছিলাম এক ছোটো খুড়তুতো ভাইয়ের। ডাকনাম নূপুর। সে পরে অঙ্ক পড়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের নামী শিক্ষক হয়।
রসময় মেমোরিয়েল হাইস্কুলের ছাত্রের ম্যাট্রিক পরীক্ষার সিট কি নদীর পাড়ে গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পড়েছিল? আর তখনো কি তার পোশাক হাফপ্যান্ট-শার্ট? ফল বেরোনোর পর যখন কলেজে পড়বার জন্য – একা একা – কলকাতা রওনা হলো তখন কি সে ফুলপ্যান্ট-শার্টে ‘উন্নীত’ হয়েছে?
[কৃতজ্ঞতা : ঊষারঞ্জন ভট্টাচার্য]

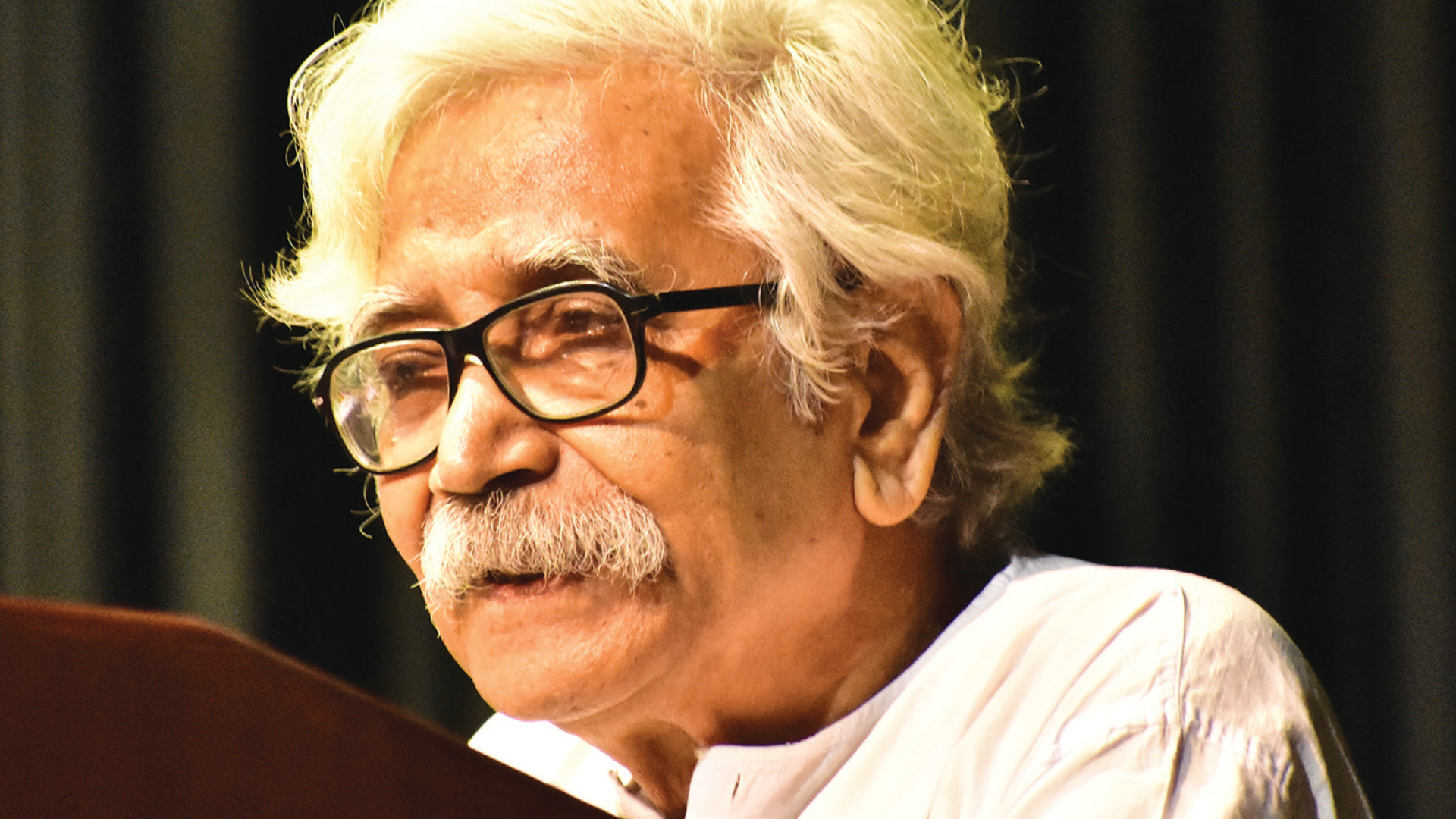
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.